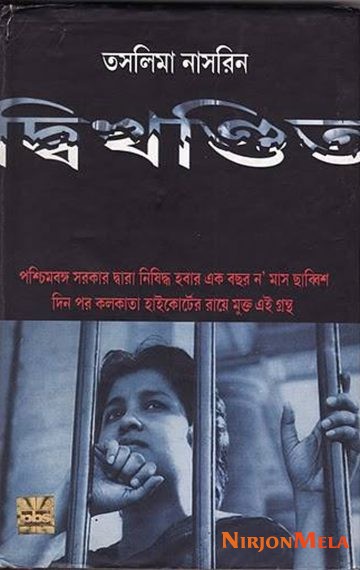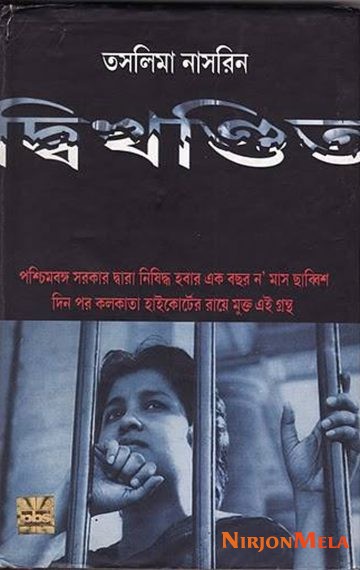০৯. সুখের সংসার
মিটফোর্ডের ব্লাড ব্যাংকে পোস্টিং আমার। রক্ত বিক্রি করার জন্য দরিদ্র কিছু লোক আসে, সেই লোকদের শরীর থেকে রক্ত কি করে নিতে হয়, কি করে রক্তের ব্যাগে লেবেল এঁটে ফ্রিজে রাখতে হয় তা ডাক্তারদের চেয়ে টেকনিসিয়ানরাই জানে ভাল। সকাল আটটা থেকে বেলা দুটো পর্যন্ত খামোকা বসে থাকতে হয় আমার। মাঝে মধ্যে কিছু কাগজে সই করা ছাড়া আর কোনও কাজ নেই। এরকম কাজহীন বসে থাকা আমার অসহ্য লাগে। ব্লাড ব্যাংকের পাশেই স্ত্রীরোগ ও প্রসূতি বিভাগ। ওখানে ডাক্তাররা দম ফেলার সময় পায় না এমন ছুটোছুটি করে কাজ করে। দেখে আমার বড় সাধ হয় ব্যস্ত হতে। দিন রাত কাজ করতে। একদিন গাইনি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক বায়েস ভুঁইয়ার কাছে একটি আবেদন পত্র লিখে নিয়ে যাই। ‘আমি গাইনি বিভাগে কাজ করতে আগ্রহী, আমাকে কাজ করার অনুমতি দিয়ে বাধিত করবেন।’ অধ্যাপক বায়েস ভুঁইয়া আমাকে বাধিত করেন।
হাসপাতালের কাছেই আরমানিটোলায় আমার বাড়ি। বাড়িটি ভাড়া নিতে আমাকে সাহায্য করেছেন বিদ্যাপ্রকাশের মালিক মজিবর রহমান খোকা। খোকার প্রকাশনায় আমার কবিতার বই খুব ভাল চলছে। আরও লেখার প্রেরণা দিচ্ছেন তিনি। হাসপাতাল থেকেই ব্লাড ব্যাংকের অকাজের সময়গুলোয় মিটফোর্ডের কাছেই বাংলাবাজারে গিয়েছি বইয়ের খবর নিতে, দুএকদিন যাওয়ার পর একদিন তাঁকে বলি, যে করেই হোক একটি বাড়ি যেন তিনি আমার জন্য খোঁজেন, ভাড়া নেব। ইতিমধ্যে হাসপাতালের আশে পাশে বাড়ি খুঁজতে খুঁজতে মাথায় টু লেট লেখা যে বাড়িতেই গিয়েছি, বাড়ি, বাড়িভাড়া সবই পছন্দ হবার পর, বাড়িঅলা জিজ্ঞেস করেছেন, ‘কে কে থাকবে বাড়িতে?’
‘আমি থাকব।’
‘আপনি সে তো বুঝলাম, কিন্তু পুরুষ কে থাকবে আপনার সঙ্গে?’
‘কোনও পুরুষ থাকবে না, আমি একা থাকব।’
বাড়িঅলা চমকে উঠেছেন, ‘একা আবার কোনও মেয়েমানুষ কোনও বাড়িতে থাকে নাকি!
আপনার স্বামী নাই?’
‘না।’
‘না, কোনও একা মেয়েমানুষকে আমরা বাড়ি ভাড়া দিই না।’
মুখের ওপর দরজাগুলো ধরাম করে বন্ধ হয়ে যায়। তারপরও আশা ছেড়ে দিই না। খোকা রাজি হলে খোকাকে নিয়ে বেরোই বাড়ি দেখতে। যে বাড়িই পছন্দ হয়, সে বাড়িতেই, যেহেতু খোকা পুরুষ মানুষ, বাড়িঅলা তাঁকেই জিজ্ঞেস করেন, কে কে থাকবে বাড়িতে? খোকা বলেন, ‘উনি থাকবেন, উনি ডাক্তার, মিটফোর্ড হাসপাতালে চাকরি করেন।’
‘উনার স্বামী নাই?’
খোকা খুব নরম কণ্ঠে বলেন, ‘না, উনার স্বামী নাই। মিটফোর্ড হাসপাতালে নতুন বদলি হয়ে এসেছেন। হাসপাতালের কাছাকাছি থাকলে সুবিধা। আপনারা ভাড়ার জন্য চিন্তা করবেন না। উনি যেহেতু ডাক্তারি চাকরি করেন, বুঝতেই তো পারছেন, মাস মাস বাড়িভাড়া দিতে উনার কোনও অসুবিধে হবে না।’
খোকাকে নিয়ে এসে এইটুকু অন্তত কাজ হয় একজন ডাক্তার যে বাড়িভাড়া দেওয়ার ক্ষমতা রাখে তা তিনি নিজমুখে ব্যাখ্যা করে বাড়িঅলাদের রাজি করাতে চেষ্টা করেন। কিন্তু যতই মধুর কণ্ঠে মধুর হেসে বলা হোক না কেন, সত্যিকার কোনও কাজ হয় না। কেউই বাড়ি ভাড়া দিতে চায় না কোনও একলা মেয়েমানুষকে। অত্যন্ত অমায়িক কিছু সজ্জন বাড়িঅলা পেয়েছি, যাঁরা মুখের ওপর ধরাম করে দরজা বন্ধ করে দেননি, বা যান ভাই রাস্তা মাপেন, বাড়ি ভাড়া দেওয়া যাবে না বলে দূর দূর করে তাড়াননি, খোকার সবিশেষ অনুরোধে রাজি হয়েছেন বাড়ি ভাড়া দিতে তবে মেয়ের বাবা বা ভাইকে সঙ্গে থাকতে হবে। এর অর্থ স্বামী যদি না থাকে, কি আর করা যাবে, পোড়া কপাল মেয়ের, তবে কোনও একজন পুরুষ আত্মীয়ের থাকতেই হবে সঙ্গে। কেন একটি মেয়ের একা থাকা চলবে না তা বিশদ করে কেউ বলেন না। আমার অভিভাবক একজন কেউ থাকতেই হবে। আমি একজন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষ, আমিই আমার অভিভাবক— এ কথা কেউ মানেন না। বাবা ভাই মামা কাকা কাউকেই যে সম্ভব নয় তাদের জীবন থেকে তুলে এনে আমার সঙ্গে রাখার, তা খোকাকে বলি। খানিক পর মার কথা মনে হয়, এক মাকেই আনা যেতে পারে। কিন্তু মা তো পুরুষ নন, বাড়িঅলারা পুরুষ চান। একজন ডাক্তার মেয়ের সঙ্গে যদি তার মা বাস করেন তবে বাড়ি ভাড়া পাওয়া যাবে কি না তার খোঁজও নেওয়া হল, এতেও লাভ হল না। খুঁজে খুঁজে ঘেমে নেয়ে রাস্তা মাপতে মাপতে আশা ছেড়ে দেওয়ার আগে শেষ চেষ্টা করে দেখার মত যে বাড়িটিতে ঢুকি সেটি আরমানিটোলার এই বাড়িটি। বাড়ির মালিকের সামনে খোকা যতটা বিনীত হতে পারেন হয়ে ঘন্টা দুয়েকের প্রশ্নোত্তরে পাশ মার্ক জুটিয়ে মা আর মেয়ের থাকার ব্যপারে অনুমতি লাভ করেন। জাহাজের মত এই বিশাল বাড়িটির মালিক একটি অশিক্ষিত লোক, লোহা লককরের ব্যবসা করে টাকার পাহাড় হয়েছেন। টাকার পাহাড় হলে যা করে বেশির ভাগ লোক, তিনি তাই করেছেন, দাড়ি রেখেছেন, মাথায় টুপি পরেছেন আর আল্লাহকে সাক্ষী রেখে চারটে বিয়ে করেছেন। চার বউকে পৃথক পৃথক চারটে বাড়িতে রেখেছেন। জাহাজ বাড়িটির দোতলায় চার নম্বর বউ নিয়ে বাস করেন। বাড়িভাড়া তিন হাজার, আর আমার মাইনে কচ্ছপের মত হেঁটে হেঁটে সাকুল্যে আড়াই হাজারে দাঁড়িয়েছে। এই পার্থক্য সত্ত্বেও বাড়ির পাঁচতলায় দুটো ঘর আর লম্বা টানা বারান্দার একটি অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নিই। একা আমি নিজের বাড়িতে থাকব, অন্যের বাড়িতে অন্যের আদেশ মত নয়, এই আনন্দ এবং উত্তেজনায় আমি কাঁপি। জীবনের প্রথম কারও ওপর ভরসা না করে জীবন যাপন করার জন্য আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। সস্তায় একটি খাট, সস্তায় তোশক বালিশ চাদর, একটি ইস্পাতের আলমারি আর কিছু প্রয়োজনীয় বাসন কোসন কিনে আপাতত বাড়িটি বাসযোগ্য করি। ময়মনসিংহ থেকে মাকে নিয়ে আসি, লিলিকেও। আলাদা একটি বাড়ি ভাড়া করে সম্পূর্ণ নিজের পছন্দ মত থাকায় মাও খুব খুশি। মা এসেই লিলিকে দিয়ে ঘরদোর পরিষ্কার করে গুছিয়ে রান্নাবান্না করে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আরমানিটোলার মাঠে ছেলেপেলেদের ফুটবল খেলা, রাস্তার গাড়িঘোড়া আর খোলা আকাশ দেখেন। ধীরে ধীরে জানালার পর্দা কিনি, বিস্তর দরদাম করে বড় একটি লাল সবুজ রঙের তকতির ডিজাইন করা লাল কার্পেট কিনি, রং মিলিয়ে কয়েকটি কুশনও। কোনও সোফা বা চেয়ার টেবিল কেনার টাকা নেই, তাই কুশনেই হেলান দিয়ে কোনও অতিথি এলে যেন বসতে পারে। সোফা যে কিনতে পারিনি, সে জন্য মনে কোনও দুঃখ থাকে না। নিজের প্রথম সংসারটি বড় সুন্দর করে সাজাতে ইচ্ছে করে, সুন্দর সুন্দর জিনিসের দিকে চোখ যায়, কিন্তু আমার সামর্থের বাইরে বলে সুন্দর থেকে চোখ ফিরিয়ে কম দাম কিন্তু দেখতে অসুন্দর নয়, তেমন জিনিস খুঁজি। তেমন জিনিসই নিজের উপার্জিত টাকায় কিনে নিজের সংসারে এনে যে আনন্দ হয় তার তুলনা হয় না। যে মাসে কার্পেট কেনা হয়, সেই মাসে অন্য কিছু কেনার জো থাকে না। পরের মাসের জন্য অপেক্ষা করি। এই অপেক্ষাতেও একধরনের সুখ আছে। মাইনের টাকায় বাড়িভাড়াই যেহেতু দেওয়া সম্ভব নয়, ভরসা লেখার ওপর। সাপ্তাহিক পূর্বাভাস আর পাক্ষিক অনন্যায় কলাম লিখি। খবরের কাগজ আর আজকের কাগজ থেকে নাইমের প্রভাব দূর হওয়ার পর ওসবেও লিখতে শুরু করি। বিদ্যাপ্রকাশ থেকে আরও একটি কবিতার বই বেরিয়েছে অতলে অন্তরীণ নামে। বই চলে ভাল। বই চললেও রয়্যালটির টাকা আমি দাবি করি না। লজ্জা হয় টাকা চাইতে তাছাড়া আমার স্বনির্ভর জীবনে খোকার আন্তরিক সহযোগিতা আমাকে বড় কৃতজ্ঞ করে রেখেছে। বাজার করতে যাব, কোথায় বাজার দেখিয়ে দিচ্ছেন। আসবাবপত্র কিনতে যাবো, থাল বাসন কিনতে যাব, কোথায় যেতে হবে, নিয়ে যাচ্ছেন, দরদাম করে দিচ্ছেন। ডাল ভাত খাচ্ছি অনেকদিন, দেখে একদিন তিনি দুটো মুরগি কিনে নিয়ে এলেন। আমার টাকা ফুরিয়ে আসছে দেখলে মা ময়মনসিংহে চলে যাচ্ছেন, বাবার ভাণ্ডার থেকে নিয়ে বস্তা ভরে চাল ডাল আনাজপাতি নিয়ে বাসে করে চলে আসছেন ঢাকায়। আমার দারিদ্র আছে ঠিকই, কিন্তু সেই সঙ্গে আনন্দও আছে। আমার জীবনে আমি এত দরিদ্র অবস্থায় কাটাইনি, এবং এত আনন্দও এর আগে আমি পাইনি। ভাইএর মত, বন্ধুর মত খোকা আছেন পাশে। মা আছেন তাঁর উজাড় করে ভালবাসা নিয়ে। লিলিও খুশি অবকাশের গাধার খাটুনি থেকে এসে অল্প কাজ আর শুয়ে বসে অনেকটা আকাশের কাছাকাছি থাকার আনন্দে। আমার হিসেবের সংসার অথচ সুখে উপচে পড়া জীবন। হাসপাতালে গাইনি বিভাগে প্রচণ্ড ব্যস্ততা আমার। রোগিতে সয়লাব হয়ে যায় বিভাগটি। ময়মনসিংহের হাসপাতালে গাইনি বিভাগে ইন্টার্নশিপ করার সময় যেমন উত্তেজনা ছিল, যেমন দম ফেলাম সময় ছিল না, এখানেও তেমন। ডেলিভারি করাচ্ছি, এপিসিওটমি দিচ্ছি, এক্লাম্পসিয়ার রোগী ভাল করছি, রিটেইন্ড প্লাসেন্টা বের করছি, ফরসেপ ডেলিভারি করছি, কারও এক্ষুনি সিজারিয়ান, দৌড়োচ্ছি অপারেশন থিয়েটারে, ঝটপট মাস্ক গ্লবস পরে সিজারিয়ানে অ্যাসিস্ট করতে দাঁড়িয়ে যাচ্ছি, আবার গাইনি আউটডোরেও রোগী দেখতে হচ্ছে, সারাদিনে শত শত রোগীর ভিড়, সময়ের চেয়ে বেশি সময় চলে যায় রোগীর চিকিৎসা করে। সারাদিন এসব কাজ করার পর আবার রাতেও ডিউটি পড়ছে। সারারাত জেগে কাজ করতে হচ্ছে। অল্প যেটুকু সময় হাতে থাকে নিজের জন্য, তখন কলাম লিখি। বাড়তি টাকা রোজগার না করলে বাড়িভাড়া দেওয়া যাবে না, উপোস করতে হবে। হাসপাতালের ইন্টার্নি ডাক্তাররা আমি জানি না কেন, আমার বেশ ভক্ত হয়ে পড়ে, অনেকটা বন্ধু-মত। আমার চেয়ে বয়সে অনেক ফারাক থাকলেও এই বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। আমার পরিচয় ওরা সকলেই জানে। আমাকে বলতে হয় না আমি কে। পরিচয় জানার অসুবিধে এই, আমি কাজ করলেও মনে করা হয় আমার মন বুঝি ডাক্তারিতে নেই, মন কবিতায়। আমি প্রেসক্রিপশান লিখতে থাকলে দূর থেকে দেখে কেউ ভেবে বসে আমি হয়ত প্রেসক্রিপশান লিখছি না, কলাম লিখছি। আমার বয়সী ডাক্তাররা এফসিপিএস পাশ করে অথবা পুরো পাশ না করলেও ফার্স্ট পার্ট পাশ করে এসে রেজিস্টার হয়ে বসেছে নয়ত সিএ, ক্লিনিক্যাল এ্যাসিস্টেন্ট। এই বয়সে আমার মত কেবল মেডিকেল অফিসার হয়ে যারা কাজ করছে বিভিন্ন বিভাগে, তাদেরও এফসিপিএস পরীক্ষা দেওয়ার ধান্দা। আমারই কোনও ধান্দা নেই। মোটা মোটা বই নিয়ে বসে যাব, বছরের পর বছর কেটে যাবে বইয়ে ঝুঁকে থেকে, এর কোনও মানে হয়! দেখেছি দশ বছরেও অনেকের পাশ হয় না, অথচ বছর বছর ক্লান্তিহীন দিয়েই যাচ্ছে পরীক্ষা, ফেলই করছে প্রতিবছর। টাকাঅলা বাপ যাদের তারা পিজির এফসিপিএস এ ফেল করে লণ্ডনে গিয়ে কোনও রকম ফেল টেল ছাড়াই এফআরসিএস ডিগ্রি নিয়ে দেশে ফেরত আসে। বাংলাদেশের এফসিপিএস পাশ করার চেয়ে বিলেতের এফআরসিএস পাশ করা সহজ, এ কথা বিশ্বাস না হলেও কথা সত্য। এসব দেখে ইচ্ছে উবে গেছে। মিটফোর্ড হাসপাতালে চাকরি করছে এরকম যে ডাক্তারকেই দেখি আমার কাছাকাছি বয়সী, সকলেই চাকরি করার পাশাপাশি এফসিপিএসএর পড়াশোনা করছে। আমাকে অনেকে জিজ্ঞেস করে, আমি পরীক্ষা দিচ্ছি কি না। আমি সোজা না বলে দিই। অবাক হয় হবু এফসিপিএসরা। হাসপাতালে বসে তাহলে কি ঘোড়ার ডিম করছি, মনে মনে বলে তারা। খানিক পর হেসে, আবার মনে মনেই বলে, কদিন পর তো ঘাড় ধরে বের করে দেবে পোস্টিং দিয়ে কোনও গাঁও গেরামে। শহরের বড় হাসপাতালে চাকরি করতে আসবে যারা পড়াশোনা করছে, এফসিপিএসের মাঝপথে অথবা শেষের পথে। তা ঠিক, হবু এফসিপিএসরা পড়ার ঘোরেই থাকে, তাদের কাজে কোনও অনিয়ম হলে কোনও অসুবিধে নেই, কিন্তু আমার মত ছোট ডাক্তারদের ওপর ইন্টার্নি ডাক্তারদের মত খাটনি যায়। আমার আপত্তি নেই খাটনিতে। কিন্তু কবি বলে নাম থাকায় আমাকে উদাসীন বলে মনে করা হলে আমার বড় মন খারাপ হয়। আর কেউ উদাসীন না বললেও প্রফেসর রাশিদা বেগম বলেন। তিনি আমাকে প্রথম দিন থেকেই মোটেও পছন্দ করতে পারছেন না। প্রথম দিন বিভাগে যেতে আমার দু মিনিট দেরি হয়েছিল বলে। রাশিদা বেগমের মাথার কোষে কোষে গেঁথে গেছে সেই দুমিনিটের কাহিনী। এমনিতে খিটখিটে মেজাজ তাঁর। গাইনি বিভাগের তিনটি শাখার মধ্যে তিন নম্বর শাখার তিনি অধ্যাপিকা। ছাগলের তিন নম্বর বাচ্চার মত মহাশয়ার অবস্থা। মেজাজ ছাড়া তাঁর বিশেষ কিছু সম্পদ নেই। রোগী সামলাতে নাস্তানাবুদ হন, কারও গোচরে এলে তিনি অবস্থা সামাল দিতে চোখের সামনে যাকেই পান তাঁর ওপর চোট দেখান, এতে যেন তাঁর গলার স্বর সকলে শোনে এবং তাঁকেও যেন খানিকটা মান্যগন্য করে তাঁর সহকারীরা, যেমন করে বিভাগের প্রধান অধ্যাপক বায়েস ভুইয়াকে। বায়েস ভুঁইয়া চমৎকার মানুষ। তাঁর কাউকে ধমক দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। তাঁর কাজই তাঁর মূল্য নির্ধারণ করে। দেখা হলেই তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন কেমন আছি, ইতিবাচক উত্তর ছুঁড়ে দিয়ে খুব দ্রুত সরে যাই তাঁর সামনে থেকে। প্রথমত আমার একটু কুণ্ঠাও থাকে পোস্ট গ্রাজুয়েশন করছি না বলে। অধ্যাপকের আশে পাশে যারাই ভিড় করে থাকেন, সকলেই পোস্ট গ্রাজুয়েশনের অর্ধেক নয়ত পুরো ডিগ্রি নিয়েছে। আমি তাই সংকোচে দূরে থাকি। এই সংকোচই আমার ইচ্ছের অংকুরোদগম ঘটায় মনে, এফসিপিএসএর জন্য লেখাপড়া শুরুই না হয় করে দিই। মাও বলেন, বিসমিল্লাহ বইলা শুরু কইরা দেও, তোমার বাপও খুশি হইব। বায়েস ভুঁইয়া বিভাগের অধ্যাপক হয়েও আমাকে বেশ খাতির করেন, কারণটি আমার ডাক্তারি বিদ্যে নয়, আমার লেখা। পত্রিকায় আমার লেখা পড়েন তিনি। মাঝে মধ্যে আমাকে ডেকে আমার এই লেখাটি কিংবা ওই লেখাটি তাঁর খুব ভাল লেগেছে বলেন। লেখালেখির বিষয়টি হাসপাতালের চৌহদ্দিতে উঠলে আমার বড় অস্বস্তি হয়। তবু ওঠে। হাসপাতালে আমি যে কোনও ডাক্তারের মত ডাক্তার। আমার অন্য পরিচয়টি হাসপাতালে এসে আমার হাসপাতালের পরিচয়টি সামান্যও গৌণ করবে তা আমার মোটেও পছন্দ নয়। অ্যপ্রোন পরে হাতে স্টেথোসকোপ নিয়ে হাসপাতালে যাচ্ছি, দেখে মা খুব খুশি হন। আমাকে মুখে তুলে খাওয়ান। আমার পরিচর্যা করতে মা সদাসর্বদা ব্যস্ত। টাকা জমিয়ে একদিন স্টেডিয়াম মার্কেট থেকে ছোট একটি লাল রঙের রেফ্রিজারেটর কিনে আসি। ফ্রিজটি মা দিনে দুবেলা পরিষ্কার করেন নিজের শাড়ির আঁচল দিয়ে। লিলিকে হাত দিতে দেন না ফ্রিজে, কিছু যদি কোথাও দাগ লাগিয়ে ফেলে লিলি। বাইরে থেকে গরমে সেদ্ধ হয়ে এলে মা দৌড়ে এক গেলাস ঠাণ্ডা পানি এনে দেন। রান্না করে করে ফ্রিজে রেখে দেন যেন অনেকদিন খেতে পারি, যেন বাজার করতে না হয় ঘন ঘন। আমাদের সুখের সংসার অভাবে আনন্দে চমৎকার কাটতে থাকে। ইন্টার্নি ডাক্তাররা বেড়াতে আসে বাড়িতে, খেয়ে দেয়ে হল্লা করে ডাক্তারি ভাষায় আড্ডা পিটিয়ে চলে যায়। আমার এই একার সংসারটি সকলের বেশ পছন্দ হয়। খাওয়া দাওয়া প্রথম প্রথম কার্পেটে বসেই হত, এরপর বাড়িতে অতিথির আগমন ঘটতে থাকায় ছোট একটি টেবিল আর দুটো চেয়ার রান্নাঘরে বসিয়ে দিই। ছোট একটি টেলিভিশন, ছোট একটি গান শোনার যন্ত্রও কিনি। আর কিছুর কি দরকার আছে? মা বলেন, না নেই। মা আমাকে বাধা দেন টাকা খরচ করতে। টেবিল চেয়ার গুলো যদি অবকাশ থেকে আনা যেত, তিনি খুশি হতেন। বাপের সম্পদে তো মেয়েরও ভাগ আছে। অথচ বাপ তো কোনওরকম সাহায্য করছে না, মা গজগজ করেন। বাপ সাহায্য না করলেও বাপের প্রতি ভালবাসা আমাকে বায়তুল মোকাররমের ফুটপাত থেকে হলেও বাপের জন্য সার্ট কেনায়, জুতো কেনায় ময়মনসিংহে যাওয়ার আগে। ছুটিছাটায় দুএকদিনের জন্য ময়মনসিংহে যাওয়া হয়। বাপকে দেখতেই যাওয়া হয়। বাপের কোনও সাহায্য নিতে আমার ইচ্ছে করে না বরং বাপকে সাহায্য করতে ইচ্ছে হয়। সাধ আছে অনেক, সংগতি তত নেই। সংগতি বাড়াতে সাইনবোর্ড টাঙিয়েছি আরমানিটোলার বাড়ির সদর দরজায়। ডাক্তার তসলিমা নাসরিন, এম বি বি এস। রোগী দেখার সময় এতটা থেকে এতটা। মাইনের টাকা, রোগী দেখার টাকা, লেখালেখির টাকা সব মিলিয়ে যা হয় তা পই পই হিসেব করে ইস্পাতের আলমারিতে রাখি। বাপের সার্ট জুতো এসব হিসেবের বাইরে। হোক না! বাড়তি খরচের জন্য শাক ভাত খেতে হয়। না হয় খেলামই।
ময়মনসিংহের আত্মীয় স্বজন ঢাকায় কোনও কাজে এলে আমার বাড়িতে ওঠে। দেখে আমার খুব ভাল লাগে। ছটকু এল একবার। কার্পেটে শুল। তাতে কী! ভালবাসা থাকলে ছেঁড়া কাঁথায় শুয়েও সুখ। ছটকু নিজেই বলেছে যে বড় মামা, ফকরুল মামা, ঝুনু খালা বা ছোটদার বাড়িতে গিয়ে এ যাবৎ কোনও স্বস্তি পায়নি, পেয়েছে আমার বাড়িতে এসেই, ছোট হোক বাড়ি, এটা না থাক, ওটা না থাক, কিন্তু নিজের মত পা ছড়িয়ে বসা যায়, গলা ছেড়ে গান গাওয়া যায়, কিছু খেতে ইচ্ছে করলে চেয়ে খাওয়া যায়। মনে হয় নিজের বাড়ি, এমন।
কেবল যে গাইনি বিভাগের ব্যস্ততায় আর পত্রিকার জন্য কলাম লিখেই সময় পার করি তা নয়। মাঝে মধ্যে সাহিত্যের আড্ডায় অনুষ্ঠানেও যাই। ময়মনসিংহের জাকারিয়া স্বপন, ইয়াসমিনের পাতানো ভাই, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে, অনুষ্ঠানের বিতর্ক প্রতিযোগিতায় বিচারক হতে আমাকে একদিন নিয়ে গেল। এর আগে আমাকে যা-ই হতে হয়েছে, কোথাও বিচারক হতে হয়নি। বিচারকদের যে গাম্ভীর্য থাকে, তা যথাসম্ভব ধারণ করে বিচার করে আসি বিতর্কের। একবার ফরহাদ মজহার আমন্ত্রণ জানালেন তার এনজিও উবিনিগে, উবিনিগের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের টাকা সাহায্য জোটে মজহারের অথচ নিজে তিনি এককালের সমাজতান্ত্রিক। টিএসসিতে তাঁর গান শুনেছিলাম অনেক আগে, নিজে গান লিখতেন, সুর দিতেন, গাইতেনও। নিজে হারমোনিয়াম বাজিয়ে ঘর ভরা দর্শককে যতগুলো গান শুনিয়েছিলেন তার মধ্যে সাততাড়াতাড়ি যাচ্ছি বাড়ি গানটি বেশ লেগেছিল। বামপন্থী গায়কটি গান টান ছেড়ে দিয়ে নিজের কবিতার বই বের করলেন। চমৎকার সব কবিতা লিখেছেন। পড়ে মুগ্ধতার শেষ নেই আমার। যাই হোক, তাঁর খবর পেয়ে সাততাড়াতাড়ি তাঁর আপিসে গিয়ে দেখা করি। একটি হাড়গিলে মহিলা নাম ফরিদা আখতার উঠে এলেন ফরহাদ মজহারের ঘর থেকে, মনে হল যেন শয্যা থেকে উঠে এলেন। আমাকে বসিয়ে ভেতর ঘরে ডাকতে গেলেন তাঁকে। ভেতর থেকে বেরোতে অনেকটা সময় নিল তাঁর। মনে হল শয্যা থেকে উঠে উদোম গায়ে সবে কাপড় চড়িয়ে এলেন। চা বিস্কুট এল। কথা চলল। কথা চলল, আসলে তিনি একাই কথা বললেন। তাঁর নিজের কবিতার কথা বললেন, কবিতার কিছু আরবি শব্দ আমি বুঝতে পারিনি বলে তিনি আরবির অর্থ বলে দিলেন। অবোধ্য আরবি শব্দ কবিতায় ব্যবহার করার কি কারণ এই প্রশ্ন করার আগেই তিনি বললেন, এ দেশের বাংলা হচ্ছে ইসলামি বাংলা, আর পশ্চিমবঙ্গের বাংলা হিন্দু বাংলা। আমাদের সংস্কৃতি ইসলামি সংস্কৃতি, আমাদের ভাষায় প্রচুর আরবি উর্দু শব্দ মেশানো উচিত ইত্যাদি ইত্যাদি। ধাঁধা লাগে শুনে। তিনি কি আমাকে দলে টানতে চাইছেন তাঁর এই উদ্ভট মিশনে! তা না হলে আমাকে এমন তলব করার কারণ কি! আসলেই তিনি আমাকে দলে টানতে চাইছেন। এসব আজগুবি চিন্তা নিয়ে তিনি চিন্তা নামে একটি পত্রিকা বের করবেন, ওতে যেন লিখি আমি। ফরহাদ মজহার সম্পূর্ণই পাল্টো গেছেন। এই দেশে ইসলামি মৌলবাদ যখন মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে, গুটিকয় মানুষ এর বিরুদ্ধে লড়াই করছে, গুটিকয় মানুষ চাইছে বাঙালি সংস্কৃতি যে সংস্কৃতি হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান সকলের সংস্কৃতি, তাকে সবলে অস্বীকার করছেন মজহার। দেশ বিভাগের ভূল সিদ্ধান্ত বাংলাকে বিভক্ত করেছে, কিন্তু পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার ভাষা ও সংস্কৃতিতে মৌলিক কোনও পার্থক্য নেই, সে যে কোনও সুস্থ মানুষই জানে। কিন্তু ফরহাদ মজহারের মত চিন্তাবিদের এ কী হাল, সমাজতান্ত্রিক বিশ্বাস থেকে ফট করে পুঁজিবাদীদের টাকায় এনজিও খুলেছেন, এখন আবার গাইছেন ধর্মের গান! কোনও এক ফকিরের গানও শোনালেন আহা কি মধুর বলতে বলতে, দীনের নবী মোস্তফা.. হরিণ একটা বান্ধা ছিল গাছেরই তলায়। আরব দেশের মরুভূমিতে গাছও নেই, হরিণও নেই, অথচ নাকি কী অভাবনীয় কল্পনার মিশ্রণ এই গানটিতে! এই গানকেই তিনি বাংলাদেশের গান বলছেন। রবীন্দ্রসঙ্গীত হিন্দু দের গান, মুসলমানদের গান নয়। বলে দিলেন। ফরহাদ মজহারের এই মতের বিরুদ্ধে পরে আমি একটি কলাম লিখি পত্রিকায়, সঙ্গে শামসুর রাহমানের কবিতায় উর্দূ শব্দ ব্যবহার আর হুমায়ুন আজাদের রবীন্দ্রনাথ বিরোধী বক্তব্যেরও প্রতিবাদ ছিল আমার কলামে। দীর্ঘদিন আমার ওই ভাষা নিয়ে লেখাটির সূত্র ধরে পত্রিকায় লেখালেখি চলল। ফরহাদ মজহার নিজে লিখলেন। তাঁর যুক্তি এবং ইনকিলাব পত্রিকার ছাপা হওয়া কোনও মৌলবাদির যুক্তির মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। তাঁর যুক্তি খণ্ডন করে আরও অনেকে কলাম লিখলেন। পূরবী বসু আমেরিকার পাট চুকিয়ে দিয়ে বাংলাদেশে চলে এসেছেন, তিনি এসেই কলম ধরলেন ফরহাদ মজহারের মতের বিপক্ষে। লোকটির চরিত্র ক্রমশ সন্দেহজনক হয়ে উঠছে, তা স্বীকারও করলেন অনেকে।
ভাষা নিয়ে আমার লেখাটি ছাপা হওয়ার পর শামসুর রাহমান বড় একটি কলাম লিখলেন আমার কলামের উত্তরে। তসলিমাকে তসলিম জানিয়ে তিনি শুরু করেছেন। লিখেছেন আত্মপক্ষ সমর্থন করে। আমি, এটা ঠিক, যে, বাংলা ভাষায় আরবি ফার্সি, উর্দূর অনধিকার প্রবেশ নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে শামসুর রাহমানকে দোষারোপ করেছি তিনি উর্দু শব্দ ব্যবহার করেন বলে। যে শব্দগুলো বাংলা অভিধানে আছে, তার ওপর প্রচলিত, কী দরকার সেই শব্দগুলো ব্যবহার না করে সে ক্ষেত্রে উর্দু শব্দ ব্যবহার করার! শামসুর রাহমান লিখেছেন, ‘প্রত্যেক ভাষাতেই অতিথি শব্দের সমাবেশ ঘটে। অতিথির মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেওয়া আতিথেয়তার রীতিবিরুদ্ধ কাজ। দরজা খোলা রাখা দরকার, সব অতিথিই যে বাঞ্ছিত ও কাঙ্খিত হবে, এটা বলা যাবে না। অবাঞ্ছিত অতিথি অনাদরে নিজে থেকেই কেটে পড়বে। ..অন্নদাশংকর রায় কিন্তু বেশ কিছু উর্দু ও হিন্দি শব্দ অবলীলাক্রমে ব্যবহার করেন। আমার কাছে কখনো দুর্বোধ্য কিংবা শ্রুতিকটু মনে হয়নি। তিনি এক জায়গায় জান পেহচান ব্যবহার করেছেন চেনাজানার বদলে। তাঁর একটি বাক্য উদ্বৃতি করছি, কমলি নেহি ছোড়তি। তসলিমা নাসরিন, আমি কিন্তু এতদূর যাইনি। তাহলে কি আপনি বলবেন শ্রদ্ধেয় অন্নদাশংকর রায় পশ্চিমবঙ্গে বসে ইসলামি বাংলা ভাষা তৈরি করছেন?’ আমি যে লিখেছিলাম ভাষাকে নতুনত্ব দেবার বা সমৃদ্ধ করবার জন্যে এই বাংলা ভাষা এত ভিখিরি হয়ে যায়নি যে অন্য ভাষা থেকে শব্দ হরণ করবার বা ধার করবার কোনো দরকার আছে। আমাদের যা আছে তা নিয়েই আমরা সন্তুষ্ট থাকি না কেন! বরং শব্দভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করবার চেয়ে সাহিত্যকে গুণগত সমৃদ্ধি দেবার আগ্রহ থাকা উচিত সকল সৎ সাহিত্যিকের। .. এ কথার উত্তরে তিনি লিখেছেন, ‘না, তসলিমা, এই উক্তি আপনার মত প্রগতিশীল ব্যক্তির যোগ্য হয়নি। আমাদের সমাজ একটি জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে বলেই কি তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে আমাদের? এর পরিবর্তনের জন্যে চেষ্টাশীল হতে হবে না? বাইরের দুনিয়ার ভালো ভালো জিনিস কি আমরা আমদানি করবো না সমাজ বদলের জন্যে? কোনো ভাষাই, সে ভাষা যত উন্নত ও ধনীই হোক, শব্দঋণ বিষয়ে লাজুক কিংবা নিশ্চেষ্ট নয়, এ কথা নিশ্চয় আপনার জানা আছে।’ আমার জানা আগে না থাকলেও জানা হয়। শামসুর রাহমান আমার চোখ খুলে দিয়েছেন। তিনি বাঙালির ভাষার মধ্যে হিন্দু মুসলমানের ভাগ আনেন না। তিনি একশ ভাগ অসাম্প্রদায়িক মানুষ। ফরহাদ মজহারের মত ইসলামি বাংলা কায়েম করতে চান না। আমি নতুন করে ভাবতে বসি, ভেবে আমি তাঁর সঙ্গেই একমত হই, নিজের ভুলগুলো স্পষ্ট হয়। আসলে সত্যি কথা বলতে, ইসলামি ভাষা বলে কোনও ভাষা নেই। ভাষার কোনও ধর্ম নেই। আরবি ভাষাকেই বা ইসলামি ভাষা বলব কেন! আরবি ভাষার লোক নানা রকম ধর্মে বিশ্বাস করে, তারওপর ওদের মধ্যে এমন লোকও প্রচুর, যারা কোনও ধর্মেই বিশ্বাস করে না। ভাষা আপন গতিতে চলবে, চলেছে, ভাষাকে কোনও নির্দিষ্ট ধর্মে অন্তর্ভুক্ত করা ঠিক নয়। আসলে, ইসলামি ভাষা নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার আমার কারণ ছিল একটিই, ইসলামপন্থী লোকেরা এ দেশটিকে একটি ইসলামি রাষ্ট্র তৈরি করার পরিকল্পনা করেছে, লোকগুলো একসময় বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিপক্ষে ছিল, এখন এই স্বাধীন বাংলায় বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে জোর জবরদস্তি করে ইসলামি বাংলা বানানোর ষড়যন্ত্র করছে— এই আশঙ্কা থেকেই তথাকথিত ইসলামি ভাষাকে রোধ করতে চেয়েছিলাম। মুশকিল কিছু ধর্মান্ধ লোক নিয়ে। কিছু মন্দ লোক মন্দ উদ্দেশে ভাষাকে খৎনা করে ভাবছে ইসলামি পতাকা ওড়াবে দেশে। কেবল ভাষাতেই তো নয়, রাজনীতির মগজেও গাদা গাদা ইসলাম ঢোকানো হচ্ছে। যদি দেশটি শেষপর্যন্ত ইসলামি শাসনে চলে, তবে আর ভাষা থেকে আরবি ফার্সি উর্দু বিদেয় হলেই বা কী! আমার দুশ্চিন্তা দূর হয় না।
কী এমন আর কলাম লিখি! কী এমন ভাল! সাহিত্যের কতটুকুই বা আমি জানি! বাংলা সাহিত্যে লেখাপড়া করার ইচ্ছে ছিল, বাবা তো ঘাড় ধরে মেডিকেলে ঠেলেছেন। এতটা জীবন ডাক্তারি বিদ্যা ঘেঁটে সাহিত্যের কিছুই নিশ্চয়ই শেখা হয় নি আমার। কবিতা লেখার অভ্যেস না হয় আছে, কিন্তু সেই অভ্যেস থেকে গদ্যে হাত পড়লে আদৌ কিছু রচিত হয় বলে আমার মনে হয় না। যা রচিত হয়, তা আলোচিত হলেও প্রশংসিত হলেও আমার সংশয় যায় না। খুঁতখুঁতি থেকেই যায়। তবে গদ্য পদ্য যা কিছুই লিখি না কেন, সবই হৃদয় থেকে আসে। লোকে যেন পড়ে বাহবা দেয়, যেন খুশি হয়, বানিয়ে বানিয়ে এমন কিছু, এমন কিছু যা আমাকে ভাবায় না, যা আমাকে কাঁদায় না, আমার ভাবনার নির্যাসটুকু নিংড়ে আনে না, আমার দ্বারা লেখা হয় না। খোকা একদিন বললেন, আমার কলামগুলো জড়ো করে একটি বই প্রকাশ করবেন তিনি। শুনে অবাক হই! পত্রিকার এসব কলাম কি সাহিত্য নাকি যে তিনি বই করতে চাইছেন! লজ্জায় মরি! বলি, ‘বলছেন কি! এসব তো প্রতিদিনকার অনুভব নিয়ে, খবর নিয়ে! কি হয়েছে গতকাল, কি হচ্ছে আজ এসব নিয়ে! কদিন পরই এসব সাময়িক ঘটনার ওপর লেখাগুলোর কোনও গুরুত্ব থাকবে না।’ খোকা মাথা নাড়েন, বলেন, ‘তা হোক না, সবই কি আর একরকম! কিছু কিছু তো আবার সবসময়ের জন্য চলে।’ আমি হাতের কাছে যে কটি পত্রিকায় আমার কলাম পেয়েছি, দেখিয়ে পড়িয়ে প্রমাণ দিয়ে বলি যে চলে না। মন কিছুতেই সায় দেয় না এই ভাষায় দুর্বল এমনকী বিষয়ে দুর্বল কলামগুলো নিয়ে কোনও বই করতে। খোকাকে নানাভাবে বোঝাতে চেষ্টা করি, বলি যে বই যদি ছাপতেই চান, তবে কবিতার বই লিখে দিচ্ছি, সেটা ছাপুন। দৈনিক সাপ্তাহিকীর তুচ্ছ বিষয়বস্তু নিয়ে বই করার দুঃসাহস অনুগ্রহ করে দেখাবেন না। আরও একটি বৈষয়িক কারণ দেখাই, কলামের বই কেউ কিনবে না, কারণ সবারই কলামগুলো পড়া হয়ে গেছে। কিন্তু খোকার ইচ্ছে এতই তীব্র যে তিনি পুরোনো পত্রিকা ঘেঁটে ঘেঁটে জড়ো করতে থাকেন কলাম। কী নাম দেওয়া যায় বইএর, তিনি আমার কাছে জিজ্ঞেস করেছেন। কোনও নামই আমার মাথায় আসে না। ভোঁতা মাথার সঙ্গে একদিন শাহরিয়ারের দেখা। বইয়ের নামের প্রসঙ্গ উঠতেই শাহরিয়ার বলল, নির্বাচিত কলাম। নির্বাচিত কলাম? এ কোনও নাম হল? কলাম তো পত্রিকার লেখা, বইএ চলে গেলে কোনও লেখাকে তো আর কলাম বলা যায় না, নিবন্ধ বা প্রবন্ধ বলা যেতে পারে। আমি যুক্তি দেখাই। কিন্তু আমার এসব কলামকে নিবন্ধ বা প্রবন্ধ বলতেও সাহস হয় না। ওগুলোকে অনেক তথ্যভিত্তিক হতে হয়, রীতিমত গবেষণা করে লিখতে হয়। আমার কলামগুলো হালকা, মোটেও ভারী কিছু নয়, এসব আর যা কিছুই হোক কোনও নিবন্ধ বা প্রবন্ধ হয়নি। শেষ পর্যন্ত শাহরিয়ারের কথাই রইল। নির্বাচিত কলাম নামটিই পছন্দ করেন খোকা। লেখাগুলো কলাম হিসেবে পরিচিত হওয়ার কারণেই সম্ভবত তিনি সরাসরি বইয়ের নামে কলাম শব্দটি ব্যবহার করতে চাইলেন। আমি আগ্রহ না দেখালেও খোকা বই বের করলেন। বই হু হু করে চলল, এক মেলাতেই সব বই শেষ হয়ে আবার নতুন মুদ্রণ এল। খোকার মুখ থেকে হাসি সরে না। বইমেলায় বইয়ের বিক্রি দেখে খোকা তো খুশি, আবার বিস্মিতও। তিনিও ভাবেননি, কলামের বইটি এত বিক্রি হবে। আমাকে তাঁর স্টলে বসতে অনুরোধ করেন। বসলে লোকে অটোগ্রাফ নিয়ে বই কেনে। কবিতার বইও দেদার বিক্রি হচ্ছে, মেলাতেই বই বিক্রি সব হয়ে যায়, বই আবার ছেপে আনেন খোকা। কোনও কবিতার বই এরকম বিক্রি হয় না তিনি বলেন। ঢাকার মানুষ তো আছেই, ঢাকার বাইরে থেকেও মানুষ আসে আমাকে এক নজর দেখতে, আমার সই করা বই কেনার জন্য রীতিমত ভিড় জমে যায়। সব কেমন অদ্ভুত লাগে। অবিশ্বাস্য লাগে।
হাসপাতালে ডিউটি না থাকলে অথবা কোনও বিকেলে হঠাৎ হঠাৎ অবসর পেলে সাহিত্যিক যে আড্ডায় আমার যাওয়া হয় সে নীলক্ষেতে অসীম সাহার ইত্যাদির আড্ডা। ওখানেই এক বিকেলে রুদ্রর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়। দুজনে পরস্পরের দিকে তাকাই। দুজনেরই কত না বলা কথা জমে আছে। সেই কতদিন থেকে আমরা আমাদের চিনি, অথচ জানি না কে কেমন আছে। কারও জীবন যাপনের কিছু আমাদের জানা নেই। আড্ডা থেকে উঠে আসার আগে জিজ্ঞেস করি, যাবে আমার সঙ্গে? কোথায় যাব, কি হবে কিছুই না জিজ্ঞেস করে রুদ্র বলে, যাবো। রিক্সা নিয়ে আরমানিটোলার দিকে যাই। পথে রুদ্র আমাকে বলে যে তার চিংড়ির ব্যবসা সে গুটিয়ে নিয়েছে। মিঠেখালিতে বহুদিন ছিল। কবিতা লিখছে, নতুন একটি গান লিখেছে। গানটি সে রিক্সাতেই গেয়ে শোনায়, ভাল আছি, ভাল থেকো, আকাশের ঠিকানায় চিঠি লিখো। হৃদয় স্পর্শ করে গানের প্রতিটি শব্দ। রুদ্রকে নিয়ে আরমানিটোলার বাড়িতে ঢোকার পর সেই বিকেলেই নাইম দরজার কড়া নেড়েছিল।
রুদ্র চোখ মেলে দেখে আমার সুখের সংসারটিকে।
‘কেমন দেখছো আমার সংসার!’ অহংকার আমার গ্রীবায় এসে বসে যখন বলি। রুদ্র বলে, ‘তুমি পারোও বটে।’
‘পারবো না কেন! ইচ্ছে থাকলেই হয়! অনেক আগেই এই ইচ্ছেটি করা উচিত ছিল আমার। নিজের বাড়ি। নিজের টাকা। কেউ নাক গলাবার নেই। কেউ আদেশ দেবার নেই। কি করছি না করছি তা নিয়ে কাউকে কৈফিয়ত দেবার নেই। এর চেয়ে সুখ আর কী আছে, বল!’
সন্ধের পর রুদ্র তখনও ঘরে, মিনার আসে একটি প্রস্তাব নিয়ে, একটি গাড়ি যোগাড় করে ময়মনসিংহে যাচ্ছে সে, যদি আমি যেতে চাই, যেতে পারি। মিনার গল্প লিখত একসময়, এখন বিচিন্তা নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা ছাপে। জানি না কোত্থেকে আমি কোথায় চাকরি করছি তার খবর নিয়ে একদিন টেলিফোন করেছিল হাসপাতালে। গভীর রাতে ফোন করেছে কদিন, নাইট ডিউটিতে তখন রোগী নেই, রোগী না থাকলেও ডিউটির ডাক্তারদের ঘুমোনো ঝিমোনো সব নিষেধ, অগত্যা বসে বসে কথা বলেছি। কথা বলতে ভালও লেগেছে। মিনার সমাজ রাজনীতি এসব নিয়ে কোনও আলোচনায় যায় না।। কেবল হাসির কথা বলে। হাসির গল্প বলে একটি বই আছে, সম্ভবত মিনারের তা মুখস্ত। দেখা করতে এক বিকেলে এসেওছিল আরমানিটোলার বাড়িতে। বলল বহুদিন সে বিদেশে ছিল, বা্রজিলে চলে গিয়েছিল পালিয়ে। তার সেই পাগল করা সুন্দরী স্ত্রী কবিতার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। এখন সে থাকে ইস্কাটনে। সেই মোহাম্মদ আলী মিনার নাম পাল্টো এখন মিনার মাহমুদ, চেকনাই বেড়েছে। গালে মুখে মাংশ, ত্বক আগের চেয়ে উজ্জ্বল।
‘বহু বছর পর দেখা। কেমন আছেন?’
কার্পেটের ওপর বসে চা খেতে খেতে মিনার বলে, ‘হ্যাঁ বহু বছর। আমি তো বেশ ভালই আছি। আপনার এই আস্তানাটি বেশ ভাল বানিয়েছেন তো!’
ঘরটিতে চোখ বুলোই। হ্যাঁ বেশ বানিয়েছি। বাবুই আর চড়ুই পাখির সেই কবিতাটি মনে পড়েছে । বাবুই গর্ব করে বলছে যেমনই তার বাসা হোক সে তো পরের বাসায় থাকছে না, থাকছে নিজের বাসায়।
কবিতা আর মিনারের ছাড়াছাড়ির খবরটি আমার মন খারাপ করে দেয়। তারুণ্যের তেজি ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে দুজনে উল্টো হাওয়ায় ছুটছে দেখতে ভাল লাগত। কেন ছাড়াছাড়ি হল, সমস্যা হলে মীমাংসার তো পথ আছে, কেন মিনার সেটির চেষ্টা করছে না, ইত্যাদি প্রশ্ন করলে খেয়ালি উত্তর জোটে।
‘ঝগড়াঝাটি মিটিয়ে ফেলে কবিতাকে নিয়ে আবার জীবন শুরু করেন।’ পরামর্শ দিই। আমার পরামর্শ মিনার কতটুকু গ্রহণ করে তা বুঝতে পারি না।
মিনারের ময়মনসিংহের প্রস্তাবে আমি রাজি হয়ে যাই, রুদ্রকে জিজ্ঞেস করলে সেও রাজি। রুদ্র আর মিনারেরও দেখা হল বহুকাল পর। দু বন্ধু গাড়ির সামনে বসে। পেছনে আমি, পেছনে একসময় ঝুনুখালাও যোগ হয়, উঠিয়ে নিয়েছি ভূতের গলি থেকে। রুদ্রর সঙ্গে ঝুনুখালারও অনেকদিন পর দেখা হয়। রুদ্রর ইচ্ছে ময়মনসিংহে পৌঁছে একবার ইয়াসমিনের সঙ্গে দেখা করার। গাড়ি জয়দেবপুর পার হয়, ভালুকা পার হয়, ত্রিশাল পার হয়ে গাড়ির চাকা পিছলে রাস্তার মধ্যে উল্টো পাল্টা চককর থেয়ে একেবারে খাদে, না, ঠিক খাদে পড়তে গিয়েই কি কারণে জানি না, খাদের ঠিক কিনারটিতে আটকে যায়। ভেতরে মুত্যর সঙ্গে সকলের একটি সশব্দ মোলাকাত হয়ে যায়। অনেকক্ষণ ঠাণ্ডা হয়ে থাকি গাড়ির সবাই। ঝুনু খালাকে নানির বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে অবকাশের কালো ফটক দেখি ভেতর থেকে তালা দেওয়া, রাত তখন অনেক, এত রাতে ডাকাডাকি করে বাবাকে ঘুম থেকে তুলে তালা খুলিয়ে অবকাশে ঢোকার সাহস হয় না। বাবা আবার এত রাতে কী করে এলাম, কার সঙ্গে এলাম এসব জিজ্ঞেস করে পাগল করে ছাড়বেন, বিশেষ করে গাড়িতে বসা রুদ্রকে যদি চোখে পড়ে, তবে আর আস্ত রাখবেন না। অগত্যা লজ্জার মাথা খেয়ে ইয়াসমিনের শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে ওর ঘরে রাতটুকু পার করে সকালবেলায় অবকাশে যাই। সারাদিন অবকাশে কাটে। সন্ধের পর অবকাশের সামনে গাড়ি এসে থামে, কথা ছিল ঢাকায় ফেরার পথে আমাকে বাড়ি থেকে তুলে নেওয়ার। গাড়িতে উঠতে গেলে রুদ্র বলে, আমি ইয়াসমিনের সঙ্গে দেখা করব। ইয়াসমিন অবকাশেই ছিল। ওকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বলি, ‘রুদ্র আইছে। তর সাথে দেখা করতে চাইতাছে।’
ইয়াসমিন বলে, কেন?
‘কেন মানে? গেটের কাছে দাঁড়াইয়া রইছে। যা, দেখা কইরা আয়।’
‘না।’
‘না কস কেন। কথা কইলে তর ক্ষতি কি?’
‘না আমি যাব না।’
‘আশ্চর্য! ঢাকা থেইকা আইছে, বার বার বলতে বলতে যে ইয়াসমিনের সঙ্গে দেখা করব। আর তুই দেখা করবি না? এত কাছে দাঁড়াইয়া রইছে। একটু কথা কইয়াই যাইব গা। তর অসুবিধাডা কি?’
ইয়াসমিনকে ঠেলেও পাঠাতে পারি না। রুদ্রকে গিয়ে বলি, ‘ইয়াসমিন আসছে না।’
‘আসছে না? বলেছো যে আমি দেখা করতে চাইছি?’
‘বলেছি। তবু আসছে না।’
রুদ্রর মন খারাপ হয়ে যায়। রুদ্রর এই মন খারাপ করা আমাকে কষ্ট দেয়। ইয়াসমিন যে রুদ্রর অনুরোধ ফিরিয়ে দিল তা না বলে আমি হয়ত বলতে পারতাম, ইয়াসমিন এ বাড়িতে নেই বা কিছু। ও এ বাড়িতে নেই, থাকলে দেখা করতে পারত বললে রুদ্রর মন নিশ্চয়ই খারাপ হত না। ফেরার পথে আমাদের খুব বেশি কথা হয়নি। রুদ্র জানালা খুলে বমি করে দুবার। ময়মনসিংহে বসে দুজনেই নাকি পেট ভরে মদ খেয়েছে। মিনার আমাকে আর রুদ্রকে আরমানিটোলায় নামিয়ে দিয়ে চলে যায় যেখানে যাবার।
রুদ্রকে আমিই বলি সে রাতে আমার বাড়িতে থেকে যেতে। আমার বিছানাতেই আমি তাকে শুতে দিই। এক হাতে যখন আমাকে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে, আমি তার হাতটিকে দিই জড়িয়ে ধরতে। যখন সে মুখটি এগিয়ে আনে আমার মুখের দিকে, চুমু খেতে চায়, দিই চুমু খেতে। যখন সে আমাকে আরও কাছে টেনে নিতে চায়, দিই নিজেকে তার আরও কাছে। যখন সে একটু একটু করে আরও ঘনিষ্ঠ হতে চায়, দিই তাকে ঘনিষ্ঠ হতে। যেন সেই আগের রুদ্র, আমি সেই আগের আমি। যেন মাঝখানে বিচ্ছেদ বলে কিছু নেই, কিছু ছিল না। যেন আগের মত আমাদের প্রতিদিন দেখা হচ্ছে। প্রতিদিন আমরা হৃদয় মেলাচ্ছি, শরীর মেলাচ্ছি। রুদ্রর উষ্ণ নিঃশ্বাস, খানিকটা জ্বরজ্বর গা আমার অনেকদিনের শীতল শরীরে উত্তাপ ছড়ায়। রুদ্রর অঙ্গ, অঙ্গ সঞ্চালন সবই এত চেনা আমার! কখন সে হাই তুলবে, কখন সে শোয়া থেকে উঠে বসবে, হাতদুটো ঘাড়ের পেছনে নেবে, কখন সে একটি সিগারেট ধরাবে, কোন কাতে শোবে সে, কটা বালিশ প্রয়োজন হয় তার, কথা বলার সময় কোন হাতটি নাড়বে, কোন আঙুলটি, সব জানা আমার। রুদ্রকে তাই চাইলেও ভাবতে পারি না সে আমার আপন কেউ নয়। বিয়ে নামক জিনিসটিকে অদ্ভূতুড়ে একটি ব্যপার বলে মনে হয়। বিয়ে কি সত্যি কাউকে আপন করে, অথবা বিচ্ছেদই কাউকে পর করে! ইচ্ছে হয় বলি, যতদিন ইচ্ছে থাকো এই বাড়িতে, এটিকে নিজের বাড়ি বলেই মনে কোরো।
‘যদি কখনও ইচ্ছে হয় এখানে আসতে, এসো।’ খুব সহজ কণ্ঠে বলি।
রুদ্র ভাবলেশহীন চোখে তাকিয়ে থাকে।
‘তোমার ওই যে প্রেম চলছিল, সেটি চলছে এখনও?’
রুদ্র শুকনো কণ্ঠে বলে, ‘হ্যাঁ চলছে।’
‘বিয়ে টিয়ে শিগরি করছো নাকি?’
‘করব।’
ম্লান একটি হাসি ঠোঁটের কিনারে এসেই মিলিয়ে যায়। রাতেই আমি রুদ্রর ডান হাতের বুড়ো আঙুলটি দেখি। আঙুলে পচন ধরেছে। কালো হয়ে গেছে আঙুলটি। সকালে হাসপাতালের সার্জারি বিভাগে চেনা এক সার্জনকে দিয়ে পূঁজ আর পচা রক্ত বের করে রুদ্রর আঙুল ব্যাণ্ডেজ করিয়ে নিয়ে আসি। গ্যাংগ্রিনের আভাস দেখেছি আঙুলটিতে। তবে কি ধীরে ধীরে আঙুলে পচন আরও বেশি ধরবে! পুরো হাতটিই তো পরে কেটে ফেলতে হবে। পেরিফেরাল সার্কুলেশনে তা নাহলে বাধা পড়বে। রক্ত জমাট বেঁধে হৃদপিণ্ডের বা মস্তিস্কের রক্তনালী বন্ধ করে না দিলেই হয়। কি বলব রুদ্রকে! অনেক বেশি শান্ত সে আগের চেয়ে। বড় মায়া হয়। ডান হাতটি সে আর ব্যবহার করতে পারছে না। মুখে তুলে রুদ্রকে ভাত খাইয়ে দিই, মুখ ধুয়ে মুছিয়ে দিই।
রুদ্র যখন যাচ্ছে, তার ব্যাণ্ডেজ বাঁধা আঙুলের হাতটি ধরে বলি, ‘যদি কোনও অসুবিধে দেখ, তবে ডাক্তারের কাছে যেও, নয়ত আমার এখানে চলে এসো, আমি তোমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করব। এরকম পচন ধরা কিন্তু ভাল লক্ষণ নয়।’
ডাক্তার প্রেসক্রিপশান লিখে দিয়েছেন। রুদ্রকে বারবার বলি নিয়মিত ওষুধ খেতে। জিজ্ঞেস করি, ‘টাকা পয়সা কিছু আছে?’
রুদ্র মাথা নাড়ে। মাথা নাড়ে, আছে। হাতে চলার মত টাকা থাকলে মুখে বলত, মাথা নাড়ত না। পাঁচশ টাকা দিতে চাই হাতে। হাতটি সংকোচে টাকাটি ছোঁয় না।
টাকার দিকে তাকিয়ে রুদ্র বলে, ‘তোমার লাগবে তো!’
‘সে আমি বুঝবো। তুমি রাখো এটা।’
চুপ হয়ে থাকে রুদ্র। একটু কি সে লজ্জা পায়! বলি, ‘তুমি তো আমাকে অনেক দিয়েছো, আমি না হয় সামান্য কিছু দিলাম।’
টাকাটি রুদ্রর সার্টের বুকপকেটে পুরে দিই। রুদ্র চলে যায়।
পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা আমার চোখে দু ফোঁটা জল। আবার কখন কোথায় দেখা হবে অথবা আদৌ দেখা হবে কি না আমাদের তা আমরা দুজনের কেউই জানি না।
বাড়িঅলা নোটিশ পাঠান, আমাকে বাড়ি ছাড়তে হবে। এই আশঙ্কা আমি আগেই করেছিলাম। যেদিন নাইম এসে দরজা ধাককালো, সেদিনই আশঙ্কার অঙ্কুরটি গেঁথে যায় মনে। ডালপালা ছড়িয়ে বড় হওয়ার আগেই নোটিশ। খোকার দ্বারস্থ হয়েছিলাম নাইমের গন্ধ পেয়েই। খোকা বাড়ি খুঁজতে শুরু করেছেন। যেখানেই যান, আবারও একই সমস্যা, একা একটি মেয়ে থাকবে, বিয়ে শাদি হয়নি? স্বামী নেই? একা মেয়ে কি করে থাকে বাড়িতে? মেয়ে ডাক্তার। ডাক্তার হয়েছে তাতে কি! স্বামী থাকতে হবে। স্বামীহীন মেয়ে ডাক্তার হোক কী ইঞ্জিনিয়ার হোক কী বিজ্ঞানী হোক, কী পতিতা হোক, এক। মেয়ে হল জ্বলজ্যান্ত ঝামেলা। খোকা বাড়ি খুঁজতে খুঁজতে বাড়িঅলাদের বিদ্রুপ, চোখ কপালে তোলা, আকাশ থেকে পড়া, ভ্রুকুঞ্চন, নাসিকাকুঞ্চন, কপালের ভাঁজ, চু চু চু, অপারগতা ইত্যাদি দেখতে থাকেন, শুনতে থাকেন। ভাড়ার জন্য কোনও বাড়ি পাওয়ার আগেই দুর্ঘটনাটি ঘটে যায়। সে রাতে মা ছিলেন না বাড়িতে, মা ময়মনসিংহে। সে রাতে মিনার এল। ময়মনসিংহে গাড়ি করে নিয়ে গিয়েছিল, আমার তো কিছু করতে হয় তার জন্য, তাই নেমন্তন্ন করেছিলাম রাতের খাবারের। হাতে তিনটি বিয়ারের কৌটো নিয়ে এসেছে। বিয়ার শেষ করে সে খাবার খাবে। মিনার বসে বিয়ার খেতে থাকে, আমি যেহেতু বিয়ার পানে অভ্যস্ত নই, এক কাপ চা নিয়ে বসে বসে মিনারের গল্প শুনি। এই মিনারকে দেখলে আমার একটুও মনে হয় না এ সেই আগের মিনার যাকে চিনতাম। যেন এ সম্পূর্ণ নতুন একজন মানুষ। আগের চেয়ে আরও ভদ্র, নম্র, আরও প্রাণবান, আরও গভীর। মিনারের বিয়ার তখনও শেষ হয়নি, তখনই দরজায় শব্দ। দরজায় বাবা আর দাদা দাঁড়িয়ে। দরজা থেকেই বাবা মিনারের দিকে এমন কটমট করে তাকালেন যে আমি মিনারকে বললাম চলে যেতে। না খেয়ে চলে গেল বেচারা। আমার খুব আনন্দ হয় দুজনকে দেখে। এই প্রথম তাঁরা আমার বাড়িতে এলেন। এই প্রথম আমি সুযোগ পাচ্ছি বাবাকে আমার স্বনির্ভর জীবনটি দেখাবার। তাঁরা কি কোনও কাজে এসেছেন ঢাকায়! রাত হয়ে গেছে বলে ময়মনসিংহে ফিরতে পারেননি! নাকি আমাকেই দেখতে এসেছেন! আমি কেমন আছি দেখতে, আমার চাকরি বাকরি কেমন চলছে দেখতে, নিজের বাড়িটি কেমন সাজালাম দেখতে! নাকি এফসিপিএস এর জন্য পড়াশোনা শুরু করেছি কি না দেখতে! নাকি আমার কোনও অর্থনৈতিক অসুবিধে আছে কি না জানতে! জানলে আমাকে সাহায্য করবেন! বাবা কোনও কিছুই বলেন না। উৎসুক বসে থাকি বাবার কথা শোনার জন্য। লিলিকে বলে দিয়েছি শিগরি ভাত চড়াতে। ভাত রাঁধা হলে হলে ভাত দেওয়া হয় টেবিলে। কিন্তু দুজনের কেউই খাবেন না। দুজনেরই মুখ ভার। কেউ কোনও উত্তরও দেন না আমার কোনও প্রশ্নের। বাবা জিজ্ঞেস করেন, ‘যে লোকটি ঘরে ছিল, সে কে?’ প্রশ্নটি বাবা দাদাকে করেন। দাদা আমার দিকে তাকান। আমি বলি, ‘মিনার, বিচিন্তা পত্রিকার সম্পাদক।’ বাবা দাদার দিকে প্রশ্ন চোখে তাকান। দাদা নরম স্বরে বলেন, ‘নাম মিনার, বিচিন্তা পত্রিকার সম্পাদক।’
‘কেন আইছিল এই বাসায়?’ প্রশ্নটি দাদাকে করা হয়। দাদা আমাকে জিজ্ঞেস করেন, ‘ওই লোক কেন আইছিল?’ আমি বাবার দিকে তাকিয়ে উত্তর দিই, ‘এমনি।’ দাদা বাবাকে বলেন, ‘এমনি।’
‘ওই লোকের সাথে তার সম্পর্কটা কি?’ বাবা দাদাকে জিজ্ঞেস করেন।
দাদা আমাকে জিজ্ঞেস করেন, ‘ওই লোকের সাথে তর সম্পর্ক কি?’
আমি কাঁধ নাড়িয়ে বলি, ‘জাস্ট ফ্রেন্ড।’
দাদা বাবাকে বলেন, ‘জাস্ট ফ্রেন্ড।’
টেবিলে ভাত তরকারি ঠাণ্ডা হয়ে যায়। বাবা বারান্দায় হাঁটাহাঁটি করেন। আর ক্ষণে ক্ষণে দাদাকে ডেকে পিলপিল করে কথা বলেন। কী কথা, আমার সাধ্য নেই বুঝি। কাপড় চোপড় পাল্টাতে হবে তো! দুজন এসেছেন খালি হাতে, কোনও লুঙ্গি গেঞ্জি আনেননি। আমার শাড়ি দেব নাকি লুঙ্গির মত করে পরতে! বাবা দাদার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়েন। না, তিনি কাপড় পাল্টাবেন না। রাতে খাটের বিছানায় যেখানে আমি আর মা ঘুমোই, নতুন চাদর বিছিয়ে দিই দাদা আর বাবার জন্য। ও বিছানায় বাবা বললেন ঘুমোবেন না। কোথায় ঘুমোবেন? তা নিয়ে নাকি আমাকে ভাবতে হবে না। কিছুতেই রাজি হলেন না বিছানায় যেতে! আমি বড় বিছানায় একা রানীর মত শুয়ে থাকব আমি আর নিজের বাবা আর দাদা কার্পেটে শোবেন! দুজনকে ঠেলে যে পাঠাবো বিছানায়, তাও সম্ভব নয়। তাঁরা লোহার মত হয়ে আছেন, শরীরেও, মনেও। খাটে দুটো তোশক নেই যে একটি এনে কার্পেটে বিছিয়ে দেব। বিছানার একটি চাদর দিই পেতে শোবার। কিন্তু বাবা শোবেন না। কি করবেন সারারাত? বসে থাকবেন। দাদাও বসে থাকবেন বাবার সঙ্গে। বাবার হাতে একটি সুগন্ধা। সুগন্ধার মত নিম্নরুচির পত্রিকা বাবা কবে থেকে পড়ছেন, তা জানি না। সুগন্ধা মৌলবাদী গোষ্ঠীর পত্রিকা। একে তাকে গালাগাল, যৌনতা, মিথ্যে সংবাদ, রটনা, ফালতু আলাপ, যা কিছু হলুদ সাংবাদিকতার জন্য প্রয়োজন, সুগন্ধায় সব কিছুর দুর্গন্ধ আছে। শেষ অবদি অনেক রাতে লোহা গলাতে না পেরে আমি শুতে যাই বিছানায়।
সকালে উঠে যখন আমি হাসপাতালে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছি, দেখি বাবা আর দাদা কাপড় চোপড় পরে তৈরি, তাঁরাও যাবেন। কোথায়? ময়মনসিংহ। আজ থেকে গেলে হয় না? বললেন, হয় না। ঠিক আছে। তারা বললেন কিছুই ঠিক নেই। আমাকে এখন তাঁদের সঙ্গে ময়মনসিংহে যেতে হবে। ময়মনসিংহে কেন? যেতে হবে। যে করেই হোক যেতে হবে। পাগল নাকি! হেসে ফেলি। হাসপাতালের গাইনি ওয়ার্ডে আমার ডিউটি, আজকে রোগী ভর্তির দিন, এক্ষুনি যেতে হবে। বাবা বললেন, না যেতে হবে না। মানে? মানে আমার আর হাসপাতালে যেতে হবে না। আমার আর চাকরি বাকরি করতে হবে না। আমাকে এক্ষুনি এই মুহূর্তে তাঁদের সঙ্গে ময়মনসিংহে যেতে হবে। আমি বলি, আমি যাবো না। যাবো না বলে যেই না ঘুরে দাঁড়িয়েছি, বাবা চিৎকার করে বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়েন আমার ওপর। এমন জোরে চড় লাগান গালে যে মনে হয় ঘাড় থেকে যেন ছিটকে পড়ল মাথাটি। ভয়াবহ চড়গুলো আমার মাথায় মুখে মিনা-পর্বতে হাজীদের ছোঁড়া পাথরের মত পড়তে থাকে। বাবা ধাককা দিয়ে আমাকে মেঝেয় ফেলে লাথি কষাতে থাকেন পিঠে পেটে। দৌড়ে গিয়ে বিয়ারের ক্যানগুলো এনে ছুঁড়ে মারেন আমাকে লক্ষ্য করে, কপালে লেগে কপাল কেটে যায়। ঠোঁটে লেগে ঠোঁট কেটে যায়। রক্ত ঝরতে থাকে। দূর থেকে ছুটে এসে আমার চুল ধরে টেনে উঠিয়ে আবার ধাককা দিয়ে ফেলেন আলমারির দরজায়। ধরাম করে মাথাটি গিয়ে পড়ে আয়নায়। আয়নার মুখটিতে চোখ যায়, দেখি কপালের আর ঠোঁটের রক্ত ঝরা। বাবার এমন আগুন হওয়ার কি কারণ থাকতে পারে আমি তার কিছুই জানি না। আমি হতবুদ্ধির মত চেয়ে থাকি। কাঁপতে কাঁপতে গা শিথিল হয়ে আসে, যেন জ্ঞান হারাচ্ছি। আমার দিকে বাবা ছুঁড়ে দেন সুগন্ধা পত্রিকাটি। পত্রিকাটি আমার গায়ের ওপর পড়ে থাকে। দাদা ওটি তুলে নিয়ে পাতা খুলে মেলে ধরেন আমার সামনে, বলেন, ‘লেখছে তর সব কাহিনী। কি করতাছস সব লেখছে।’ কে আমার কি কাহিনী লিখেছে আদৌ দেখার ইচ্ছে হয় না। মনের শক্তিতে উঠে দাঁড়াই। অ্যাপ্রোনটি হাতে নিয়ে দরজার দিকে যেতে থাকি। বাবা দৌড়ে এসে দরজা ধরে দাঁড়ান।
‘হাসপাতালে যাইতে হইব আমার। দেরি হইয়া যাইতাছে।’ শক্ত গলায় বলি।
তর কোথাও যাইতে হইব না। আমার চেয়ে দ্বিগুণ শক্ত গলায় বলেন বাবা।
আমি চিৎকার করে উঠি, ‘হইব। আমার যাইতে হইব।’ বলতে গিয়ে দেখি গলা কাঁপছে আমার। কান্নায় কাঁপছে।
বাবার রক্তচোখের দিকে তাকানো যায় না, চোখ ঝলসে যায় আমার। আমার যেতে চাওয়াকে তিনি টেনে এনে ছুঁড়ে ফেলে দেন। যেতে চাওয়া কাতর অনুনয় জানায়। বাবা যে আমার হাসপাতালের ডিউটিতে যাওয়ার পথ রোধ করে জীবনে কখনও দাঁড়াতে পারেন, আমার বিশ্বাস হয় না। এই বাবার মুখ দিয়ে কখনও যে উচ্চারিত হতে পারে যে আমার চাকরি করতে হবে না, তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। অকল্পনীয় সব ব্যপার চোখের সামনে ঘটতে থাকে। হঠাৎ আমার মনে হয়, এ সত্যি নয়, এরকম ঘটনা সত্যি সত্যি ঘটতে পারে না। এ নিশ্চয়ই দুঃস্বপ্ন। নিশ্চয়ই আমি ঘুমিয়ে আছি, আর স্বপ্নের ভেতর দেখছি অবিশ্বাস্য সব কাণ্ড। ঘুম ভাঙলেই দেখব আমি ধবল বিছানায় শুয়ে, জানলা গলে পূর্ণিমার রং এসে গা ঢেকে দিয়েছে।
আমার কোনও প্রতিবাদ টেকেনি। সুগন্ধা পত্রিকার লেখাটি মিথ্যে এ কথা যতবারই বলি বাবা ধমকে ওঠেন। হাতে নাতে তিনি এক লোককে ধরেছেন আমার ঘরে, রাতে। এর চেয়ে বেশি কী আর প্রমাণ তাঁদের দরকার! অবশ্য এই প্রমাণটি না পেলেও দুজনে ময়মনসিংহ থেকেই পরিকল্পনা করেই এসেছেন কী করবেন। বাবা আর দাদা আমাকে টেনে হিঁচড়ে নিচে নামান। লিলিকেও নামান দরজায় তালা দিয়ে, চাবি বাবার পকেটে। নিচে অপেক্ষা করে থাকা একটি ভাড়া গাড়িতে আমাকে তোলেন। গাড়ি ময়মনসিংহে পৌঁছে। আমার মন পড়ে থাকে ঢাকায়। মন পড়ে থাকে আমার সুখের সংসারে। পড়ে থাকে হাসপাতালে, আমার অনুপস্থিতি নিয়ে তুলকালাম হচ্ছে নিশ্চয়ই। গাইনি বিভাগের সব ডাক্তারদেরই চোখে পড়ছে আমি নেই। নামটিতে একটি লাল দাগ পড়ছে। নামটিতে একটি ভ্রুকুঞ্চন এসে যোগ হচ্ছে। এই যে ভীষণ উদ্দীপনায় কাজ করছি হাসপাতালে, এতে রোগীর সেবা যেমন হচ্ছে, বিদ্যেটিও আমার আবার হাতে কলমে শেখা হচ্ছে। শেখার, শেখানোর এই উৎসাহই আমাকে নিয়ে যেতে পারত এফসিপিএসের দিকে। এফসিপিএস বড় সংক্রামক, কেউ একজন পড়ছে দেখলে নিজের ভেতর ইচ্ছে জাগে পড়ার। বাবা কি সত্যি সত্যি আমার সমস্ত সম্ভাবনার গলা জবাই করছেন! ভাবতে পারি না।
অবকাশে পৌঁছলে ঘাড় ধরে আমার ঘরটির দিকে আমাকে ঠেলে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন বাবা। বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে দিলেন দরজায়। ওপাশে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলতে থাকেন, ‘এখন এইভাবে এই ঘরে তর সারাজীবন কাটাইতে হইব। তর বাইরে যাওয়া বন্ধ। চাকরি বাকরির খেতা পুরি। ডাক্তারি করতে হইব না। পাখনা গজাইছে তর। তর পাখনা আমি পুড়াইয়া দিতাছি।’
সুগন্ধায় আমাকে নিয়ে লেখাটির শিরোনাম ছিল তসলিমা নাসরিন এখন উড়ে বেড়াচ্ছেন। উড়ে বেড়াচ্ছি আমি আজ এর সঙ্গে, কাল ওর সঙ্গে। আমাকে রিক্সায় দেখা গেছে আজ লম্বা মত কালো মত এক ছেলের সঙ্গে, কাল ফর্সা মত মোটা মত এক লোকের সঙ্গে ইত্যাদি। আমি মধূ আহরণে ব্যস্ত ইত্যাদি। সুগন্ধার মত পত্রিকার এই কড়া হলুদ লেখাটি আমার সুখের সংসার ধূলিসাৎ করে দিতে পারে, এত শক্তি এর। ছাপার অক্ষরে বাবার প্রচণ্ড বিশ্বাস। যে কোনও কাগজে যা কিছই লেখা থাকে, তিনি তা বিশ্বাস করেন।
সেদিনই ঢাকায় লোক পাঠিয়ে আরমানিটোলার বাড়িতে যা কিছু ছিল সব ট্রাকে তুলে ময়মনসিংহে নিয়ে এসেছেন বাবা। জানালা দিয়ে দেখি উঠোনের কাদা মাটিতে আমার বড় শখের বড় সুখের সংসারের জিনিসপত্র পড়ে আছে। বন্ধ ঘরটির তালার চাবি বাবার বুক পকেটে। আমাকে খাবার দিতে হলে মা বাবার কাছ থেকে চাবি নিয়ে তালা খুলে ভেতরে ভাত রেখে চলে যাবেন, দরজা তালা বন্ধ করে। বাবা এই নিয়ম করে দিয়েছেন। ভেতরে একটি বালতি দেওয়া হয়েছে। ওতে আমার পেচ্ছ!ব পায়খানা বমি কফ থুতু সারতে হবে। পছন্দ না করলেও বাবার নিয়মে চলতে হয় মার। দরজার ওপাশ থেকে মাঝে মাঝে আমার উদ্দেশ্যে সবাই ঘেউ ঘেউ করেন। মাও গলা চড়ান, ‘বালাই ত আছিলি। ব্যাডাইনগর সাথে না মিশলে কী হয়! পত্রিকায় এইসব লেখা উডে কেন? কত মেয়ে আছে, চারদিকে কত মেয়েরা ডাক্তারি করতাছে। সুন্দর ভাবে থাকতাছে। তর জীবনে ত তা আর হইল না। বিয়া যদি না করতে চাস, বালা কথা। কত মেয়ের জামাই মইরা গেছে অথবা বিয়াই করে নাই, তারা একলা থাকে না? তাদের নামে ত এইসব লেখা হয় না। মেয়েদের কথা এত লেখস, ব্যাডাইনগর বদনাম এত লেখস, ব্যাডাইন ছাড়া বাছস না কেন?’