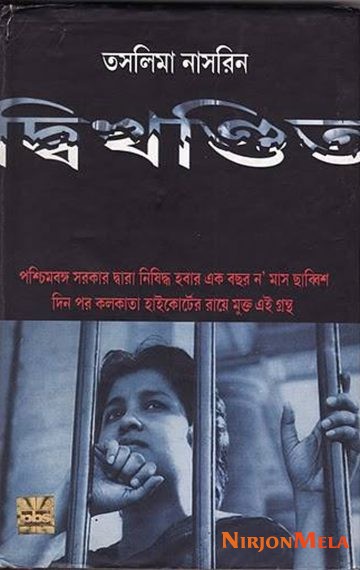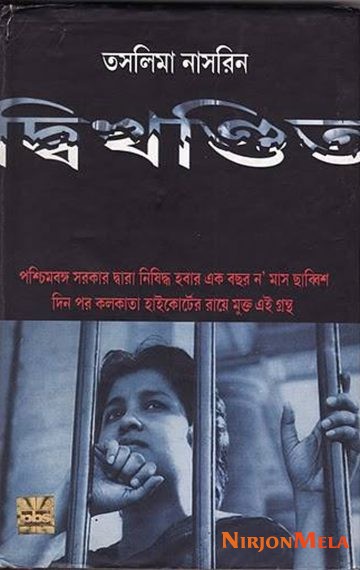০৬. অন্য ভূবন
১৯৮৯ সালে অনেক কিছু ঘটে। অনেক ভাল কিছু, অনেক মন্দ কিছু । কিছু ঘটে আবার ভালও নয়, মন্দও নয়। সকাল প্রকাশনী থেকে গাঁটের পয়সা খরচ করে নির্বাসিত বাহিরে অন্তরে নামে নিজের একটি কবিতার বই বের করা পড়ে ভালও নয় মন্দও নয় তালিকায়। আজকের এই সকাল কবিতা পরিষদ গড়ার আগে সকাল নামে একটি প্রকাশনী গড়েছিলাম। প্রকাশনীর প্রথম বই যেটি বের করেছিলাম, সেটি কবি আওলাদ হোসেনের কাব্যনাট্য। আওলাদ হোসেনের কথা বলতে গেলে সময় দুবছর পিছিয়ে নিতে হয়। তখন সবে চাকরি হয়েছে ময়মনসিংহ শহরে। নকলা স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে দু সপ্তাহের মাথায় যাদুর মত বদলি হয়ে ময়মনসিংহ শহরে। কলেজের বন্ধুবান্ধবীরা নতুন চাকরিতে দেশের আনাচ কানাচে ছড়িয়ে গেছে। রুদ্র চিংড়ির ঘের নিয়ে ব্যস্ত মোংলা বন্দরে। কদাচিৎ ঢাকায় ফেরে।
তুমি যখন একা, তুমি যার তার সঙ্গে মেশো। তুমি আওলাদ হোসেনের সঙ্গে মেশো। আওলাদ হোসেনকে বড়জোর তুমি দুবার দেখেছো এর আগে, ঢাকায়। আওলাদ কবিতা লেখেন। কবিতা তুমি ছেপেছোও তোমার সেঁজুতি পত্রিকায়। রুদ্র পাঠিয়েছিল বেশ কিছু তরুণ কবির কবিতা, আওলাদ তার মধ্যে একজন। আওলাদের বাড়ি সিরাজগঞ্জে। বিশ্ববিদ্যালয় শেষ করে বিসিএস পাশ দিয়ে রুদ্রর বেশ কিছু বন্ধু, কবিতা বা গল্প লেখায় ইতি টেনে, লম্বা চুলের সর্বনাশ ঘটিয়ে ভদ্র কাট কেটে, স্যুটেড বুটেড ক্লিন শেভড হয়ে, মদ গাঁজা ভাংএর দুর্গন্ধ দূর করে মুখে গম্ভীর গম্ভীর ভাব এনে রীতিমত ভদ্রলোক সেজে ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিযুক্ত হয়েছেন। ইকতিয়ার চোধূরী, কামাল চৌধুরী, আওলাদ হোসেন, মোহাম্মদ সাদিক, ফারুক মইনুদ্দিন..। তুমি যখন সার্কিট হাউজের মাঠে সকালবেলা আন্তঃ জেলা খেলা প্রতিযোগিতায় গেছো, খেলা দেখতে নয়, চিকিৎসা করতে খেলতে গিয়ে চোট লাগা খেলোয়ারদের, তখন পেছন থেকে কেউ একজন তোমাকে ডাকল। কে ডাকল দেখতে যেই না ঘাড় ঘোরালে, দেখলে মিষ্টি মিষ্টি হাসি মুখে দাঁড়িয়ে থাকা স্যুটেড বুটেড পরিপাটি চুলের একটি লোক। তাকে তুমি চিনতে পারো। শ্রীমান আওলাদ হোসেন।
আপনি এখানে?
হ্যাঁ, আমি তো এখানে চাকরি করি। তথ্য অফিসার হয়ে এই কিছুদিন হল এই শহরে এসেছি। তা আপনার খবর কি? রুদ্র কোথায়, কেমন আছে?
আমি এখানে চাকরি করছি। রুদ্র কোথায়, কেমন আছে, জানি না।
আওলাদ হোসেন গুলকিবাড়িতে তাঁর তথ্য অফিসে তোমাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে দু গাল হাসলেন।
এরপর ইয়াসমিনকে নিয়ে প্রতিদিনকার অভ্যেসমত রিক্সা করে শহর চক্কর দিতে দিতে কোনও এক বিকেলবেলা গুলকিবাড়িতে আওলাদ হোসেনের তথ্য অফিসে ঢুঁ দিয়ে এসো। বড় একটি মাঠ নিয়ে হলুদ একটি একতলা বাড়ি। আওলাদ হোসেন অফিসের খাতাপত্তর গুটিয়ে রুদ্রর সঙ্গে তোমার সম্পর্কের সমাপ্তির কথা শুনলেন। নিজের কথা বলতে তাঁর কবিতার কথাই বললেন বেশি। কাব্য নাট্য লিখেছেন। সেটি নিয়ে তিনি খুব আশাবাদী। তিনি যে করেই হোক এটি ছাপতে চান। রুদ্র আওলাদ হোসেনের কবিতার খুব প্রশংসা করত। নিশ্চয়ই ভাল লিখেছেন তিনি। ডাক্তারির বাইরে আর কিছু করার না থাকলে তুমি তাই কর, একটি কবি-সংগঠন গড়ে তোলার কথা ভাবো, কবিতা পত্রিকা বের করার ইচ্ছে বুদবুদ করে, এমনকি পুস্তক প্রকাশনার কাজেও হাত দিতে হাত নিশপিশ করে। তুমি এখন উপার্জন কর, মাস গেলে মাইনে পাও, বাপের হোটেলে থাকছ, খাচ্ছ, নিজের টাকা পয়সা খরচ হতে থাকে শিল্প সাহিত্যের সেবায়। আহ, যেন শিল্প সাহিত্য কোনওরকম অসুস্থ ছিল যে তোমার সেবা প্রয়োজন! রোগীর সেবা কর হে বাপু, সাহিত্য বাদ দাও। বাদ দাও বললে বাদ দেওয়া যায় না। পুরোনো শখের শেকড় নতুন ঘটির জল পাচ্ছে। জল পাচ্ছে বলে ঢুঁ মেরে একদিন আওলাদ হোসেনের শখের কাব্য নাট্য নিয়ে জমান প্রিন্টার্সে দিয়ে এসো। আওলাদ হোসেন কথা দেন তিনিই বই বিক্রির ব্যবস্থা করবেন। কাব্য নাট্যটির আগা গোড়া কিছুই না বুঝে তুমি দিব্যি বই বের করে দিলে। তোমার প্রকাশনীর নাম সকাল। সকাল বলে এখন কেউ তোমাকে ডাকে না আর। তুমিই নিজেকে মাঝে মাঝে হঠাৎ হঠাৎ সকাল বলে ডেকে ওঠো। এই সকালে কোনও রোদ নেই। মেঘ মেঘ অন্ধকারে ডুবে আছে তোমার সকাল। সকাল প্রকাশনী থেকে বন্দী দেবতা ছেপে বের করলে নিজে প্রুফ দেখে, গাঁটের পয়সা খরচা করে। আওলাদ হোসেন বলেছিলেন, দুশ বই তিনি নিজেই কিনে নেবেন। কোথায়! দুশ বই আওলাদ হোসেনকে দিলে, তিনশ বই তোমার খাটের তলায়। রুদ্র ময়মনসিংহে বেড়াতে এলে তাকেও কিছু বই দিলে বিক্রি করতে, আওলাদ হোসেনের হলুদ আপিস-বাড়িতে নিয়ে গেলে রুদ্রকে, দু বন্ধুর দেখা করাতে। কিন্তু দেখা তো হল, দেখা হয়ে রুদ্র কি মোটেও সুখ পেয়েছে! পায়নি। বরং সে ঢাকায় ফিরে গিয়ে ইতর নামে ইতরের মত একটি গল্প লিখেছে। সেই ইতরে সে সন্দেহ করেছে যে তুমি যার তার সঙ্গে শুয়ে বেড়াচ্ছে!, আওলাদ হোসেনের সঙ্গেও তোমার সেরকম সম্পর্ক। আসলে তুমি জানো, তুমি কারও সঙ্গে শোওনি। তুমি নিজে জানো যে আওলাদকে নিতান্তই একজন বন্ধু ছাড়া অন্য কোনও ভাবে তুমি দেখ না। তুমি কখনও কল্পনাও করোনি আওলাদের সঙ্গে এই বন্ধুত্বের বাইরে তোমার আর কোনও রকম সম্পর্কের কথা। বরং আওলাদকে বন্ধু বলতেও দিনদিন তোমার আপত্তি হচ্ছে, তাঁর অদ্ভুত আচরণ যে তুমি লক্ষ্য করছ না এমন নয়, করছ। লোকটি উদাসীন, আবার উদাসীনও নয়। কী এক দুর্ভেদ্য ঘোরের মধ্যে থাকেন তিনি। কখনও অনর্গল কথা বলেন, কখনও কোনও কারণ ছাড়াই হেসে ওঠেন, হারমোনিয়ামে মরমিয়া সব সঙ্গীতের সূর তোলেন, আবার কখনও একেবারে চুপ, কোনও কিছুই তাঁর নিমগ্নতা ভাঙতে পারে না। এই আছেন তিনি, এই নেই। আপিসের গাড়ি করে দূর দূরান্তে চলে যাচ্ছেন। গাড়ির চালককে রাতভর খাটাচ্ছেন, কখনও আবার খুব হাসিমুখে চালকের পকেটে টাকা গুঁজে ছুটি দিয়ে দিচ্ছেন। এক আওলাদ হোসেনের অনেকগুলো চরিত্র। কোনটি আসল, তা তুমি বুঝতে পারো না। ক্রমে ক্রমে তুমি আবিষ্কার করছ যে শম্ভুগঞ্জের এক পীরের কাছে তিনি ঘন ঘন যাচ্ছেন, পীরের সংসারে টাকা পয়সা ঢালছেন, পীরের সঙ্গে বসে গাঁজা খাচ্ছেন। তুমি লক্ষ্য করছ যে আপিসে লোকটি দিন দিন অপ্রিয় হয়ে উঠছেন। নিজের সহকর্মীদের সঙ্গে মোটেও সম্পর্ক মধুর রাখতে পারছেন না তিনি। আওলাদ হোসেনের আপিসের সমস্যা তুমি সমাধান করতে পারো না, কিন্তু একটি সমস্যার সমাধান করতে চাইলে, যখন তাঁর রাঁধা বাড়া করার জন্য ষোল বছরের মরিয়মের সঙ্গে সত্তর বছরের এক বুড়োর বিয়ে ঠিক করলেন তিনি। বুড়োটি আপিসেই পিয়নের কাজ করে। আওলাদ হোসেনের বক্তব্য দুজনে চুটিয়ে প্রেম করছে, করছে যখন, তখন তিনি ধুমধাম করে বিয়ে দেবেন। চাইলেও তোমার পক্ষে বিয়েটি বন্ধ করা সম্ভব হয়নি। মরিয়মকে আলাদা করে ডেকে নিয়ে তুমি জিজ্ঞেসও করেছো, কী কারণ এই বুড়োকে বিয়ে করার। মরিয়ম হেসেছে, প্রেমিকারা যেমন করে লাজরাঙা হাসি হাসে তেমন করে। তোমার বিশ্বাস হয়নি মরিয়ম আর আবদুল হামিদ নামের ফোকলা বুড়োর মধ্যে কোনও প্রেম ছিল। সম্ভবত বুড়োর কিছু টাকা আছে আর এক টুকরো জমি আছে, তাই সহায় সম্বলহীন মরিয়মের বাবা এই বিয়েতে রাজি হয়েছেন, মেয়ে খেয়ে পরে বেঁচে থাকবে, এই আশায়। বিয়েতে বাধা দেওয়া তোমার পক্ষে সম্ভব হল না। নাতির বয়সী মেয়ের সঙ্গে আবদুল হামিদের বিয়ে দেখে এলে, খেয়ে এলে। আওলাদ হোসেনকে তখন থেকে তোমার মনে হয় যেন তিনি কিছু আড়াল করছেন। লোকটি তাঁর রহস্য কোনওদিন ভাঙেন না। ধোঁয়া ধোঁয়া কিছুর আড়ালে তিনি অনড় মূর্তির মত। একদিন তুমি এও জানবে যে আওলাদ হোসেন তাঁর বউকে মেরে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। ছেলে মেয়ে নিয়ে বউ চলে গেছে সিরাজগঞ্জ। অল্প বয়সে চমৎকার গান গাইত এক মেয়েকে তিনি বিয়ে করেছিলেন। বাচ্চা কাচ্চাও হয়ে গেছে আর সব বন্ধুদের চেয়ে অনেক আগেই। প্রায়ই যখন তুমি বউ ছেলে মেয়ে কেমন আছে জিজ্ঞেস কর, আওলাদ হোসেন ওদের খবর জানেন না বলে জানিয়ে দেন। তিনি কোনও টাকা পয়সাও পাঠান না ওদের জন্য। তুমি লক্ষ্য কর, ওদের জন্য লোকটির মোটেও কোনও মায়া হয় না। বউ তাঁর অবাধ্য হয়েছিল বলে তিনি শাস্তি দিয়েছেন। তিনি স্বামী, তিনি সে ক্ষমতা রাখেন। তিনি কবি, তিনি ভাবুক, তিনি এই, তিনি সেই। তিনি লাটসাব, তিনি জমিদার। জমিদারের খবর নিতে তুমি আগ্রহ হারাতে থাকো। না দেখা বউটির জন্য তোমার খুব মায়া হতে থাকে। তুমি বউটির কষ্ট অনুভব করতে থাকো। বছর চলে যায়, তুমি সকাল কবিতা পরিষদ নামে একটি সংগঠন গড়ে তুললে আর শহরের কবি আর আবৃত্তিকাররা যোগ দিচ্ছে তোমার সংগঠনে, এই সংগঠনে আওলাদ হোসেনকে যুক্ত করতে পারলে মন্দ হয় না, একজন কেউ প্রস্তাব করার পর তুমি খোঁজ নিয়ে দেখলে আওলাদ হোসেন আর ক্লিন শেভড স্যুটেড বুটেড ভদ্রলোক নন। তিনি শম্ভুগঞ্জে পীরের আসরে গাঁজা টেনে টেনে, পীরকে টাকা পয়সা যা ছিল সব দান করে এখন সর্বস্বান্ত। চাকরিটিও গেছে। মাথা পাগল লোক। খালি পায়ে হাঁটেন। ময়লা কাপড়চোপড়। চুল দাড়িতে মুখ ঢেকে গেছে। আরোগ্য বিতানে নেমে তোমার দাদার কাছ থেকে দু পাঁচ টাকা ভিক্ষে চান। তোমার কাছেও এলেন একদিন টাকা চাইতে। মায়া হল বলে দিলে। আওলাদ হোসেন বগলতলায় একটি বড় বাঁধাই খাতা নিয়ে ঘোরেন আর বলেন তিনি চমৎকার একটি কাব্যনাট্য লিখেছেন, এটি ছাপা হলে, তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, পৃথিবীতে হৈ চৈ পড়ে যাবে। আওলাদ হোসেনকে দেখে সত্যিই খুব মায়া হয় তোমার। সিরাজগঞ্জের জমিদারপুত্র আওলাদ হোসেন ফার্স্ট ক্লাস গেজেটেড অফিসার থেকে এক বছরের মধ্যে এখন পথের ভিখিরি। যে মানুষ শখ করে নিজের এমন সর্বনাশ করেছে, তুমি কী ইবা করতে পারো তাঁর জন্য! কিছুই না। তুমি সিদ্ধান্ত নাও এই লোকের জন্য তোমার দরজা আর তুমি খুলবে না, লোককে টাকাও আর দেবে না। টাকা পয়সা অন্য খাতে ঢালা বরং ভাল।
ভালও নয়, মন্দও নয় কাজটি করার ভার তারিক সুজাত নেয়। তারিকের অল্প বয়স, তার ওপর বাচ্চা বাচ্চা মুখ। জাতীয় কবিতা পরিষদ গড়ার সময় যে সব তরুণ কবি দিন নেই রাত নেই দৌড়োদৌড়ি করেছে, তারিক সুজাত তাদের মধ্যে একজন। পরিষদ গঠন করা, বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনের চৌরাস্তায় মঞ্চ সাজিয়ে বিরাট করে জাতীয় কবিতা উৎসব করার সেই উত্তেজিত উদ্দীপ্ত সময়ে তারিক সুজাত মোজাম্মেল বাবু শিমুল মোহাম্মদ এমন আরও তরুণ কবির সঙ্গে আমার আর রুদ্রর ঘনিষ্ঠতা বেড়েছিল। রুদ্রর সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি ঘটছে যখন, যখন সম্পর্কটি যায় যায় যাচ্ছে যাচ্ছে অথবা গেছে, তখনও এদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ হত। মোজাম্মেল বাবু প্রকৌশলী হয়েও কৌশলে প্রকৌশলে পা না বাড়িয়ে শৈলী নামে একটি পাক্ষিক সাহিত্য পত্রিকা বের করছে। শৈলীর আপিস স্টেডিয়ামের দোতলায়। সাহিত্যের নেশায় বৈষয়িক জগত থেকে মুখ ফিরিয়েছে বাবু। ধনী বাবার ছেলে হয়ে মলিন পোশাকে ঘোরাঘুরি করে। তারিক সুজাতও তাই। তারিককে বই ছাপার সব খরচ দফায় দফায় ঢাকা গিয়ে দিয়ে আসি। বইয়ের পঈচ্ছদ করছেন খালিদ আহসান, শুনে খুব ভাল লাগে। চট্টগ্রামে বাড়ি খালিদের। বইমেলার আগে আগে ঢাকা এসে কিছু বইয়ের চমৎকার পঈচ্ছদ করে দিয়ে যান। নিজে তিনি কবিও। বইটি যেদিন আমার হাতে পাওয়ার কথা, সেদিন তো হাতে আসেইনি, মাস চলে যায়, বইয়ের নাম গন্ধও নেই। তারিককেও খুঁজে পাওয়া যায় না। গরু খোঁজার মত খুঁজে যখন পেলাম, বলে দিল বইএর কাজ এখনও শেষ হয়নি। একশ কাজের কাজীকে এ কাজটি দেওয়া মোটেও উচিত হয়নি, বুঝি। বই যখন কাঁচা বেরোলো বাঁধাই ঘর থেকে, তখন ফেব্রুয়ারির বইমেলার শেষ দিকে। একুশে ফেব্রুয়ারিও পার হয়ে গেছে। ছোটদার বাড়ির খাটের তলায় বইয়ের বাণ্ডিলগুলো রেখে দিই। কিছু বই মেলার কিছু দোকানে সদলবলে দিই বটে, দ্বিধায় সংকোচে আমি বইয়ের দোকানগুলোর আশপাশ দিয়ে হাঁটি না, যদি দেখি যে পাঁচটি বই দোকানে ছিল, সেই পাঁচটিই পড়ে আছে অনাথের মত! বিক্রি যদি কিছু হয় তো হয়েছে। খোঁজও নিই না। টাকা আনতেও দোকানে উঁকি দিই না। মেলার চায়ের দোকানে আড্ডা দিয়ে কাটাই। মেলা শেষ হলে বইয়ের বস্তা নিয়ে ময়মনসিংহে ফিরি। গাঙ্গিনাড় পাড়ের কবীর লাইব্রেরী আর পারুল লাইব্রেরীতে বই রেখে আসি যদি কেউ কেনে। কদিন পর পর লাইব্রেরীতে বই কিনতে গিয়ে আমার পড়ে থাকা বইগুলোর দিকে চোখ পড়ে। চোখ ঘুরিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘরে ফিরি। এই মনোকষ্ট থেকে নাইম আমাকে উদ্ধার করে। নাইমের সঙ্গে পরিচয় আবু হাসান শাহরিয়ারের মাধ্যমে। শাহরিয়ার ময়মনসিংহে এসেছিল কবিতা অনুষ্ঠানে। শাহরিয়ার ছড়া লেখে, ময়মনসিংহের ছড়াকার আতাউল করিম সফিকের সঙ্গে ভাল যোগাযোগ ওর। আতাউল করিমই ওকে নিয়ে যায় টাউন হলের বটতলায় সকাল কবিতা পরিষদের প্রতিবাদের কবিতা অনুষ্ঠানে। নিজে সে চমৎকার একটি কবিতা পড়ে অনুষ্ঠানে। তেমন লোক জমেনি বটতলায়। কিন্তু শাহরিয়ার এমনই মুগ্ধ সকালের বৃন্দ আবৃত্তি শুনে যে ঢাকায় গিয়ে স্বরশ্রুতিকে জানায়। স্বরশ্রুতি একটি বড় আবৃত্তি সংগঠন। স্বরশ্রুতি তখন বৃটিশ কাউন্সিলের অডিটোরিয়ামে বিশাল এক অনুষ্ঠান করার প্রস্তুতি নিচ্ছে, আমন্ত্রণ জানাচ্ছে দেশের প্রথিতযশা কবিদের এমন কী পশ্চিমবঙ্গের কবিদেরও। একক আবৃত্তি, বৃন্দ আবৃত্তির জন্য আমন্ত্রণ যাচ্ছে বিভিন্ন শিল্পীর কাছে, গোষ্ঠীর কাছে এপার বাংলায়, ওপার বাংলায়। স্বরশ্রুতির একটি আমন্ত্রণ সকাল কবিতা পরিষদের জোটে। মেডিকেল কলেজের ছাত্র পাশা, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী রোজেলিন, শহরের ছোটখাটো চশমাপরা আঁতেল আবৃত্তিকার দোলন, ইয়াসমিন আর আমি আবৃত্তির মহড়ায় মহা উৎসাহে নেমে পড়ি। চলে অবকাশে। সুস্থ রাজনীতি, বৈষম্যহীন সমাজ, সমতা আর সাম্যের স্বপ্ন ঝংকৃত হয় প্রতিটি কণ্ঠে। দল বেঁধে ঢাকা গিয়ে মেয়েরা জামদানি শাড়ি, ছেলেরা সাদা পাঞ্জাবি পাজামা পরে মঞ্চে উঠে যাই। আবৃত্তি করি কোথাও একক, কোথাও দুজন, কোথাও তিন জন, কোথাও সকলে। কারও কোনও ভুল হয় না, কোনও পা কাঁপাকাঁপি নেই কারও। দিব্যি শ্রোতা দর্শকদের হাততালি কুড়িয়ে নেমে আসি মফস্বলের আবৃত্তি-দল। মফস্বলের দল হিসেবে ঢাকায় তেমন দাম পাওয়া যায় না। বরাবরই ঢাকার কবি বা আবৃত্তিকারদের মধ্যে একটু দাদাগিরি ভাব আছেই। দাদাগিরি উড়িয়ে দিয়ে ব্রিটিশ কাউন্সিলের মাঠে বসে ঢাকার কবিবন্ধুদের সঙ্গে দীর্ঘ আড্ডা জমিয়ে তুলি। শাহরিয়ার সে মাঠেই পরিচয় করিয়ে দেয় নাইমের সঙ্গে। দেখতে বিচ্ছিরি নাইম। উঁচু দাঁত, উঁচু কপাল। চুলের কোনও ছিরিছাদ নেই। ও কটা চুল এই বয়সেই পাকতে শুরু করেছে। হাড়সর্বস্ব শরীর। হাত পা বাতাসে ছুঁড়ে ছুঁড়ে কথা বলে। হাঁটলে নিতম্ব দোলে। কিলো পঞ্চাশেক ওজনের শরীরে এই এতটুকুন নিতম্ব। নাইম খবরের কাগজ নামের একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক। পত্রিকাটি রাজনীতি সাহিত্য সমাজ সংস্কৃতি ইত্যাদির পাঁচ মিশেলি পত্রিকা, বেশ নাম করেছে এর মধ্যে। খুব সস্তায় বের করে, পঈচ্ছদও নিউজপ্রিণ্টে। দেশে কয়েক ডজন সাপ্তাহিকী বেরোয়, খবরের কাগজ সবগুলোর চেয়ে অন্যরকম। বড় বড় কবি সাহিত্যিকদের দিয়ে কলাম লেখানো হচ্ছে পত্রিকায়। এরকম একটি সুস্থ সুন্দর পত্রিকার প্রয়োজন ছিল দেশে। পত্রিকার নাম হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে নাইমের পরিচয়ও বাড়ছে লেখক অঙ্গনে। বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতায় বিভাগে পড়াশুনো করা ছেলে হঠাৎ করে কবি সাহিত্যিকদের এমন ঘরের লোক হয়ে যায় না। গুণ আছে বটে বিচ্ছিরি দেখতে ছেলেটির। তারিকের মত নাইমও একশ কাজের কাজী। স্বরশ্রুতি আবৃত্তি সংগঠনের সে সভাপতি জাতীয় কিছু একটা হয়ে বসে আছে, যদিও কবিতা বা আবৃত্তি কিছুরই মাথামুণ্ডু সে জানে না। নাইমের একটি ভাল দিক, সে অকপটে স্বীকার করে যা সে জানে না। তবে যা সে জানে, তা নিয়ে অহংকার তার কম নয়। অহংকার কখনও সুপ্ত, কখনও বিকট রূপে প্রকাশিত। কুমিল্লার আঞ্চলিক সুরে কথা বলা নাইমকে আমার প্রথম দেখায় পছন্দ হওয়ার কোনও কারণ নেই। কিন্তু পরিচয় থেকে চেনা জানা, চেনা জানা থেকে বন্ধুত্ব হতে খুব বেশি সময় নেয় না। সময় নেয় না কারণ নাইম সিদ্ধান্তই নিয়েছিল আমার সঙ্গে সে যে করেই হোক বন্ধুত্ব করবে। নাইম যা ভাবে তা যে করেই হোক সে করে ছাড়ে। তার যে জিনিসটি আমার ভাল লাগে, তা হল নতুন কিছু করার উৎসাহ। নতুন ধরনের কিছু। প্রতিনিয়ত সে পরিকল্পনা করছে, আর ঝাঁপিয়ে পড়ছে তা বাস্তবায়ন করতে। প্রচণ্ড উৎসাহী, উদ্যমী, ক্লান্তিহীন, কর্মঠ যুবক। শাহরিয়ার, নাইম, আমি প্রায় সমবয়সী। আমাদের আড্ডা জমে ভাল। শাহরিয়ারও ডাক্তারি ছেড়ে এসে মন্দ করেনি, গতি নামে একটি বিজ্ঞাপনী সংস্থা খুলেছে। গতি, শাহরিয়ার বলে, অন্ন বস্ত্র বাসস্থানের খোরাক জোটাতে, আর মনের খোরাকের জন্য আছে সাহিত্য। দুটোই চলছে ভাল শাহরিয়ারের। শাহরিয়ারের ছড়াকার বন্ধু সৈয়দ আল ফারুকের আছে গার্মেন্টসএর ব্যবসা। নিজের পয়সায় নিজের ছড়ার বই বের করে। শাহরিয়ার আর ফারুক মিলে একসময় ছড়া-পত্রিকা বের করত। সেই জিগরি দোস্ত ফারুকের সঙ্গে শাহরিয়ারের আজকাল বনিবনা হচ্ছে না। বনিবনা না হলে শাহরিয়ারের ধারালো জিভে তাকে খণ্ড খণ্ড হতেই হবে। নাইম আর শাহরিয়ারের মধ্যে অনেক অমিল, কিন্তু একটি ব্যপারে খুব মিল, তা হল যদি কাউকে পছন্দ করে তো তার মত ভাল পৃথিবীতে আর একটিও নেই, সে দেবতা, ভগবান, ঈশ্বর ! আর যাকে অপছন্দ হয়, সে নরকের সবচেয়ে নিকৃষ্টতম কীট ছাড়া কিছু নয়। এসব আমি তাদের সঙ্গে কেবল কদিনের কথাবার্তাতেই বুঝিনি, দীর্ঘদিন সময় লেগেছে। মাঝে মাঝে কিছু সাদামাটা জিনিসও সময় আমার কিছু বেশিই নিয়ে নেয়। শাহরিয়ারের মাধ্যমে পরিচয় হলেও একসময় শাহরিয়ারের চেয়েই বেশি দেখা হতে থাকে নাইমের সঙ্গে। নাইমের অতি উৎসাহের কারণেই ঘটে সব। শাহরিয়ারের সঙ্গে দেখা কম হওয়ার কারণ শাহরিয়ার নিজেই। একদিন সে আমাকে তার বাড়িতে নিমন্ত্রণ করল। গিয়ে দেখি বাড়ি খালি, তার বউ ঢাকায় নেই। খালি বাড়িতে প্রথম ভাল গল্প হল, কিন্তু এরপর শাহরিয়ারকে দেখে আমি অবাক, সে আমার রূপের প্রশংসা করতে করতে আমার গা ঘেঁসে বসে আমাকে জোর করে চুমু খাওয়ার চেষ্টা করছে। ঠেলে তাকে সরিয়ে দিয়েছি বারবার। নিরাপদ দূরত্বে যতবারই বসতে চেয়েছি, ততবারই সে দূরত্ব ঘোঁচানোর জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। তার ওই নিরন্তর চেষ্টা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে আমি তাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছি যে আমার সামান্যতমও আগ্রহ নেই তার ঠোঁটের কাছে নিজের ঠোঁট পেতে দেওয়ার এবং তাকে অনুরোধ করেছি আমাদের সুন্দর বন্ধুত্বটি যেন সে এভাবে নষ্ট না করে ফেলে কিন্তু তারপরও যখন সে হাত বাড়ানো বন্ধ করেনি, অতিষ্ট হয়ে আমাকে বেরিয়ে আসতে হয়েছে তার বাড়ি থেকে। আমাকে চুমু খেয়ে শাহরিয়ার হয়ত তার বউ মুনিরার কালো ঠোঁটে হযরে আসওয়াদ হযরে আসওয়াদ বলে চুমু খেয়ে পূর্ণ করত পাপী ও সন্তপ্ত প্রেমিকের হজ্ব। নাইমের সঙ্গে এই সমস্যা হয় না। নাইম কখনও কোনও সুযোগ নিতে চেষ্টা করে না, আমরা কোনও খালি ঘরে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দিলেও না। নাইম আমার একজন ভাল বন্ধু হয়ে ওঠে, ভাল বন্ধু মানেই তো এই যাকে বিশ্বাস করা যায়, যে সুখ দুঃখে পাশে দাঁড়ায়। নাইমের সঙ্গে পুরোনো দিনের গল্প করতে করতে একদিন চন্দনার কথা বলি, চন্দনা কুমিল্লায় থাকে বলতেই নাইম আমাকে তার গাড়িতে তোলে কুমিল্লা যাওয়ার জন্য। ইমদাদুল হক মিলন ভিড়েছিল, মিলনকেও নেওয়া হল। নাইম, মিলন আর আমি ঢাকা ছেড়ে সোজা কুমিল্লা। মিলনকে নিয়ে নাইম একদিন অবকাশে হাজির হয়ে আমাকে চমকে দিয়েছিল। নাইমের স্বভাবে এই চমকে দেওয়া ব্যাপারটি খুব আছে। সেদিন নাইমের এই এক তুড়িতে কুমিল্লা যাওয়ার সিদ্ধান্তটি সত্যিই ভীষণ ভাল লেগেছে। আমিও এরকম, যা মনে হয় করতে, সঙ্গে সঙ্গে করে ফেলি, কালের জন্য আমার কিছু ফেলে রাখতে ইচ্ছে করে না। কিছু করার আগে ভাবনা চিন্তা করা আমার একদম ভাল লাগে না। কুমিল্লায় চন্দনার শ্বশুর বাড়ি খুঁজে বের করে ঢুকে দেখি একটি ছোট বাচ্চার মা সে, বাড়ির ঘোমটা পরা পূত্রবধূ সে। সেই চন্দনা, আমার চন্দনা, এত কাছের সে, তারপরও কত দূরের। আমি স্পর্শ করি চন্দনাকে, আমার সেই আগের চন্দনাকে, গৃহবধু চন্দনা সে স্পর্শ কতটৃকু অনুভব করে আমি ঠিক বুঝি না। বলি, ‘রাঙামাটি গিয়েছিলাম, ওখানে কেবল তোর কথাই মনে হয়েছে, আমাদের যে কথা ছিল দুজনে রাঙামাটি যাবো, তুই আমাকে সব দেখাবি, সব চেনাবি, কত আনন্দ করব আমরা, মনে আছে!’ বুঝি না সেই কথার কথা চন্দনার আজও মনে আছে কি না। যখন হাতে চাঁদ পাওয়া উচ্ছঅ!সে বলি চল বেরোই, চল কোথাও ঘুরে আসি, চল ময়মনসিংহ যাই, চল ঢাকা যাই। চন্দনা হাসে আমার পাগলামি দেখে। চন্দনা খুব জোরে হাসে না, খুব জোরে কথা বলে না। অসম্ভব এক পরিমিতি বোধ তার এখন। সন্তর্পণে হাঁটে, সন্তর্পণে কথা বলে, চিলেকোঠার গোলাপ বাগানে নিয়ে গোলাপের কথাই বেশি বলে। মিলনের গল্প চন্দনা অনেক পড়েছে, এমনকি ওর ও সজনী গল্পটি পড়ে নিজের নামেই সজনী জুড়েছে, কিন্তু মিলনও চন্দনার জন্য এখন আর কোনও আকর্ষণ নয়। মিলনকে দেখে চন্দনা, খুব শান্ত চোখে দেখে, যেমন করে যে কোনও রহিম করিমকে দেখে। মিলনের সঙ্গে এর পরেও আমার মাঝে মাঝে দেখা হতে থাকে। বন্ধুত্ব মিলনের সঙ্গেও গড়ায়, আপনি থেকে তুমিতে সম্বোধন জলের মত গড়িয়ে যায়।
সাহিত্যিক, অসাহিত্যিক দু জগতেই আমার বন্ধুর সংখ্যা একটু একটু করে বাড়ে। পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের ডাক্তার সাইদুল ইসলাম, সাহিত্যের কোনও খবর যে কোনওদিন রাখে না, ভাল বন্ধু হয়ে ওঠে। বন্ধুত্বের দুয়োর আমি বন্ধ করে রাখি না। তাই বলে দুয়োরে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে আছি যে কোনও কাউকে বন্ধু করার জন্য, তা নয়। অনেক সাহিত্যিককে আমি প্রথম আলাপে না হোক দ্বিতীয় আলাপেই খারিজ করে দিয়েছি। হারুন রশিদের কথাই ধরি। সাংঘাতিক প্রতিভা ছেলেটির। সেই সেঁজুতি ছাপার সময় থেকেই হারুনকে চিনি আমি। তার কবিতার রীতিমত ভক্ত ছিলাম। চিঠিতে যোগাযোগ ছিল প্রথম প্রথম, একবার দেখাও করতে এসেছিল, কুইনিন জ্বর সারাবে বটে, কিন্তু কুইনিন সারাবে কের মত দেখা করতে সে আসতে পারে বটে, কিন্তু দেখা তাকে কে দেবে! আমি মফস্বলের লজ্জাশীলা মেয়ে, দেখা করব, তেমন সাহস আমার ছিল না বলতে গেলে। সেই হারুনই কয়েক বছর পর যখন দিব্যি হুট করে অবকাশে এল, এমন ভঙ্গিতে যে এসেছি আমি, আমার এই দেহখানি তুলে যদি না ধরতে পারো, অন্তত অনুমতি দাও তোমার ওই দেবালয়ের প্রদীপ হতে – যেহেতু আমার সঙ্গে রুদ্রর বিচ্ছেদ ঘটে গেছে, আমি একা, অতল একাকীত্বে আমি ডুবে যাচ্ছি, আমি এখন তার মত সুদর্শন যৃবককে কিছুতেই ফিরিয়ে দিতে পারব না। হারুন আমার দিকে প্রেম প্রেম চোখে যতই তাকাতে চায়, আমি চোখ সরিয়ে নারকেল গাছের ঝুলে থাকা ঝুলে থাকা নারকেলের দিকে চেয়ে থাকি, জানালার শিকে চেয়ে থাকি, গত বর্ষায় বজ্রপাতে পুড়ে যাওয়া সুপুরি গাছের মাথার দিকে চেয়ে থাকি, বলার মত কোনও শব্দ খুঁজে পাই না। বরং শব্দ খুঁজে পাই সেওড়াগাছের ভুতের মত দেখতে ফরিদ কবির নামের যে কবিকে হারুন সঙ্গে এনেছিল, তার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে। ঢাকায় হারুনের বাড়িতে গিয়েও আমাকে আবার সেই অস্বস্তিকর অবস্থায় পেয়েছিল। কিছুতেই হারুনের সঙ্গে আমার সাদামাটা সহজ সম্পর্কটিও হয়নি। এর মানে এই নয়, যাকে আমি বন্ধু বলে মেনে নিলাম, সে আমার আদপেই বন্ধু কোনও, আর যে মানুষকে তুচ্ছ করলাম, হেলায় ফিরিয়ে দিলাম, সে আমার খুব ভাল বন্ধু হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। হারুনের কথা না হয় বাদই দিলাম, হেলাল হাফিজের সঙ্গে সম্পর্ক ওভাবে শেষ হবে ভাবতে পারিনি কখনও। আসলে সম্পর্ক যেমন যেভাবে যে জায়গায় আছে, তার চেয়ে হঠাৎ করে সম্পূর্ণ অন্য দিকে মোড় নিলে কেমন যেন এলোমেলো হয়ে যায় সব। হেলাল হাফিজের সঙ্গে আমার যোগাযোগ অনেকদিনের। সেঁজুতির জন্য কবিতা চাইতে গিয়ে পরিচয়। প্রায়ই যখন কিছু করার থাকে না, বাড়িতে বসে থাকতেও ভাল লাগে না, প্রেসক্লাবে হেলাল হাফিজের সঙ্গে দেখা করতে যাই। দেখা করতে যাওয়া মানেই তিনি রেস্তোরাঁয় বসাবেন, দুপুরে একজনের বদলে দুজনের খাবার দিতে বলবেন। দুজন ভিড়ের রেস্তোরাঁয় বসে খাবো। আমি কখনও খাবারের পয়সা দিতে চাইলে তিনি কিছুতেই দিতে দেবেন না। কোনও উপহার তার জন্য নিয়ে গেলেও খুব ঠাণ্ডা গলায় বলবেন, তিনি কারও কোনও উপহার নেন না, আমি যেন উপহারটি নিয়ে চলে যাই, নিজে ব্যবহার করি অথবা অন্য কাউকে দিয়ে দিই। তাঁর সঙ্গে আমার কথা যা হয় তার মধ্যে বেশির ভাগই পরিবারের কথা। তিনি জানতে চান আমার বাবা কেমন আছেন, মা কেমন আছেন, দুই ভাই কেমন আছেন, বোন কেমন, এসব। হেলাল হাফিজ একা থাকেন, বিয়ে থা করেননি। একটি পত্রিকায় কাজ করতেন, পত্রিকা উঠে যাওয়ার পর তিনি কোথাও চাকরি বাকরি করেন না, জুয়ো খেলে জীবন কাটান। জুয়োতে তাঁর ভাগ্য খুব ভাল, জেতেন বেশির ভাগ সময়। আমাকে একবার জুয়োর নেশায় পেয়েছিল, তা অবশ্য খুব বেশিদিন টেকেনি। প্রতিরাতে হাসিনার আসলে আপন বোন নকলে ফুপাতো বোন পারভিনের বাড়িতে প্রতি সন্ধায় জুয়োর আসর বসত। বাঘা বাঘা সব খেলোয়ার টাকার তোড়া পকেটে নিয়ে জুয়ো খেলতে আসতেন। পারভিন আর তাঁর খেলোয়ার বন্ধুরা আমাকে শিখিয়ে দিয়েছেন কী করে ফ্লাশ খেলতে হয়। শেখানো খেলা খেলতে গিয়ে দেখি এক পশলা দেখা দিয়েই হাওয়াই মিঠাইয়ের মত উবে যায় আমার টাকা। প্রতিবারই মনে হয় বুঝি জিতব আর প্রতিবারই গাদা গাদা টাকা হেরে আসি। বাড়ি ফেরার সময় এমনকী হাতে রিক্সাভাড়ার পয়সাটিও থাকে না। খালি হাতে বাড়ি ফিরে দুটো টাকার জন্য এর ওর কাছে হাত পাততে হয়। আমাকে নিরীহ পেয়ে লোকেরা আমাকে ঠকাচ্ছে এই কথাটি আমার বোঝার সাধ্য ছিল না, কিন্তু বাবার হস্তক্ষেপে দাদা জ্ঞানদান করে করে আমাকে সরিয়েছেন জুয়োর আড্ডা থেকে। তবে ক্রমাগত হারলেও এ কথা স্বীকার আমি করি, উত্তেজনা ছিল খেলায়। টাকা আসে টাকা যায়, কিন্তু টাকা কি সবসময় এরকম উত্তেজক সময় দিতে পারে? পারে না। হেলাল হাফিজের জুয়ো খেলা প্রতিদিনের দশটা পাঁচটা চাকরি করার মত। সংসার বিরাগী একটি মানুষকে এভাবে মানিয়ে যায়। কোনও ঘর কারও ঘর তাঁকে টানে না। সামাজিক নিয়ম কানুনকে য়চ্ছন্দে পাশ কাটিয়ে চলে যান, স্পর্শ করেন না কিছু অথবা কিছুই তাঁকে স্পর্শ করে না। হেলাল হাফিজ মানুষটির এই অন্যরকম দিকটি আমাকে আকর্ষণ করে তাই এত বেশি। আমিও যদি পারতাম তাঁর মত নিস্পৃহ হতে। যে কেউ পারে না জানি। ঢাকা থেকে যখন তিনি আমাকে ময়মনসিংহে প্রায় প্রতিদিন ফোন করতেন, তখনও আমার মনে হয়নি তিনি আমার শ্রদ্ধাস্পদ দাদা ছাড়া অন্য কিছুতে রূপান্তরিত আদৌ হতে চান। আমার আশঙ্কার সূচনা আমাকে নিয়ে লেখা তাঁর কবিতা আর আমার জন্য একটি নতুন নাম তৈরি করা। তারপর যে মানুষ নিজের ঘর আর প্রেসক্লাবের বাইরে অন্য কোথাও যান না, কোনও বাড়িতে না, কোনও অনুষ্ঠানে না, তিনি কি না পঁচিশে আগস্টে চলে এলেন ময়মনসিংহে, আমার জন্মদিন পালন করতে! ঢাকায় গেলে তিনি একবার ছোটদার বাড়িতেও নিজের সব কৃচ্ছউত!র সঙ্গে যুদ্ধ করে চলে এসেছিলেন, এমনই ছিল তাঁর আবেগ। আবেগে যখনই তিনি প্রেম প্রেম চোখে তাকিয়েছেন আমার দিকে, আমি চোখ সরিয়ে নিয়েছি। যেদিন প্রথম আমার হাতটি নিলেন নিজের হাতে, দ্রুত আমি কেড়ে নিয়েছিলাম নিজের হাতটি, তিনি আবারও সেটি নিয়ে রাখতে চাইছেলেন অনেকক্ষণ তাঁর উষ্ণ হাতে। আমার ভাল লাগেনি, এই রূপে আমি তাঁকে দেখতে চাইনি। বড় বেমানান তিনি, যখন বলেন,
কোনওদিন আচমকা একদিন
ভালবাসা এসে যদি হুট করে বলে বসে
চলো যেদিকে দুচোখ যায় চলে যাই,
যাবে?
আমার চোখে তখন এই হেলাল হাফিজ সেই হেলাল হাফিজ নয়, উনসত্তরে যাঁর একটি কবিতা হাজার মানুষকে উদ্দীপিত করেছে রাজপথের মিছিলে নামতে।
এখন যৌবন যার, মিছিলে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়,
এখন যৌবন যার, যুদ্ধে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়।
সেই হেলাল হাফিজ যাঁর সংসারহীন উদাসীনতা, যাঁর মৌনতা মগ্নতা আমাকে মুগ্ধ করে। যাঁর কবিতার বিষাদ আমাকে আবৃত করে, তিনি ঠিক সেই মানুষটি নন। আমি খুব ভাল করেই জানি যে হেলাল হাফিজকে আমি আমার প্রেমিক হিসেবে কল্পনা কখনও করিনি। যাঁর মহত্বের পদধূলিতে পুস্পাঞ্জলি অর্পণ করে নিজেকে ধন্য মানি, তিনি যদি সেই শীর্ষাসন থেকে নেমে আমারই ধুলোয় গড়াগড়ি যান, তবে আমার যেমন সব যায়, তাঁরও যায়। তাঁর কাতর করুণ চোখে আমার কুঞ্চিত কুণ্ঠিত দৃষ্টি কালো কালো মেঘ ছুঁড়ে দিতে থাকে। আমার ভেতরে না কল্পনা করা অবিশ্বাস্য রকম বিস্মিত মানুষটি ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে, মানুষটির কণ্ঠস্বর কঠিন হতে থাকে, নির্দয়তা তার স্বভাবসুলভ নম্রতা ঢেকে দেয়, তাকে অমানবিক করে তোলে, তাকে অমানুষ করে তোলে। সে কঠোর হতে হতে, আরও কঠোর হতে হতে সেই আপাদমস্তক কবিটিকে, নিরীহ সংসারবৈরাগ্য যাঁর অঙ্গে অঙ্গে অথচ গোপনে গোপনে যে প্রচণ্ড এক স্বপ্নচারি মানুষ, ভুল করে একটি ভুল স্বপ্নের গা ছুঁতে গিয়েছিল— বের করে দেয় বাড়ি থেকে।
হেলাল ভাই, আপনি চলে যান, এক্ষুনি চলে যান এখান থেকে।
স্বপ্নভঙ্গের বেদনা ছিল সে কণ্ঠে, ছিল হতাশা, ছিল কিছুটা ঘৃণাও। রুমালে চোখ মুছতে মুছতে তিনি চলে গেছেন। তাঁর চলে যাওয়ার দিকে ফিরে তাকাইনি আমি, ভেতরে তখনও কঠোর আমিটি আমাকে বারণ করছে তাঁর চলে যাওয়ার দিকে করুণ করে তাকাতে। যে প্রণয় মানুষটিকে নিজের অস্তিত্ব অনুভব করতে শিখিয়েছিল, আছি,
বড্ড জানান দিতে ইচ্ছে করে, — আছি,
মনে ও মগজে গুনগুন করে
প্রণয়ের মৌমাছি।
সেই তাঁকেই লিখতে হল
আমারে কান্দাইয়া তুমি
কতোখানি সুখী হইছ,
একদিন আইয়া কইয়া যাইও।
আমার কোনওদিন তাঁরে গিয়া কওয়া হয় নাই, কতখানি সুখী হইছি আমি। কেবল দূর থেকে তাঁর ছোট ছোট পদ্য পড়ে পড়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছি। ছোবল তাঁকে আমি দিতে চাইনি। মন দেওয়ার কথাও আমার মনে কখনও আসেনি।
ভালবেসেই নাম দিয়েছি তনা,
মন না দিলে
ছোবল দিও তুলে বিষের ফণা।
তনার সঙ্গে ফণা মিলে যায় বটে, কিন্তু আমি কখনও বিষাক্ত সাপ ছিলাম না যে হেলাল হাফিজের মত নিরীহ নির্জন মানুষকে আমি ছোবল দিতে যাবো। আমি সে যেই হোক, একবার যদি বন্ধুত্ব হয়, কখনও সম্পর্ক নষ্ট করার পক্ষে নই। কিন্তু হেলাল হাফিজের মুখোমুখি দাঁড়াবার আমার কোনও মুখ রইল না। যদিও ছোবল দেওয়ার কথা বলেছিলেন মন যদি না দিই, কিন্তু আবার রাগ দেখিয়েছেন এ বলেও যে,
যদি যেতে চাও, যাও
আমি পথ হব চরণের তলে
ফেরাবো না, পোড়াবোই হিমের অনলে।
অথবা
তোমার হাতে দিয়েছিলাম অথৈ সম্ভাবনা
তুমি কি আর অসাধারণ? তোমার যে যন্ত্রণা
খুব মামুলী, বেশ করেছো চতুর সুদর্শনা
আমার সঙ্গে চুকিয়ে ফেলে চিকন বিড়ম্বনা।
কিন্তু নরম মনটি এরকম গাল দিয়ে স্বস্তি পেতে পারে না। কতটুকু উদার হতে পারেন তিনি তাও বলেছেন —
আমাকে উষ্টা মেরে দিব্যি যাচ্ছো চলে
দেখি দেখি
বাঁ পায়ের চারু নখে চোট লাগেনি তো!
ইস করেছো কি! বসো না লক্ষ্মীটি
ক্ষমার রুমালে মুছে সজীব ক্ষতেই
এন্টিসেপটিক দুটো চুমু দিয়ে দিই।
এখন যৌবন যার বইটির অসামান্য সাফল্যের পরে অভিমানী কবির দ্বিতীয় বই যে জলে আগুন জ্বলে বেরোচ্ছে। এর পরের বইএর জন্য নাম ঠিক করেছেন তিনি, যদিও কবিতা একটিও লেখা হয়নি, নামটি আমার কানে কানে বলেছিলেন, কার কী নষ্ট করেছিলাম! মাঝখানে অচল প্রেমের পদ্য ধ্রুব এষের আঁকা কার্ডে বেরিয়েছে। ছোট ছোট পদ্যগুলো পড়ে কষ্ট পেয়েছি, কষ্ট পেয়েছি তিনি কষ্ট পেয়েছেন বলে। ওরকম প্রেমে তিনি না পড়লেও পারতেন। কী দরকার ছিল! কী দরকার ছিল কষ্ট পাওয়ার, কষ্ট দেওয়ার! আসলে সংসার বিরাগী হিসেবে সকলে হেলাল হাফিজকে জানলেও আমার মনে হয় তিনি ভেতরে ভেতরে খুব সংসারী একটি মানুষ। তিনি যে মেয়েদের ভালবেসেছেন, তাদের কেউই তাঁকে সত্যিকার ভালবাসেনি। তাই কখনও তাঁর সংসার করা হয়নি, কেউ হয়তো বোঝে না, কিন্তু ভেতরে ভেতরে একটি স্বপ্ন তিনি লালন করেন। বাইরে থেকে বোঝা না গেলেও আসলে খুব গোছানো মানুষ তিনি। ইস্ত্রি করা সার্ট প্যান্ট পরবেন, চকচকে স্যান্ডেল পরবেন, আর একটি মোটা কাপড়ের ঝোলা থাকবে কাঁধে, ঝোলায় তাঁর কলম, কিছু কাগজ, সিগারেটের প্যাকেট, সবই খুব সুন্দর করে গোছানো। এমন গুছিয়ে তো কিছু আমি কোনওদিন রাখি না। কাঁধে ঝোলা নিয়ে ঘুরে বেড়ানো দাড়িঅলা কোনও মানুষ দেখলে কবি কবি লাগে, উদাসীন উদাসীন, এলোমেলো অগোছালো মনে হয়, আসলে কিন্তু তা নয়। কষ্ট পেতে কেউ কেউ ভালবাসেন, কেউ কেউ সন্ন্যাসী হতে ভালবাসেন। হেলাল হাফিজ তাঁর এককালের প্রেমিকাকে হারিয়ে নিজেই বলেছেন অনেক কষ্টের দামে জীবন গিয়েছে জেনে, মূলতই ভালবাসা মিলনে মলিন হয়, বিরহে উজ্জল। কষ্ট ফেরি করেন তিনি, সেই কতকাল আগে, আমার সঙ্গে যখনও পরিচয় হয়নি, লিখেছিলেন, পড়েছিলেন ফেরিঅলার মত সূর করে, কষ্ট নেবে কষ্ট,
হরেক রকম কষ্ট আছে, লাল কষ্ট নীল কষ্ট.
অনাদর আর অবহেলার তুমুল কষ্ট,
ভুল রমণী ভালোবাসার
ভুল নেতাদের জনসভার
হাইড্রাজেনে দুইটি জোকার নষ্ট হবার কষ্ট আছে,
কষ্ট নেবে কষ্ট?
আর কে দেবে আমি ছাড়া
আসল শোভন কষ্ট
কার পুড়েছে জন্ম থেকে কপাল এমন
আমার মত কজনের আর
সব হয়েছে নষ্ট
আর কে দেবে আমার মত হৃষ্টপুষ্ট কষ্ট!
গোপনে গোপনে ভালবসেন তিনি, যাকে ভালবাসেন, সে ই বোঝে না তিনি যে ভালবাসেন। একাকী বসে বেদনার জাল বোনেন তিনি, জানতে চান ভালবাসার মানুষটি কেমন আছে, যদি চিঠি না লেখে প্রেমিকা, তবে তিনি অভিমান করে বলেন,
..আর না হলে যত্ন করে ভুলেই যেও, আপত্তি নেই।
গিয়ে থাকলে আমার গেছে, কার কী তাতে?
আমি না হয় ভালবেসেই ভুল করেছি ভুল করেছি
নষ্ট ফুলের পরাগ মেখে
পাঁচ দুপুরে নির্জনতা খুন করেছি, কী আসে যায়!
বোন নেত্রকোণাকে ভালবাসেন তিনি, কিন্তু যান না তিনি নেত্রকোনার কাছে, নেত্রকোনা আছে তাঁর মজ্জার আর মগজের কোষে অনুক্ষণ, যে রকম ক্যামোফ্লাজ করে থাকে জীবনের পাশাপাশি অদ্ভুত মরণ।
ত্যাগ বিরহ যন্ত্রণা কষ্ট সন্ন্যাস কবি হেলাল হাফিজের একধরনের সম্পদ কিন্তু ঘনিষ্ঠ আর একজন কবিকে জানি ভোগ যাঁর কাছে প্রধান, জীবন যাঁর কাছে নিছক খেলা ছাড়া কিছু নয়। জীবন রঙ্গমঞ্চের মত, তিনি সেই মঞ্চে প্রতিনিয়ত অভিনয় করে যাচ্ছেন। মাঝে মাঝে আমার বুঝতে কষ্ট হয় কোন কথাটি বা কোন ব্যবহারটি তাঁর সত্যি এবং কোনটি মিথ্যে, কোনটি অভিনয়। সরল মনে তাঁর সবটুকুকেই সত্যি বলে মনে হয়। মনে হয় বলেই সম্ভবত আমাকে তিনি খুব পছন্দ করেন। তাঁর বিখ্যাত উপন্যসের নাম খেলারাম খেলে যা। বড় দক্ষ তুলিতে এঁকেছেন খেলারাম বাবর আলীকে। লুইচ্চউ! বদমাইশ বলে যে বাবর আলীকে সকলে গাল দেয় সেই বাবর আলীর চরিত্রটি যে সৈয়দ শামসুল হকের ভেতরের চরিত্র, তা অনেকটা পথ তাঁর সঙ্গে না চললে আমার সম্ভবত অনুমান করা হত না।
রুদ্রর সঙ্গে বিচ্ছেদের পর আমার ভগ্ন হৃদয়ের শুশ্রুষা করার দায়িত্ব সৈয়দ শামসুল হক নিজে থেকেই নিয়েছিলেন। তিনিই একদিন আমাকে নিয়ে চলেন রাঙামাটি। রাঙামাটি কখনও যাইনি আমি আগে। বিশাল বিশাল পাহাড় আর পাহাড়ের পায়ের কাছে জলের পুকুর, সে পুকুরের ধারে ঘাসে বসে সৈয়দ হক তাঁর নিজেরও মাঝে মাঝে যে একা লাগে বলেন। বলার সময় এত চমৎকার চমৎকার শব্দ তিনি ব্যবহার করেন যে মুগ্ধ হই। আমার শব্দগুলো তুলনায় তুলোর মত, যে কোনও ঘাসপোকাও য়চ্ছন্দে অনুবাদ করে দেবে, বাক্যগুলো এত নরম যে প্রায়ই আমার মুখের কাছে তাঁকে কান এগিয়ে আনতে হয়। রাঙামাটির মধ্যিখানে রঙিন একটি হোটেলে ঢুকে আমার কানের কাছেই তাঁর মুখ এগিয়ে এনে বললেন, একটি ঘর নিলেই তো চলে, তাই না?
আমি যদি বলি, না চলে না, তবে মনে হতে পারে যে আমি তাঁকে কোনও কারণে বিশ্বাস করছি না, তাঁকে দৃশ্চরিত্র বলে সন্দেহ করছি, কিন্তু সন্দেহের প্রশ্ন ওঠার যেহেতু প্রশ্ন ওঠে না, আমার যে তাঁকে নিয়ে মোটেও আশঙ্কা করার কিছু নেই, তা প্রমাণ করতে চেয়ে অত্যন্ত নিস্পৃহ নির্লিপ্ত কণ্ঠে কেমন আছর উত্তরে ভাল আছি বলার মত করে বলি, হ্যাঁ চলে।
তোমার অসুবিধে হলে বল, তাহলে দুজনের জন্য দুটি ঘর নিই।
আমার সরল উত্তর, আমার কেন অসুবিধে হবে? আমার কোনও রকম অসুবিধে নেই।
‘ঠিক বলছ তো?’
আমি উদ্বেগের ঘাড় চেপে প্রশান্ত মুখে অতি নিস্পাপ-অতি নিস্কলুষ সম্পর্কটির ধারে কাছে কোনও ক্লেদ উড়ে আসার আশঙ্কা অবান্তর বলে, হেসে, ‘নিশ্চয়ই’ বলি।
সৈযদ হক আমার পিঠে আলতো করে হাত রেখে বলেন, ‘তোমার একটি জিনিস আমার বেশ ভাল লাগে, তুমি না বল না কিছুতে।’
তা ঠিক। আমি না বলি না কিছুতে। সৈযদ হক, আমার বাবার বয়সী লোকটি, যাকে আমি বাবা বা দাদা বলে ভাবতে পারি অনায়াসে, অথবা কোনওরকম আত্মীয-সম্পর্কের তুলনা না করলে বন্ধুই ভাবতে পারি— তাঁকে না বলব কেন! আমি না বলব কেন, আমি তো তাবৎ অকবির মত ঘরকুনো রক্ষণশীল নই, সংসারবৃত্তে খাবি খাওয়া, সংকুচিত, সংকীর্ণ মনের কেউ নই! এর আগে আমাকে আর ইয়াসমিনকে নিয়ে সৈয়দ হক গিয়েছিলেন কুমিল্লার শালবন বিহারে, ওখানেও বন উন্নয়ন দপ্তরের একটি অতিথি ভবনে ছিলাম আমরা। আমি আর ইয়াসমিন ঘুমিয়েছিলাম এক ঘরে, তিনি আরেক ঘরে। সকালে বন উন্নয়নের নাস্তার ঘরে গিয়ে নাস্তা খেয়ে শালবন বিহারে হেঁটে বেরিয়ে ঢাকা ফিরে এসেছি। সারা পথই সৈয়দ হক মূলত একাই কথা বলেন, নিজের শৈশব কৈশোরের কথা, দারিদ্রের কথা, নিজের যক্ষা রোগের কথা, যক্ষা রোগীকে হাসপাতালে যে ডাক্তারটি ভাল করে তুলেছিলেন, সেই ডাক্তার আনোয়ারার কথা, তাঁদের প্রেমের কথা, কী করে তাঁদের বিয়ে হল সেই কথা, দুটি ছেলে মেয়ের কথা, নিজের লেখালেখির কথা, আশেপাশের মানুষের নির্লজ্জ আর নিষ্করুণ চরিত্রের কথা নির্দ্বিধায় বলে যান। লেখালেখির প্রসঙ্গ এলে বড় আগ্রহ নিয়ে আমি কী লিখছি জানতে চান। বড় অপ্রতিভ বোধ করি তখন। শরমে মিইয়ে যাই। মাঝে মাঝে শখের কবিতা লিখি, আমার কবিতা সৈয়দ হকের মত বিশাল মানুষের কাছে উপস্থিত করার মত দুঃসাহস আমি করি না। বরং বিভোর হয়ে তাঁর ধীরতা, উদারতা, তাঁর মহানুভবতা, তাঁর মমত্ব দেখি। তিনি বিলেতে থাকা লোক, ঢাকার গুলশানে বাড়ি গাড়ি নিয়ে সচ্ছঅল জীবন যাপন করেন। দেশের নামকরা লেখক। দেশময় ঘুরে বেড়ান। অগাধ পাণ্ডিত্য তাঁর। এত জানেন, তবু জানার ইচ্ছে আরও। আরও তিনি দেখতে চান, খুঁড়ে খুঁড়ে খুঁটে খুঁটে। জীবনের স্বাদ সাধ তাঁর কখনও ফুরোয় না। আমাদের মত মফস্বলের দুটি মেয়েকে তিনি খাতির করছেন, তাঁর খাতির পেয়ে আমরা দুবোন উচ্ছসিত, কিছুটা কুণ্ঠিত। তাঁর একটি ব্যপার লক্ষ্য করে অবাক না হয়ে পারি না, এত তিনি উন্মুক্ত, এত তাঁর ব্যাপ্তি, ময়মনসিংহে আমাদের বাড়িতে তিনি আতিথ্য বরণ করেছেন, অভাবনীয় সমাদর পেয়েছেন কিন্তু ঢাকায় নিজের বাড়িতে তিনি কখনও আমাদের একবার যেতেও বলেন না, রাত কাটাতে বলা তো দূরের কথা। রাত বরং তিনি দূরে কোথাও কাটাতে ভালবাসেন। দূরে কোথাওএর শখ আমারও কম নয়, দেশটির কত কোথাও এখনও যাইনি, কত কি দেখার বাকি। ছোট্ট একটি দেশ, তার বেশির ভাগ অঞ্চলই না দেখা পড়ে আছে। এদিকে বিচ্ছিরিরকম বয়স বাড়ছে।
রাঙামাটির রাঙা-রূপ দেখে একজনের কথাই আমার বার বার মনে পড়েছে, সে চন্দনা। চন্দনা নিশ্চয়ই এই মাঠটিতে হেটেঁছে, এই পুকুরের পাশে নিশ্চয়ই ও বসেছে, ওই গাছতলায় নিশ্চয়ই ও শৈশব জুড়ে দৌড়েছে, খেলেছে, কী খেলা খেলত চন্দনা! কোনওদিন ও গোল্লাছুট খেলেছে কি? না খেলে থাকলেও ওর জীবনেই ও খেলেছে খেলাটি, গোল্লা থেকে ছুটে গেছে চন্দনা। রাঙামাটির চাকমা জীবনের গোল্লা থেকে বাঙালি জীবনে ছুটে গেছে। চন্দনা কি সুখে আছে! বড় জানতে ইচ্ছে করে। মনে হয় হাজার বছর পার হয়ে গেছে ওকে দেখি না। শেষ দেখা হয়েছিল রুদ্রর মুহম্মদপুরের ভাঙা বাড়িটিতে। ওখানে ও খোকনকে নিয়ে এসেছিল, ওকে আপ্যায়ন করার ক্ষমতাও আমার ছিল না, বাইরে যে দুপুরে একসঙ্গে খেতে যাব, সেও হয়নি। এর আগে অবশ্য ঢাকায় ওর স্বামীর বোনের বাড়িতে একবার গিয়েছিলাম, বাড়িতে চন্দনা কেমন জবুথবু বসে থাকত, ছোট একটি ঘর ছিল যেখানে ও আর খোকন ঘুমোতো, আমার বিশ্বাস হয়নি চন্দনা কোনও পুরুষের সঙ্গে ঘুমোয় এখন, কোনও পুরুষকে খাবার চিবোতে দেখলে,খালি গায়ে দেখলে চন্দনার বমির উদ্রেক হত, সেই চন্দনা। সেই উচ্ছল উদ্দাম চন্দনা, জীবন নিয়ে গোল্লাছুট খেলা চন্দনা, চাকমা সমাজে শ্রাদ্ধ হওয়া চন্দনা। এখন সত্যিই কি ও নিপূণ সংসারী! আমার বিশ্বাস হতে চায় না। কেবল মনে হতে থাকে, চন্দনা যেখানেই যার আলিঙ্গনেই আছে, ভাল নেই। চন্দনা কি এখন আগের মত কবিতা লেখে আর!
রাঙামাটি থেকে কাপ্তাই যাওয়ার পরিকল্পনা করেন সৈয়দ হক। কাপ্তাইএ তাঁর ভক্ত বৃন্দের সঙ্গে তাঁর দেখা হবে, ওখানে ওদেরই অতিথি হবেন তিনি। কাপ্তাই পৌঁছে যে কাজটি করলেন, আমি তার জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না। তিনি তাঁর ভক্তবৃন্দকে আমার পরিচয় দিলেন, তাঁর কন্যা। তাঁর কন্যাকে ভক্তবৃন্দ দেখেনি কখনও, সুতরাং কন্যা আমি তাঁর হতেই পারি। লেকের জলে বড় একটি নৌকোয় বসে সৈয়দ হক ভক্তবৃন্দের নানা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাচ্ছেন হাসিমুখে। নতুন কি বই লিখলেন, কবিতা লিখছেন নাকি উপন্যাস, নাকি কাব্যনাট্য, নাকি গল্প। আমার পাশে একজন ভক্ত ছিল বসা, যেহেতু সৈয়দ হকের কন্যার সঙ্গে বাক্যবিনিময় না করা অভদ্রতার লক্ষণ, লাজুক হেসে বলল, ‘কাপ্তাই এ প্রথম এসেছেন?’
‘হ্যাঁ প্রথম।’
‘আপনাদের বাড়ি তো ঢাকার গুলশানে, তাই না?’
বুকের ধুকপুক নিজের কানে শুনি, আমি জলের দিকে চোখ ফেরাই, যেন ভক্তের বাক্যটি আমি ঠিক ষ্পষ্ট শুনিনি।
এরপর আবার প্রশ্ন, ‘আপনার বাবার লেখা সব আপনি পড়েছেন নিশ্চয়ই।’
এবার তাকাই, ‘কি বলছেন?’
‘বলছিলাম, হক ভাইএর সব লেখা নিশ্চয় পড়েছেন?’
‘ও। সব না, কিছু পড়েছি।’
বলে আমি আবার জলের দিকে, চাইছিলাম মন দিয়ে আমার জল দেখা দেখে ভক্তটি ভাবুক আমি জল নিয়ে বড় বেশি মগ্ন, এ সময় প্রশ্নবাণে বিরক্ত হতে চাই না। কিন্তু সেই ভক্ত তো আছেই, আরও একটি ভক্ত যোগ দেয় আমাকে সঙ্গ দিতে।
নতুন ভক্তটির প্রশ্ন, ‘আপনি কি শিগরি লন্ডন ফিরে যাচ্ছেন?’
জল থেকে চোখ তুলিনা আমি, ভয়ে আমার অনন্তরাত্মা কাঁপে। কী উত্তর দেব আমি এই প্রশ্নের আমি জানি না। যেন কারও কোনও প্রশ্ন শুনিনি আমি, আমি কানে খাটো, সৈয়দ হক বড় লেখক হতে পারেন, তাঁর নাকে কানে গলায় কোনও অসুবিধে না থাকতে পারে, কিন্তু তাঁর কন্যার যে থাকবে না তার কোনও যুক্তি নেই। মনে হতে থাকে, এই নৌকো থেকে যদি জলে ঝাঁপ দিতে পারতাম, তবে কোনওরকম প্রশ্নের সামনে আমাকে পড়তে হত না।
‘আপনার মেয়ের নাম কি হক ভাই?’ কেউ একজন জিজ্ঞেস করল।
সৈয়দ হক মধুর হেসে বললেন, ‘ওর নাম অদ্বিতীয়া।’
‘বাহ, বেশ সুন্দর নাম তো।’ সেই একজন বলল।
‘নামটি রেখেছি আমি।’
সৈয়দ হক বেশ স্নেহচোখে তাঁর অদ্বিতীয়াকে দেখছেন। অদ্বিতীয়ার করুণ চোখদুটো দেখছেন। চোখে জল জমতে চাইছে দেখছেন। দেখেও মধুর হাসিটি তিনি ঝুলিয়ে রেখেছেন ঠোঁটে। ঝুলে থাকা হাসির তল থেকে বললেন, ‘অবশ্য ওর মা ওকে অন্য নামে ডাকে। .. কী, কথা বলছ না কেন অদ্বিতীয়া, তোমার ভাল লাগছে তো?’
আমি মাথা নেড়ে ভাল লাগছে জানিয়ে, যেহেতু ভাল না লাগাটা অশোভন এই চমৎকার নৌকো ভ্রমণে, চোখ ফেরালাম জলে।
জলের চোখ জলে।
সৈয়দ হক প্রায়ই তাঁর শার্ট খুলে গলা থেকে পেট অবদি কাটা হৃদপিণ্ডে অস্ত্রেপাচার করার দাগ দেখিয়ে বলেন তিনি বেশিদিন নেই। বেশিদিন তিনি নেই বলে আমার একধরণের মায়া হয় তাঁর জন্য। ওই মায়ার কারণেই কি না জানি না আমি চেঁচিয়ে বাবাকে ভাই বলে ডেকে উঠছি না, খুব সতর্ক থাকছি মুখ ফসকে যেন কোনও সম্বোধন বেরিয়ে না যায়। অভিনয়ে পাকা হলে নৌকোভরা দর্শক শ্রোতার সামনে হয়ত বলে বসতাম, বাবা তুমি কি দুপুরের ওষুধদুটো খেয়েছো?
সৈয়দ হক নাটক লেখেন, নাগরিক নাট্যগোষ্ঠীর জন্য বেশ কটি নাটক লিখেছেন। ইদানীং আবার শেক্সপিয়ারের নাটক অনুবাদ করছেন, কোন এক ইংরেজ নাট্যকার সেই নাটক পরিচালনা করছেন। সৈয়দ হক কেবল নাটক লেখেন না, জীবনেও নাটক করেন। নাটক না হলে এ কী! তিনি আমাকে কন্যার মতো বললেও না হয় পার পাওয়া যেত, একেবারে কন্যাই বলছেন। এই যে তিনি এত সম্মান পাচ্ছেন এখানে, একটুও ভয় করছেন না যদি আমি বলে ফেলি যে আমি তাঁর কন্যা নই! মিথ্যুক হিসেবে প্রমাণিত হলে কোথায় যাবে তাঁর সম্মান! ফেলি ফেলি করেও তাঁর সম্মান জলে ছুঁড়ে ফেলতে আমার স্পর্ধা হয় না, সম্মান তো সৈয়দ হককে আমিও কম করি না। কিন্তু আমাকে মঞ্চে তুলে দিয়ে তিনি কি মজা করছেন! তাঁর নিজের নামটি খোয়াতে হয়নি, তাঁর পরিচয়েই তিনি আছেন, কেবল আমাকে রেখেছেন ঢেকে। আমি না পারছি তাঁকে হক ভাই বলে ডাকতে, না পারছি আপনি বলে সম্বোধন করতে। জিভের ডগায় শব্দগুলো যখনই আসে, তখনই আমাকে গিলে ফেলতে হয়, শব্দগুলো জিভের জলের সঙে গিলতে গিলতে দেখি জিভ শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে। নৌকো ভ্রমণ শেষ করে কাপ্তাই বাঁধ দেখে তিনি নৌবাহিনীর আগপাশতলা ঘুরে দেখলেন, আমি পেছন পেছন, বোবা কালা অদ্বিতীয়া। রাতে এক নৌসেনার বাড়ি নেমন্তন্ন, ওখানে বাড়ি ভরা লোকের সামনে ওই একই পরিচয় আমার, সৈয়দ হকের কন্যা। নাম অদ্বিতীয়া। নৌসেনা আমাকে আপনি বলে সম্বোধন করাতে সৈয়দ হক হা হা করে ছুটে এলেন, ‘ওকে আপনি বলছেন কেন! তুমি করে বলুন। বয়স তে একুশও পেরোয়নি, এই তোর কি একুশ হয়েছে?’ পঁচিশ ছাড়িয়ে যাওয়া মেয়ে আমি মাথা নোয়াই। পায়ের আঙুল গুনি, দশটি জেনেও গুনি আবার। গোনা শেষ হলে মনে মনে গুনি হাতের আঙুল, হাত শেষ হলে আবার পায়ের। সৈয়দ হক মদ্যপান করছেন তখন। ‘আচ্ছ! আপনার মেয়ে খুব কম কথা বলে বুঝি?’
‘ঠিক বলেছেন। খুব কম কথা বলে। জানি না কোত্থেকে এত লজ্জা সংগ্রহ করেছে ও। কোত্থেকে রে? ময়মনসিংহ থেকে?’ সৈয়দ হক চোখ টিপলেন।
ময়মনসিংহের ওঁরা কিছুই জানেননা।
নৌসেনার স্ত্রী সেজে গুজে ছিলেন, তিনি ধন্য ধন্য হাসি হেসে সৈয়দ হকের সামনে দাঁড়ালেন, ছবি তুলবেন। এক এক করে বাড়ির লোকেরা ছবি তুলল, পাশের বাড়ি থেকেও সৈয়দ হককে দেখতে লোক এসেছিল, ওরাও তুলল। সৈয়দ হক আমাকে প্রতিবারই ডেকে বসালেন তাঁর পাশে।
‘আপনার মেয়েও কি লেখে নাকি?’ নৌসেনার স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন।
‘লেখে, ও কবিতা লেখে। খুব ভাল কবিতা লেখে কিন্তু। তোমার লেখা একটি কবিতা শোনাও তো অদ্বিতীয়া।’
আমি সবেগে মাথা নাড়ি।
‘ভারি দুষ্টু ও। ভারি দুষ্টু।’ সৈযদ হক আমার ঘাড়ে চাপড় দিয়ে বললেন।
নৌসেনার বাড়ির লোক, এমনকী পড়শিরাও বললেন, সৈয়দ হককে তাঁরা টেলিভিশনে দেখেছেন। বিশাল ভোজনউৎসবে বসেও ওই এক কথা, টেলিভিশনে কবে কে তাঁকে দেখেছেন। একজনই কেবল সদর্পে ঘোষণা করলেন, তিনি তাঁর একটি বই পড়েছেন, বইয়ের নাম ‘আদিগন্ত নগ্ন পদধ্বনি’। নাম শুনে আমি চমকে উঠি, চমকে উঠি কারণ এটি শামসুর রাহমানের বই! লক্ষ্য করি তিনি প্রতিবাদ করছেন না, বলছেন না যে এটি তাঁর লেখা বই নয়। একবার শুধু আমার দিকে তাকিয়ে আগের মত চোখ টিপলেন। তিনি, দেখে আমার মনে হয়, সবকিছুতেই খুব মজা পাচ্ছেন। দিন খুব বেশি না থাকলে বুঝি এই হয়, প্রতিটি মুহূর্তে বাঁদর নাচিয়ে আনন্দ করতে হয়। আনন্দ খুব বেশিক্ষণ করা সম্ভব হয় না তাঁর, বারবারই তিনি স্নানঘরে দৌড়োন। খাওয়া শেষে আমি ও ঘর হয়ে আসতে গেলে দেখি স্নানঘর ভেসে যাচ্ছে বমিতে। বেসিনগুলোয় উপচে উঠছে যা তিনি খেয়েছিলেন। নির্যাস নিস্ক্রান্ত হওয়ার পথও বন্ধ হয়ে আছে। কিন্তু অসুস্থ হয়ে তিনি যে কাত হয়ে আছেন কোথাও, তা নয়, বরং একটি হাসি ঝুলিয়ে রেখেছেন ঠোঁটে, যে হাসিটির আমি কোনও অনুবাদ করতে পারিনি।