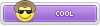গল্প (শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়) » বয়স
তখন দিন শুরু হত স্মৃতিশূন্যভাবে। অতীত বা ভবিষ্যৎ কোনোটারই কোনো ভার ছিল না। দিনটা নতুন তামার পয়সার মতোই আদরের ছিল, প্রতিটা দিন ছিল উৎসবের মতো। কয়লার ধোঁয়ার গন্ধে ঘুম ভাঙত। দাঁত মাজতে কী যে আলিস্যি। উঠে এক দৌড়ে ঘরের বাইরে গিয়ে পড়লেই পৃথিবীর আদিমতম গন্ধটি পাওয়া যেত তখন। ঘাস, গাছপালা আর মাটির ভিজে সোঁদা গন্ধ। পুবে রোদের মুখ লাল, পশ্চিমে আমাদের লম্বা। ছায়া। চারদিকে মাটি, গাছপালা, পৃথিবী। পৃথিবী কেমন তা অবশ্য জানা ছিল না। শোনা ছিল, নীচে এক গভীর। জলাশয় আছে, তার ওপর জাহাজের মতো ভাসছে পৃথিবী। সতুয়ার বিশ্বাস ছিল, ব্রহ্মপুত্র আড়াই প্যাঁচ দিয়ে রেখেছে পৃথিবীকে, গারো পাহাড় পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু পাহাড়। মিসিসিপি আর মিসৌরির কথা সে কখনো বিশ্বাস করত না। ম্যাপ দেখালে হাসত। বলত–ওসব হচ্ছে সাহেবদের কথা। ওসব কী বিশ্বাস করতে আছে? যারা খেয়ে হাত প্যান্টে মোছে, দাঁত মাজে না–অ্যাঃ।
দিন শুরু হত দুঃখের সঙ্গেই। পড়াশুনো। কালী চক্রবর্তী বারোমাস কফের রুগি, কম্ফটারটা গামছার মতো হয়ে গিয়েছিল। তাঁর কণ্ঠমণি আমরা কখনো দেখিনি। মুঠ মুঠ মুড়ি মুখে দিয়ে, সুরুৎ সুরুৎ চা টেনে নিতেন ভেতরে, বলতেন–আঃ! তাঁর আঙুলের ডগা থেকে সরল, সাঙ্কেতিক আর সুদকষা ঝরে পড়ত। সবসময়ে উবু হয়ে বসতেন, অর্শ বা ভগন্দর কিছু একটা ছিল বলে বসতে পারতেন না। তাঁর গা থেকে একটা শসা-শসা গন্ধ আসত। স্নান বারণ ছিল বলেই বোধ হয় ঘাম বসে একরকম গন্ধ ছাড়ত।
ঝাঁপের জানালাটা লাঠি দিয়ে ঠেলে তোলা। পাশেই উত্তরে ছোট্ট একটু জমি, তারপর শওকত আলির বাড়ি। যুবা শওকত আলি সেই জমিতে সকালের মিঠে রোদে কসরত করছে। তুর্কি লাফ দিয়ে শূন্যে উঠে শরীর উলটে ঝপ করে নেমে আসত প্রথমটা। সেই শূন্যের ডিগবাজি ছিল দেখবার মতোই। এত সহজে করত যেন মনে হত ওরকম করাটাই যেকোনো মানুষের নিত্যক্রিয়া। তারপর লাঠির কসরত। লোকে বলত, শওকত লাঠি ঘুরিয়ে বন্দুকের গুলি আটকায়। আমরা অবশ্য ছোটো ছোটো ঢিল ছুঁড়ে দেখেছি, সেগুলো টুকটাক ছিটকে পড়ে। গায়ে লাগে না। আমরা ভূগোল পার হয়ে ইতিহাসের পড়া দিতে দিতে আলেকজাণ্ডারের বাবার নাম ভুল করতামই। বারবার ম্যাসিড়নের নৃপতি… ম্যাসিডনের নৃপতি ছিলেন… অ্যাঁ… ম্যাসিডনের… মনে পড়ত না। কারণ বাইরে শওকতের স্যাঙাত নিধে তখন এসে গেছে। ছোটো দু-খানা কাঠের ছুরি নিয়ে দু-পক্ষ ঘুরে ঘুরে বলছে, শির, তামেচা, বাহেরা, কোটি, ভান্ডা, ঊর্ধ্ব… শির তামেচা বাহেরা, কোটি ভান্ডা ঊর্ধ্ব… মাথা থেকে শুরু করে সারাশরীর জুড়ে আক্রমণ এবং প্রতিরোধ। ছোরা খেলার নামতা আমাদের ওইভাবেই মুখস্থ হয়ে যায়। আলেকজাণ্ডারের বাবার নাম মনে পড়ত না।
শওকত আলির ছিল একটা ম্যাজিকের ঘর। সে-ঘরে ঢোকা বারণ ছিল। কিন্তু আমরা জানতাম। সে-ঘরে মড়ার মাথার খুলি আছে, আর আছে হাতের হাড়–জাদুদন্ড। পুরোনো পুথির মতো জাদুর বই। বাইরের ঘরে একটা বাঘছাল, দেওয়ালে টাঙানো, মাথাসুদ্ধ। চিতাবাঘের ছাল। সেবার মাদপুরে বাঘটা এসে এক মাঘমাসে উৎপাত শুরু করে। একটা কুকুরের মতো ছোটোখাটো বাঘ, তবু তার দাপটেই বাহেরা অস্থির হয়ে গেল। জোতদার দলুইয়ের গাদা বন্দুক তার গায়ে আঁচড়ও কাটল না। সে এসে গঞ্জে খবর দিল। শৌখিন শিকারিরা ছুটির দুপুরে বন্দুক কাঁধে চলল। শওকত আলির বন্দুক ছিল না। বশংবদ লাঠিগাছ কাঁধে নিয়ে সেও চলল বিটারদের সঙ্গে। মাদপুরের ধানখেত পার হলে জঙ্গল, জল। সেখানে টিন আর ক্যানেস্ত্রার চোটে বিস্তর পাখি উড়ে গেল। বন্দুকের শব্দ ধুন্ধুমার। বাঘ আর বেরোয় না। একা শওকত আলি জঙ্গল টুড়তে ছুঁড়তে এক গর্তের মধ্যে দুটো বাচ্চাসমেত মাদি বাঘটাকে ঘুমোতে দেখতে পেল। দেখে অবাক। এইটুকু বাঘ গোরু-মোষ মারে! সদ্য-বিয়োনী সেই বাঘ একবার শওকতকে মুখ ঘুরিয়ে দেখে ঠিক বেড়ালের মতো শব্দ করে। বাঘটাকে ছোট্ট দেখেই শওকত আলি তার লাঠির ওপর বিশ্বাস রেখে এগিয়ে যায়। সেই লাঠি নিপুণভাবেই চালিয়েছিল শওকত আলি কিন্তু বাঘটা কেবল একটা ছোট্ট চকিত লাফ দিয়ে উঠে এসেছিল। নিঃশব্দে। একটা চড়ে কোথায় গেল লাঠি। বাপরে বলে শওকত আলি জান বাঁচাতে লড়াই শুরু করে। সমস্ত গা ফালা ফালা করে ভেঁড়া ন্যাকড়ার মতো ছিঁড়ে ফেলছিল বাঘ। হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। শিকারিরা দৌড়ে এসেছে, হাতে বন্দুক কিন্তু কিছু করার নেই। গুলি যে কারও গায়ে লাগতে পারে। গলা টিপে অবশেষে মেরেছিল শওকত আলি বাঘটাকে। গভর্নমেন্ট থেকে পাঁচশো টাকা পুরস্কার আর চিকিৎসার খরচ দিয়েছিল। স্কুল ছুটি ছিল একদিন। সোনা-রুপোর গোটাকয় মেডেল আর মানপত্র দেওয়া হয়েছিল তাকে। সে সবই বাইরের ঘরে আলমারিতে সাজানো। আলমারির পাশের দেওয়ালে একটা বেতের ঢাল, তার পিছনে দু-খানা সত্যিকারের তরোয়াল ছিল। মাঝে মাঝে সেগুলোতে তেল মাখাতে খাপ থেকে বের করে আমাদের ডাকত সে। আমরা সর্বস্ব ফেলে তরোয়াল দেখতে যেতাম। গঞ্জে শওকত আলিকে সবাই খাতির করত।
সেবার চা-বাগান ঘুরে ছেঁড়া পাতলুন পরা ম্যাজিশিয়ান প্রোফেসর ভট্টাচার্য গঞ্জে এসে হাজির হল। ডাক্তার শশধর হালদারই তখন গঞ্জের সবচেয়ে বড়োলোক। ফোড়া কাটতে ভয় পেতেন দারুণ, একমাত্র ইঞ্জেকশনেই ছিল তার হাতযশ। ব্যথা লাগত না যে তার নয়। এমনকী রুগীর যে-রকম মুখ বিকৃত হত ব্যথায়, তারও সেরকম হত। তবে ইঞ্জেকশনটা খুব তাড়াতাড়ি দিতে পারতেন এবং তারপর ভালো করে ধুয়ে ফেলতেন। ডাক্তারির চেয়েও তার পসার ছিল ওষুধের ব্যবসায়, আর গোরুর দুধে! সাত সের দুধ দেয় এমন গোরু আমরা তার বাড়িতেই প্রথম দেখি। গঞ্জে গণ্যমান্য লোক এলে তার বাড়িতে ওঠাই ছিল রেওয়াজ।
বড়ো একখানা টিনের গুদামঘর ছিল সেই গঞ্জের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, তার একধারে বাজুরিয়াদের সিমেন্টের। বস্তা, ত্রিপল, কাঠ আর বাঁশের ভূপ। অন্য ধারে কাঠের তক্তা জুড়ে মঞ্চ। টিনের চেয়ারে সামনের দিকে বসতেন গণ্যমান্যরা, তাদের সামনে বিছানো ত্রিপল আর শতরঞ্চিতে বাচ্চারা, পিছনের বেঞ্চ-এ পাবলিক। প্রোফেসর ভট্টাচার্য প্রথমদিকে এলেবেলে খেলা দেখালেন। পিস্তল ছুঁড়ে ধোঁয়ার ভিতর থেকে ভারতমাতার আবির্ভাব দেখে পাবলিক আর বাচ্চারা খুব হাততালি দিল। তারপর বাক্সবন্দি খেলা, কঙ্কালের জলপান, শূন্যে ভাসমান মানুষ। ক্লাস সিক্সের দিলীপকে ডেকে নিয়ে অদৃশ্য করে দিলেন। আধঘণ্টা পর খেলার মাঠের গোলপোস্টের সঙ্গে বাঁধা অবস্থায় তাকে পাওয়া গেল। এসব দেখে গণ্যমান্যরা হাততালি দিতে লাগল। প্রোফেসর ভট্টাচার্য বারবার বলতে লাগলেন–
এই পুওর বেলিটার জন্য ডোর টু ডোর বেগিং করে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে… এই পুওর বেলিটার জন্যে… এইসব বললেন আর মড়ার হাড় নেড়ে সব আশ্চর্য খেলা দেখাতে লাগলেন। সবশেষে চ্যালেঞ্জ। যদি কেউ থাকেন যিনি প্রোফেসর ভট্টাচার্যের সব খেলা দেখাতে পারবেন, তবে ভট্টাচার্য তাঁকে একশো টাকা দেবেন, যদি কেউ চ্যালেঞ্জ করে না পারেন তবে তাঁকে একশত টাকা দিতে হবে।
শওকত আলি টিনের চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়িয়ে বলল–আমি পারি।
পরদিন সকালেই প্রোফেসর ভট্টাচার্য হাওয়া হয়ে গেলেন। কিন্তু শওকত আলি সব খেলা দেখাল। প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত। এমনকী নন্তুকে ডেকে হিপনোটাইজ করে তাকে দিয়ে এমন সব শক্ত শক্ত অঙ্কের উত্তর। করিয়ে নিল যে, কালীমাস্টারমশাই পর্যন্ত হাঁ হয়ে গেলেন। নন্তু সাতঘরের নামতাও পারে না যে! সবশেষে নকে শওকত আলি বলেছিল–সাবধান, কাউকে খুঁয়ো না, তুমি কিন্তু কাঁচের তৈরি। সেই ঘোর নন্তু পরের সাতদিনেও কাটাতে পারেনি। খেত ঘুমোত খেলত, কিন্তু কেউ ছুঁতে গেলেই আঁতকে উঠে চেঁচাত–ধোরো না, ধোরো না আমাকে, আমি কাঁচের তৈরি।
দিন শুরু হত। কালীমাস্টারমশাই বেলা করেই পড়িয়ে উঠতেন। আইবুড়ো মানুষ। গঞ্জে কী করে যে কবে এসে পড়েছিলেন কে জানে! নন্তুদের বাড়ি সকালবেলাটায় খেয়ে স্কুল সেরে বিকেলে সাধনদের পড়িয়ে রাতে শশধরবাবুর বাড়িতে খাওয়া সেরে ওদের বাইরের ঘরের একধারে গিয়ে শুয়ে পড়তেন। আমাদের দিন। সূর্যোদয়ের সঙ্গে শুরু হত, শেষ হতে চাইত না। কালীমাস্টার চলে গেলে দুই লাফে বাইরে গিয়ে পড়তাম। বই খাতা গুছোনোর জন্য দিদি পড়ে থাকত। বাইরে তখন সকালের প্রথম বনজ গন্ধটি আর নেই। শওকত আলির কসরত শেষ হয়ে গেছে। মাঠ ফাঁকা। তবু পৃথিবীতে করণীয় কিছুর শেষ ছিল না। মড়ার হাড় খুঁজতে শেলিদের। বাড়ির পিছনে পোড়ো মাঠটাতে চলে যেতাম।
সেই মাঠে পশ্চিমাদের বয়েল গাড়ির বড়ো বড়ো বলদগুলো চরে বেড়াত। কাঁধে ঘা। সেই ঘা খুঁটে খাচ্ছে কাক। সেখানে হাড় পাওয়া যেত বিস্তর। কিন্তু সাধন বলত–ও হাড় ছুসনি, ভাগাড়ের গো হাড়। সেই মাঠ পার হলে নদীর ধারে ছিল শ্মশান। শরৎকালে শ্মশানের দিকটায় কাশ ফুলে ঢেউ দিত। কিন্তু শ্মশান পর্যন্ত যেতে সাহস হত না। সেই মাঠে দাঁড়িয়ে আমরা দূর থেকে শ্মশান দেখতাম। ভয় করত। মানুষের হাতের হাড় পাওয়া হয়নি।
দূর থেকেই দেখতাম বাবুপাড়ার রাস্তা দিয়ে শচীন আর শেলি গোবরের ঝুড়ি হাতে ফিরছে। শচীনরা ছিল তিন বোন আর এক ভাই। পিকলি, বিউটি, শচীন, শেলি। শচীনের বোনদের এইসব সাহেবি নাম রেখেছিলেন। তার বাবা। একসময়ে শচীনরা ছিল গঞ্জের বড়োলোক। তার বাবা কাছেপিঠের এক চা-বাগানের ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। বন্দুক ছিল, ঘোড়া ছিল। বাড়িখানাও ছিল বাংলো প্যাটার্নের। তার ছিল দুই বিয়ে, অনেককাল সেটা জানা যায়নি। আগের পক্ষের ছেলেরা সব বড়ো বড়ো। সেবার শচীনের বাবা কালাজ্বরে মারা গেলে, আগের পক্ষের ছেলেরা এসে সব সম্পত্তি দখল করে। কলকাতায় তাদের বাড়ি ছিল বলে কেবল গঞ্জের বাড়িখানা ছেড়ে দেয়। শচীনরা গরিব হয়ে গেল। পিকলি, বিউটি আর শেলি লেস-এর জামা পরা, রুজ পাউডার মাখা, অর্গান বাজিয়ে গান গাওয়া, কিংবা জন্মদিনে পার্টি দেওয়া–এসব ভুলেই গেল। বাড়িখানা এখন রংচটা, কোথাও দেওয়ালের ইট বেরিয়ে আছে, বাগানের ভিতরে মোরামের বাহারি রাস্তাটায় গর্ত, সকাল থেকেই শচীন আর শেলি গোবর কুড়োয়, কাঠ-পাতা কুড়োয়। তার মা একসময়ে জর্জেটের শাড়ি পরত, এখন লজ্জার মাথা খেয়ে বাজুরিয়াদের বাড়ি আয়ার কাজ করে। বাজুরিয়াদের এক ছেলে বিলেত গিয়ে মেম বিয়ে করে। এনেছিল। বাজারের ভেতরে তাদের পৈতৃক বাড়িতে সেই মেমবউয়ের ঠাঁই হয়নি বলে হাই স্কুলের পেছনদিকে চমৎকার একখানা বাড়ি করে সেইখানে থাকত। সেই বাড়িতেই যেত শচীনের মা। পিকলি আর বিউটি একসময়ে কারও সঙ্গে মিশত না। ঘরে তাদের ব্যাপাটেলি, কারম, লুডো কত কী ছিল, ভাই-বোনেরা সেসব নিয়ে থাকত। এখন সেই দু-বোন পাড়ায় পাড়ায় ঘোরে। এ-বাড়ি সে-বাড়ি গিয়ে এর-ওর তার নিলেমন্দ করে। কেউ তাদের বসতে বলে না। তাদের চরিত্র নিয়ে কথা ওঠে। শচীন ক্লাসে ফাস্ট হয়। হেডমাস্টার এমদাদ আলি বিশ্বাস নিজের পকেট থেকে তাকে বই কেনার খরচ দেন। বলেন, গরিবরাই ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভের যোগ্য।
ছোটো ছোটো ঝুপসি লিচুগাছের ঘন ছায়ার ভেতর দিয়ে পথটি গেছে। বইখাতা হাতে সেই পথ ধরে যেতে যেতেই হঠাৎ শুনতে পেতাম দূর থেকে ইস্কুলের ঘণ্টার শব্দ। ওয়ার্নিং। সাধন বলত–দৌড়ো। এমদাদ আলি বিশ্বাস এ সময়টায় গেট-এর কাছে দাঁড়িয়ে থাকেন। টর্চবাতির মতো তাঁর চোখ জ্বলে। আমরা দৌড়োতাম!
ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে পড়ে সেই ইস্কুলে। মাস্টারমশাইরা আছেন, দিদিমণিরাও আছেন। মেয়েরা ক্লাসে বসে থাকে না, তারা থাকে মেয়েদের কমনরুমে। মাস্টারমশাই কিংবা দিদিমণিদের সঙ্গে ক্লাসের শুরুতে লাইন বেঁধে আসে, আবার ক্লাসের শেষে লাইন বেঁধে ফিরে যায়। ছেলেদের দিকে তাকানো বারণ। কথা বলা তো দূরের কথা। দিদি এক ক্লাস উঁচুতে পড়ত, ফেল করে আমার সঙ্গে পড়ে তখন। ক্লাসে আমি পড়া না পারলে একমাত্র সে-ই আমার দিকে কটমট করে চেয়ে থাকত। বিশ্বাস সাহেবের দাপটে তখন বাঘে-গোরুতে এক ঘাটে জল খায়।
সেবার শহরের ইস্কুলের টিম ফুটবল খেলতে আসে। এইট-এর কামু দারুণ খেলেছিল। শহরের টিম দু-গোল খেয়ে গেল। ফ্রেণ্ডলি ম্যাচ বলে কোনো প্রাইজ ছিল না। তবু বিশ্বাস সাহেব কামুদার পিঠ চাপড়ে দিয়ে আদর করলেন এবং ঘোষণা করলেন–কামুদাকে তিনি রুপোর মেডেল দেবেন। খেলার শেষে আমরা কামুদাকে ঘিরে ধরলাম। কামুদা বাড়ি ফেরার সময়ে বলল–বিশ্বাস সাহেবের গায়ে যা সুন্দর আতরের গন্ধ, না রে!
পরদিন হইহই কান্ড। সারাস্কুলের দেওয়ালে সব অসভ্য কথা লেখা। কমনরুমেই বেশি। শহরের ফুটবল টিম ইস্কুলবাড়িতেই রাত্রিবাস করে সকালে ফিরে গেছে। সবাই বলল–এ ওদেরই কাজ। দু-গোল খেয়ে রাগের চোটে এসব করে গেছে। কিন্তু তবু আমাদের ইস্কুলের কোনো ছেলে এ কান্ডের সঙ্গে জড়িত কিনা সে-বিষয়ে নিঃসংশয় হওয়ার জন্য এমদাদ আলি বিশ্বাস ক্লাসে ক্লাসে ঘুরে ডিকটেশন দিলেন–মনোজ মাংস মুখে দিয়া মুখ মুছিয়া মালদহ মুখে যাত্রা করিল। এই বাক্যটা আমরা সবাই খাতায় লিখে, সেই পাতায় নাম ক্লাস রোল নম্বর দিয়ে পাতাটা ছিঁড়ে বিশ্বাস সাহেবকে দিয়ে দিলাম। ভয়ে বুক শুকিয়ে আছে। কিন্তু কারও কিছু হল না। আমরা সেই বাক্যটার মধ্যে তন্নতন্ন করে খুঁজেও কোনো অসভ্য কথা পেলাম না। বিশ্বাস সাহেব তবে কেন ওই অদ্ভুত বাক্যটা আমাদের দিয়ে লেখালেন? দেওয়ালের কথাগুলো আমরা দেখিনি! তবে অনেকে বলল। বেশির ভাগ অসভ্য কথাই ম দিয়ে লেখা। সাধন সেদিন সন্ধেবেলা এসে বলল–মাংস মুখে দিয়ে কেউ মুখ মোছে নাকি! না আঁচালে এঁটো থেকে যায় না?
বিকেলটা ফুরোত সবার আগে। পূর্ণিমা থাকলে খেলা শেষ হতে না হতেই চাঁদ উঠে পড়ত। বিকেলটা শেষ হয়ে যাক এরকম ভাবতে ভালো লাগত না। দরগার পেছনে চাঁদমারির মতো উঁচু একটা ঢিবি ছিল। আমরা সেটার ওপর উঠে বসতাম। সাধন, দীপু, প্রদীপ, নন্তু, কোনো কোনো দিন সতুয়া। পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু তালগাছ আছে তাদের গাঁয়ের পাশের গাঁয়ে, সে গাছ শুইয়ে দিলে পৃথিবী ছাড়িয়ে আধ হাত বেরিয়ে থাকবে –এই গল্প বলত সতুয়া। সেই তালগাছ থেকে তাল পড়লে নাকি আশপাশের দশ-বিশটা গ্রামে ভূমিকম্প হয়। এক-একটা তালের ওজন বিশ মন। দীপু বয়সে প্রায় আমার সমান। কিন্তু সে দৌড়ঝাঁপ তেমন করতে পারত না। একটু খেলেই হাঁফিয়ে পড়ত, মারপিট লাগলে বরাবর সে মার খেত। তারপর কাঁদতে বসত। বলত–ম্যালেরিয়া না হলে তোদের দেখে নিতুম। সে সব সময়ে আমার পাশ ঘেঁষে বসত এবং বন্ধুত্ব অর্জনের চেষ্টা করত। সেই ঢিবির ওপর থেকে দেখা যেত, শেলিদের বাড়ির পেছনের মাঠে সূর্য ডুবে গেলে কেমন দু-খানা আকাশজোড়া পাখনা মেলে অন্ধকার উঠে আসছে। সেই দিকে চেয়ে ক্ষণস্থায়ী বিকেলের জন্য খুব দুঃখ পেতাম। নীল সমুদ্রে চাঁদ সাঁতরে চলত অবিরাম। খেলার শেষে আমরা সেই ঢিবির ওপর বসে আরও কিছুক্ষণ বিকেলের আলো দেখার চেষ্টা করতাম। সন্ধে উতরে ফিরলেও আমার তেমন ভয় ছিল না। বাবা বারমুখো লোক, মা রোগাভোগা। আমাদের বাড়ির শাসন তেমন কঠিন নয়। সবচেয়ে বেশি শাসন ছিল প্রদীপের। তার বাবা দেবীপ্রসাদ চক্রবর্তী ছিলেন সাহিত্যিক। অল্প বয়সেই মারা যান। প্রদীপের মা নানারকম হাতের কাজ শিখে গঞ্জে মহিলা সমিতির দিদিমণির চাকরি পেয়ে কলকাতা থেকে চলে আসেন। শোভনা দিদিমণি রোগা কালো মানুষ, ঠোঁটে একটু শ্বেতির দাগ, খুব নিয়ম মেনে চলতেন। প্রদীপ কড়া শাসনে থাকত। তার এক বড়ো ভাই। আছে–সুদীপ। সে মার সঙ্গে আসেনি। কলকাতায় মাসির কাছে থেকে ইস্কুলে পড়ে। সন্ধে হলেই প্রদীপের বাসায় তার বাবার বড়ো করে বাঁধানো ছবির সামনে দীপ জ্বেলে, ধূপকাঠি জ্বেলে দেওয়া হয়, ফুলের মালা দেওয়া হয় ছবিতে। প্রদীপ তাদের বাড়িতে যত্নে রাখা মাসিক পত্রিকা বের করে আমাদের দেখাত। শ্রীদেবপ্রসাদ চক্রবর্তীর নাম ছাপা গল্প আর কবিতা দেখে অবাক হয়ে যেতাম। তাঁর লেখা একটা কলের কোকিলের গল্প ছিল। কিছু বুঝিনি। প্রদীপ বলত–বাবার লেখা বুঝতে হলে মাথা চাই। আমার মা-ই কত লেখা বোঝে না। গঞ্জের সবাই তাদের খাতির করত। যদিও দেবপ্রসাদ চক্রবর্তীর লেখা কম লোকই পড়েছে। শোভনা দিদিমণি তাঁর স্বামীর কথা উঠলেই চোখ আধবোজা করে রাখতেন। সেই চোখের পাতার গভীর থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল জন্ম নিত। কিন্তু অন্য সময়ে তিনি ছিলেন ভীষণ কড়া। প্রদীপকে কখনো আদরের কথা বলতেন না। উঠতে-বসতে খেতে-শুতে সময় বাঁধা ছিল। বিকেলের দিকটায় দিদিমণির ফিরতে দেরি হত বলে সেই সময়টুকুতে চাঁদের আলোয় চাঁদমারির মতো উঁচু ঢিবিটায় সময় চুরি করে সে আমাদের সঙ্গে খানিক বসে থাকত। বলত–আমি একদিন পালাব, দেখিস। লোকের বাড়ি বাসন মাজব, ঘর ঝাঁট দেব, তবু পালাব। কথার মাঝখানে দীপু হঠাৎ চেঁচিয়ে বলত, রন্টু, ওই দেখ তোর বাবা আজও আবার লোক এনেছে। অবাক হয়ে। তাকিয়ে দেখতাম ঠিকই। দরগার সামনে লিচুবাগানের ভেতর থেকে রাস্তাটা যেখানে হঠাৎ বেরিয়ে এসেছে। সেই জায়গাটা পার হয়ে গল্প করতে করতে বাবা আসছে, সঙ্গে একটা খাকির হাফপ্যান্ট পরা লোক, মাথায় হ্যাট। কোথা থেকে যে ধরে ধরে বাবা অতিথি নিয়ে আসত কে জানে। সপ্তাহে তিন-চার দিনই বাইরের অচেনা লোকেরা এসে পাত পাড়ত আমাদের বাসায়। মা রাগ করলে বাবা উদার গলায় বলত–অতিথি খেলে বাড়ির মঙ্গল হয়, মানুষের পায়ের ধুলোয় কত জায়গা তীর্থ হয়ে গেল। মা তখন ঝোঁকে বলত–তা অসময়ে লোক এলে যে আমাদের হরিমটর করতে হয়। বাবা শান্ত গলায় মিনমিন করে বলত–তিথি মেনে যে না আসে সেই তো অতিথি। যারা আসত তাদের মধ্যে ভবঘুরে, চোর, জ্যোতিষী সব রকমের মানুষ ছিল। এসব লোক আমাদের গা সওয়া হয়ে গিয়েছিল। এই হাফপ্যান্ট আর হ্যাটঅলা লোকটা আসার আগে যে এসেছিল, সে এক সকালে চলে গেলে দেখা গেল একটি পেতলের ঘটি, বিছানার চাদর, একজোড়া চটিজুতো সে নিয়ে গেছে। এরপর মা রাগারাগি করায় বাবা আর লোক আনত না। কেবল একা খেতে বসে দুঃখ করে বলত–আমাদের দেশের বাড়িতে প্রতিবেলা একশোখানা পাত পড়ে। বিদেশে চাকরি করতে দেখে এসে দেখ কেমন একা একা খেতে হয়। একা খেলে আমার পেট ভরে না। সেই চুরির পর অনেকদিন বাদে লোক এল। দীপু আমাকে ঠেলা দিয়ে বলল–মামিমা আজ কুরুক্ষেত্র করবে। চল দেখি গিয়ে–! শুনে আমি তাকে একটা গাঁট্টা মারি, বলি। আমার মা-বাবার ঝগড়া দেখবি কেন? সে কাঁদতে থাকে।
খাকি হাফপ্যান্ট পরা লোকটা ছিল গায়ক। মোটাসোটা নাদুসনুদুস চেহারা, গালে পানের ঢিবি। বাবার একখানা লুঙ্গি পরে নিয়ে দিদির সিঙ্গল রিডের হারমোনিয়ামটা নিয়ে সে বারান্দায় চাঁদের আলোয় শতরঞ্চি পেতে বসে গাইতে লাগল–ভুলিনি, ভুলিনি, ভুলিনি প্রিয়, তব গান সে কি ভুলিবার…! বাবা শুনতে শুনতে আধশোয়া হয়ে চাঁদের দিকে চেয়ে উদাস হয়ে গেল। মা নতুন করে রাঁধতে বসেছে। সেই ফাঁকে দেখি উত্তরের মাঠে নালির ধারে শওকত আলি হ্যারিকেন জ্বেলে মুরগি জবাই করতে বসেছে। মুরগি কাটা দেখতে চুপে উঠে গেলাম। ভুলিনি… ভুলিনি… গানের সঙ্গে মুরগিটার প্রাণান্তকর ডাক মিশে যাচ্ছিল। আকাশে জ্যোৎস্নার বান।
লোকটার নাম আমরা দিলাম ডি ও সান্যাল। আমাদের বাড়ির অতিথিরা দু-রকমের ছিল। কিছু লোক ছিল যারা একবার এসে সেই যে চলে যেত, আর আসত না। আর কিছু লোক ছিল যারা ঘুরে-ফিরে আসত। এই লোকটাকে দেখে মনে হল, এ দ্বিতীয় দলের। কাজেই এর একটা নাম দেওয়া দরকার। বাবা তাকে সান্যাল, সান্যাল বলে ডাকে, নাম টের পাই না। সান্যাল আরও একজন আমাদের বাড়িতে আসে। সে ফোকলা। এ লোকটার দাঁত আছে তাই তার নাম দেওয়া হল, দাঁতঅলা সান্যাল। সংক্ষেপে ডি ও এস। ফোকলা জনের নাম এফ সান্যাল আগেই দেওয়া ছিল। পরদিন সকালে কোনো সময়ে যেন বাবার চটিজোড়ায় আমার পা লাগলে লোকটা বলল, খোকা, বাবার চটিতে পা লাগলে প্রণাম করবে। তারপর সে মার রান্নার প্রশংসা করল। আমাকে শংকরা আর বেহাগের পার্থক্য বোঝাতে লাগল। দু-দিন গানে গানে আমাদের মাথা গরম হয়ে রইল। কালীমাস্টারমশাই পর্যন্ত একদিন কামাই করলেন। তারপর লোকটা চলে গেল। শুনলাম সে যুদ্ধে যাচ্ছে। ডি ও সান্যাল আর কোনোদিনই ফিরে আসেনি।
হিটলারের হাতে ইংরেজ তখন বেজায় মার খাচ্ছে। তার ফলে চারদিকে বেকার আর ভবঘুরে বেড়ে গেল। খুব। চাল-ডাল পাওয়া যায় না, কেরোসিন নেই, দেশলাইয়ের আকাল। মার মেজাজ সপ্তমে চড়ে থাকে। দেশ থেকে সেই সময়ে বাবার দু-চারজন জ্ঞাতি, আর তাদের আত্মীয়েরা এসে আমাদের বাসায় থানা গাড়ল। তারা শুনেছে যুদ্ধের বাজারে ধুলো বেচে অনেকে বড়োলোক হচ্ছে। তারাও সব কারবার কনট্রাক্টরি করার জন্য চলে এসেছে কিন্তু ঘাঁতঘোঁত জানা না থাকায় বেমক্কা সারাদিন ঘোরে, রাতে ঘরে বসে জটলা পরামর্শ করে। বাবা অনেকদিন থেকেই সিগারেট ছেড়ে স্বদেশি বিড়ি ধরেছে। জ্ঞাতিরা আসার পর সেই বিড়ি প্রায়ই চুরি হতে লাগল। বাবা কিছু বলতে পারে না কাউকে। তাড়ানো তো দূরের কথা। আমাদের ভাতের ফ্যান গালা বন্ধ হয়ে। গেছে তখন। বাসায় অঙ্ক কষতে আর কাগজ নষ্ট করি না, স্লেটে কষে মুছে ফেলি, স্কুলে উঁচু ক্লাসে স্লেট অ্যালাউ করলেন বিশ্বাস সাহেব। বাড়িতে মা-বাবার কথাবার্তা বন্ধ। শোনা গেল শওকত আলি যুদ্ধে যাবে। আমরা ক-দিন খুব উত্তেজিত হয়ে রইলাম। শওকত আলি লাঠি দিয়ে গুলি ঠেকায়, হাতে বাঘ মারে, মানুষকে সম্মোহিত করে দেয়, সে যুদ্ধে গেলে একটা হেস্তনেস্ত হবেই।
জ্ঞাতিদের জ্বালায় মার প্রাণ ওষ্ঠাগত। দিনে পঞ্চাশবার উনুন থেকে কাগজ জ্বেলে তাদের বিড়ি ধরিয়ে দিতে হয়। দেশলাই নেই। মা প্রকাশ্যে রাগারাগি শুরু করে। জ্ঞাতিরা তখন মাকে খুশি রাখার জন্য বিচিত্র কান্ড শুরু করল। কেউ মার চেহারার, কেউ মার রান্নার প্রশংসা শুরু করল। কেউ বা এর-ওর বাগান থেকে চুরিচামারি করে ফলপাকুড় এনে দিত। ঘরের কিছু কিছু কাজকর্মেও আসত। বাবা ফিরলে তারা সবাই একসঙ্গে হইহই করে উঠত–কাকা এসেছেন, কাকা এসেছেন! তারপর বাবার চটি ধরে টানাটানি, জামা খুলে দেওয়া নিয়ে কাড়াকাড়ি। শেষে বাবা হাত-পা ধুয়ে বিশ্রাম করার সময়ে তারা বাবার হাত-পা-পিঠ দাবাতে বসত, আঙুল মটকে দিত, পিঠে সুড়সুড়ি, মাথা চুলকোনো–সবই করত। বাবা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়ে চেঁচামেচি করত–ওরে আর জোরে দাবাসনি, হাড়গোড় ভেঙে যাবে। তারা ছাড়ত না।
জ্ঞাতিদের মধ্যে একজন ছিল পুলিন। একদিন তাকে দেখি শেলিদের বাড়ির পেছনের মাঠে ভাগাড়ে হাড় কুড়িয়ে একটা বস্তা বোঝাই করছে।
ভারি অবাক হয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম–এসব কুড়োচ্ছেন কেন?
পুলিন ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বলল–চুপ। একটা কারবারের কথা মাথায় এসেছে। হাড়ে বোতাম হয় জানো তো?
জানি।
পুলিন খুব হেসে বলল–কথাটা এতদিন একদম মাথায় আসেনি। হঠাৎ সেদিন এপাশটা দিয়ে যেতে যেতে ব্যাপারটা মাথায় এসে গেল। শুধু বোতাম না, লবণ শোধন করতেও লাগে। গোরারা তো সবই কিনে নিচ্ছে, যুদ্ধে নাকি সব লাগে। কাউকে বোলো না কিন্তু, লোকে বুদ্ধি পেয়ে যাবে।
পুলিন সেই হাড়ের বস্তা নিয়ে বাসায় ঢোকামাত্র মার উনপঞ্চাশ বায়ু কুপিত হয়। সন্ধেরাতে সেই হাড় পুলিনকে ফেলে দিয়ে আসতে হয়। তারপর শীতের রাতে স্নান করে ঘরে ঢোকা। সেই বস্তার মুখটা একবার আমি একটু ধরেছিলাম। কিন্তু পুলিন খুব মহত্ত্ব দেখাল, আমার কথা মাকে বলল না। বাজারে তখন লোহার বোতাম চালু হয়েছে।
ব্ল্যাক মার্কেট কথাটা তখন শোনা যাচ্ছে খুব। পুলিন সর্দিজ্বরে পড়ে থেকেই প্রায়ই বলত–এবার ব্ল্যাক মার্কেটের ব্যাবসা চালু করব। কথাটার অর্থ সেও ভালো বুঝত না।
বাড়িতে জ্ঞাতিরা জড়ো হওয়ায় বাবা অখুশি ছিল না। একা খেতে হত না। পেট ভরত। কিন্তু মার মূর্তিখানা দিন দিন মা কালীর মতো হয়ে আসছিল। ঠিক সেই সময়ে কলকাতায় বোমা পড়ায় সেখানে আমার মামাবাড়ি থেকে দিদিমা, তিন মামা, দুই মাসি চলে এল আমাদের বাসায়। মার আর কিছু বলার রইল না। বাবার মুখ উজ্জ্বল দেখাল। মামাবাড়ির লোকজন যেদিন গেল সেইদিনই মা নিজে যেচে বাবার সঙ্গে ভাব করে। বাড়িতে আর জায়গা ছিল না। পড়াশুনো মাথায় উঠে গেল। আমরা সারাদিন মনের আনন্দে ঘুরি। সাধনদের বাড়িতেও লোক, দীপুদের বাড়িতেও। কেবল প্রদীপদের বাড়িতে সন্ধেবেলা সাহিত্যিক দেবপ্রসাদ চক্রবর্তীর ফটোতে রোজ বিকেলে মালা দেওয়া হয়, ধূপকাঠি জ্বলে। প্রদীপ সকাল-বিকেল পড়তে বসে। তার মা বলে–কত বড়ো সাহিত্যিক ছিলেন তোমার বাবা সে-কথা কখনো ভুলো না। তোমাকে বড়ো কিছু হতেই হবে। প্রদীপ আড়ালে-আবডালে বলত–সাহিত্যিক না কচু! লিখত তো বাচ্চাদের লেখা, তাও বেশির ভাগ অনুবাদ।
আমরা অবাক হয়ে বলতাম–তুই কী করে জানলি?
মামাবাড়িতে এই নিয়ে হাসাহাসি হত কত! আমি যুদ্ধে যাব জানিস। সাহিত্যিক-ফাহিত্যিক নয়, আমি হব। সোলজার।
চারদিকে ট্রেঞ্চ কাটা হচ্ছে তখন। দরগার মাঠে লোকলশকর লেগে দিব্যি আঁকাবাঁকা ট্রেঞ্চ কেটে দিল। নতুন রকমের একটা খেলা পেয়ে গেলাম আমরা। গর্তের মুখে লাফ দিই। সবাই পারি, কেবলমাত্র দীপুই পারে না। তিন বোনের পর দীপু একমাত্র ভাই, তার মা-বাবার খুব আদরের, তাই বোধ হয় পারত না। তার হাত-পা নরম নরম ছিল।
বর্ষায় ট্রেঞ্চে ব্যাঙের আস্তানা হল। জল জমে ডুবজল। নিধে ছিপ ফেলত। চ্যাঙা-ব্যাঙা মাছ ধরত। অনেক রাতে বৃষ্টি নামলে প্রবল ব্যাঙের ডাক শোনা যেত। আকাশে কাক, চিলের মতো এরোপ্লেন দেখে দেখে আর শব্দ শুনেও চোখ তুলে তাকাতাম না।
মামারা ছিল বয়সে আমাদের চেয়ে অনেক বড়ো। তারা তখন কিশোর কিংবা যুবা। প্রখর চোখে তারা মেয়েদের দেখত। দীপুদের বাড়িতে তাদের বয়সি কয়েকটা ছেলে এসেছিল। সব কলকাতার ছেলে। মামারা তাদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াত। সিঁথি কাটা, জুতো পরা, জামার হাতা গুটোনো–এসব আমরা তখনই তাদের কাছ থেকে শিখছি।
দরগার সামনে আমাদের ট্রেঞ্চ-এর দু-ধারে লাফাতে দেখে মামারা হেসে খুন। দীপু লাফাতে পারে না দেখে আমার ছোটোমামা জ্যোতির্ময় গম্ভীর হয়ে বলল–ও লাফাবে কী! ও তো মেয়ে!
যাঃ। বলে আমি চেঁচিয়ে উঠি।
মামা হাসল। বলল–আমি জানি। ওর ভাই নেই বলে ওর মা-বাবা শখ করে ওকে ছেলে সাজিয়ে রাখে।
আমরা তাকিয়ে দেখি, দীপু দরগার মাঠ ধরে প্রাণপণে দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছে।
পরদিন বিকেলে টিলার ওপর আমাদের মিটিং বসল। আমি সাধন, প্রদীপ, সতুয়া, নন্তু আর একধারে দীপু গোঁজ হয়ে বসে। তার চোখে জল।
তুই মেয়ে? সাধন জিজ্ঞেস করল। মাথা নাড়ল দীপু, হ্যাঁ।
আমরা অনেকক্ষণ কথা খুঁজে পাই না। কী বলব! দীপু ততক্ষণে কাঁদতে থাকে। বলে–আমার সঙ্গে খেলবি? আর খেলায় নিবি না?
সেসময়ে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলতে খেলতে আমাদের মধ্যে পৌরুষ এসে গেছে। প্রদীপ বলল–কী করে খেলি বল! সবাই জেনে গেলে বলবে মেয়েদের সাথে খেলি।
দীপু অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল–আমি যে মেয়েদের খেলা কখনো খেলিনি। আমার মেয়ে-বন্ধুও নেই।
সতুয়া খুব অবাক হয়েছিল। বলল–মেয়েছেলে তো তোকে হতেই হবে। ও কি লুকোনো যায়?
আমার মন খুব খারাপ ছিল। দীপু আমার বন্ধুত্বই সবচেয়ে বেশি চাইত। আমার দিকে চেয়ে দীপু বলল–মেয়ে হতে আমার একটুও ভালো লাগে না।
নন্তু ধমক দেয়–মেয়ে হবি আবার কী! তুই তো মেয়েই।
দীপু গোঁজ হয়ে বসে কাঁদতে থাকে, সে কিছুতেই আমাদের সঙ্গ ছাড়বে না।
নন্তু আমাদের আড়ালে ডেকে বলল–ভাই, বদনাম হয়ে যাবে কিন্তু। আমরা ক-জন ছাড়া দীপুর সঙ্গে আর কেউ খেলত না। ওকে দলে রাখা যাবে না।
আমরা পরামর্শ করলাম অনেক। সবশেষে সতুয়া গিয়ে বলল–দীপু, তোকে আমরা অনেক জিনিস দেব। কাল থেকে আর আমাদের সঙ্গে খেলতে আসিস না।
সেই দিন দীপুকে আমরা প্রায় একটা ফেয়ারওয়েল পার্টি দিলাম। সেদিনও দিনের শেষে চাঁদ উঠেছিল। আমরা যে-যার বাসা থেকে মার্বেল, ছুরি, গল্পের বই এনে দিলাম। দীপু নিল। চলে যাওয়ার সময় বলল-বড়ো হয়ে তো কোনো ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ে হবেই, তখন আমি
বলে সে সবার দিকে তাকাল। আমরা চুপ।
দীপু পায়ের আঙুলে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে মুখ নীচু করে বলল–তখন আমি রন্টুকে বিয়ে করব।
এই বলে এক ছুটে টিলা থেকে নেবে গেল দীপু।
যুদ্ধের শেষে একদিন বাড়ি বাড়ি তেরঙা পতাকা উড়ল। ইস্কুলে পতাকা তুললেন এমদাদ আলি বিশ্বাস। তার কিছুদিন পরেই ফেয়ারওয়েল দেওয়া হল তাঁকে। সবাই তাঁর কৃতিত্বের কথা বললেন। তিনি বলতে উঠে বললেন–আমি যে মুসলমান বলে পাকিস্তানে চলে যাচ্ছি তা নয়। আমি বুড়ো হয়েছি, এই জায়গা ছেড়ে কোথাও না কোথাও আমাকে যেতেই হত। গোরও তো ডাকছে। আমি হিন্দু-মুসলমান দু-রকম ছেলেই পড়িয়েছি। যখন শাসন করতে হাত তুলেছি তার ভালোর জন্য তখন হিন্দু বলে ভয় পাইনি, মুসলমান বলে ছেড়ে দিইনি। যে শেখায় তার ভয় পেতে নেই। যে ভয় পায় সে ভয় পেতে শেখায়। … ইত্যাদি। শহরসুদ্ধ লোক তাঁর জন্য দুঃখ করল। তিনি চট্টগ্রামে চলে গেলেন। শওকত আলি যুদ্ধে যায়নি। যাব যাব করছিল, তার আগেই যুদ্ধ থেমে গেল। শওকত আলি চলে গেল লালমণিরহাট।
আমরা স্কুলের শেষ ক্লাসে পড়ি তখন। স্কুলের মাঠে ফুটবল খেলতে নামি। গোঁফের জায়গাটা কালচে হয়ে আসছে। ট্রেঞ্চগুলো বুজিয়ে ফেলা হয়েছে। দরগার পেছনের টিলাটা ফাঁকা পড়ে থাকে। এখনও দিনের শেষে চাঁদ ওঠে। টিলার ওপর কেউ গিয়ে বসে না। আলাদা গার্লস স্কুল খোলায় পুরোনো স্কুলে মেয়েদের পড়া বন্ধ হয়ে গেল। আমরা তখন মেয়েদের মানে বুঝতে শিখেছি।
দীপু অনেক লম্বা হয়েছে। মাথার চুলে পিঠ ঢাকা যায়। লালচে আভার এক ঢল চুল তার। পরনে কখনো ফ্রক, কখনো শাড়ি। তার নাম এখন দীপালি। খুব সুন্দর হয়েছে, কেবল একটু রোগা। তারা এখন চার বোন। মাঝে মাঝে লিচুগাছে ছাওয়া রাস্তায় দেখা হয়। ছেলেবেলা থেকেই মেয়েদের সঙ্গে কথা না বলার অভ্যেস। বিশ্বাস সাহেবের নিয়ম ছিল। দেখা হলেও দীপুর সঙ্গে কথা বলতাম না। দীপুও বলত না। তাকাতও না।
দিন শুরু হত। দিন শেষ হত। আবার শুরু হত। তার মানে তখন বুঝতে শিখেছি। বয়স।
তখন দিন শুরু হত স্মৃতিশূন্যভাবে। অতীত বা ভবিষ্যৎ কোনোটারই কোনো ভার ছিল না। দিনটা নতুন তামার পয়সার মতোই আদরের ছিল, প্রতিটা দিন ছিল উৎসবের মতো। কয়লার ধোঁয়ার গন্ধে ঘুম ভাঙত। দাঁত মাজতে কী যে আলিস্যি। উঠে এক দৌড়ে ঘরের বাইরে গিয়ে পড়লেই পৃথিবীর আদিমতম গন্ধটি পাওয়া যেত তখন। ঘাস, গাছপালা আর মাটির ভিজে সোঁদা গন্ধ। পুবে রোদের মুখ লাল, পশ্চিমে আমাদের লম্বা। ছায়া। চারদিকে মাটি, গাছপালা, পৃথিবী। পৃথিবী কেমন তা অবশ্য জানা ছিল না। শোনা ছিল, নীচে এক গভীর। জলাশয় আছে, তার ওপর জাহাজের মতো ভাসছে পৃথিবী। সতুয়ার বিশ্বাস ছিল, ব্রহ্মপুত্র আড়াই প্যাঁচ দিয়ে রেখেছে পৃথিবীকে, গারো পাহাড় পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু পাহাড়। মিসিসিপি আর মিসৌরির কথা সে কখনো বিশ্বাস করত না। ম্যাপ দেখালে হাসত। বলত–ওসব হচ্ছে সাহেবদের কথা। ওসব কী বিশ্বাস করতে আছে? যারা খেয়ে হাত প্যান্টে মোছে, দাঁত মাজে না–অ্যাঃ।
দিন শুরু হত দুঃখের সঙ্গেই। পড়াশুনো। কালী চক্রবর্তী বারোমাস কফের রুগি, কম্ফটারটা গামছার মতো হয়ে গিয়েছিল। তাঁর কণ্ঠমণি আমরা কখনো দেখিনি। মুঠ মুঠ মুড়ি মুখে দিয়ে, সুরুৎ সুরুৎ চা টেনে নিতেন ভেতরে, বলতেন–আঃ! তাঁর আঙুলের ডগা থেকে সরল, সাঙ্কেতিক আর সুদকষা ঝরে পড়ত। সবসময়ে উবু হয়ে বসতেন, অর্শ বা ভগন্দর কিছু একটা ছিল বলে বসতে পারতেন না। তাঁর গা থেকে একটা শসা-শসা গন্ধ আসত। স্নান বারণ ছিল বলেই বোধ হয় ঘাম বসে একরকম গন্ধ ছাড়ত।
ঝাঁপের জানালাটা লাঠি দিয়ে ঠেলে তোলা। পাশেই উত্তরে ছোট্ট একটু জমি, তারপর শওকত আলির বাড়ি। যুবা শওকত আলি সেই জমিতে সকালের মিঠে রোদে কসরত করছে। তুর্কি লাফ দিয়ে শূন্যে উঠে শরীর উলটে ঝপ করে নেমে আসত প্রথমটা। সেই শূন্যের ডিগবাজি ছিল দেখবার মতোই। এত সহজে করত যেন মনে হত ওরকম করাটাই যেকোনো মানুষের নিত্যক্রিয়া। তারপর লাঠির কসরত। লোকে বলত, শওকত লাঠি ঘুরিয়ে বন্দুকের গুলি আটকায়। আমরা অবশ্য ছোটো ছোটো ঢিল ছুঁড়ে দেখেছি, সেগুলো টুকটাক ছিটকে পড়ে। গায়ে লাগে না। আমরা ভূগোল পার হয়ে ইতিহাসের পড়া দিতে দিতে আলেকজাণ্ডারের বাবার নাম ভুল করতামই। বারবার ম্যাসিড়নের নৃপতি… ম্যাসিডনের নৃপতি ছিলেন… অ্যাঁ… ম্যাসিডনের… মনে পড়ত না। কারণ বাইরে শওকতের স্যাঙাত নিধে তখন এসে গেছে। ছোটো দু-খানা কাঠের ছুরি নিয়ে দু-পক্ষ ঘুরে ঘুরে বলছে, শির, তামেচা, বাহেরা, কোটি, ভান্ডা, ঊর্ধ্ব… শির তামেচা বাহেরা, কোটি ভান্ডা ঊর্ধ্ব… মাথা থেকে শুরু করে সারাশরীর জুড়ে আক্রমণ এবং প্রতিরোধ। ছোরা খেলার নামতা আমাদের ওইভাবেই মুখস্থ হয়ে যায়। আলেকজাণ্ডারের বাবার নাম মনে পড়ত না।
শওকত আলির ছিল একটা ম্যাজিকের ঘর। সে-ঘরে ঢোকা বারণ ছিল। কিন্তু আমরা জানতাম। সে-ঘরে মড়ার মাথার খুলি আছে, আর আছে হাতের হাড়–জাদুদন্ড। পুরোনো পুথির মতো জাদুর বই। বাইরের ঘরে একটা বাঘছাল, দেওয়ালে টাঙানো, মাথাসুদ্ধ। চিতাবাঘের ছাল। সেবার মাদপুরে বাঘটা এসে এক মাঘমাসে উৎপাত শুরু করে। একটা কুকুরের মতো ছোটোখাটো বাঘ, তবু তার দাপটেই বাহেরা অস্থির হয়ে গেল। জোতদার দলুইয়ের গাদা বন্দুক তার গায়ে আঁচড়ও কাটল না। সে এসে গঞ্জে খবর দিল। শৌখিন শিকারিরা ছুটির দুপুরে বন্দুক কাঁধে চলল। শওকত আলির বন্দুক ছিল না। বশংবদ লাঠিগাছ কাঁধে নিয়ে সেও চলল বিটারদের সঙ্গে। মাদপুরের ধানখেত পার হলে জঙ্গল, জল। সেখানে টিন আর ক্যানেস্ত্রার চোটে বিস্তর পাখি উড়ে গেল। বন্দুকের শব্দ ধুন্ধুমার। বাঘ আর বেরোয় না। একা শওকত আলি জঙ্গল টুড়তে ছুঁড়তে এক গর্তের মধ্যে দুটো বাচ্চাসমেত মাদি বাঘটাকে ঘুমোতে দেখতে পেল। দেখে অবাক। এইটুকু বাঘ গোরু-মোষ মারে! সদ্য-বিয়োনী সেই বাঘ একবার শওকতকে মুখ ঘুরিয়ে দেখে ঠিক বেড়ালের মতো শব্দ করে। বাঘটাকে ছোট্ট দেখেই শওকত আলি তার লাঠির ওপর বিশ্বাস রেখে এগিয়ে যায়। সেই লাঠি নিপুণভাবেই চালিয়েছিল শওকত আলি কিন্তু বাঘটা কেবল একটা ছোট্ট চকিত লাফ দিয়ে উঠে এসেছিল। নিঃশব্দে। একটা চড়ে কোথায় গেল লাঠি। বাপরে বলে শওকত আলি জান বাঁচাতে লড়াই শুরু করে। সমস্ত গা ফালা ফালা করে ভেঁড়া ন্যাকড়ার মতো ছিঁড়ে ফেলছিল বাঘ। হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। শিকারিরা দৌড়ে এসেছে, হাতে বন্দুক কিন্তু কিছু করার নেই। গুলি যে কারও গায়ে লাগতে পারে। গলা টিপে অবশেষে মেরেছিল শওকত আলি বাঘটাকে। গভর্নমেন্ট থেকে পাঁচশো টাকা পুরস্কার আর চিকিৎসার খরচ দিয়েছিল। স্কুল ছুটি ছিল একদিন। সোনা-রুপোর গোটাকয় মেডেল আর মানপত্র দেওয়া হয়েছিল তাকে। সে সবই বাইরের ঘরে আলমারিতে সাজানো। আলমারির পাশের দেওয়ালে একটা বেতের ঢাল, তার পিছনে দু-খানা সত্যিকারের তরোয়াল ছিল। মাঝে মাঝে সেগুলোতে তেল মাখাতে খাপ থেকে বের করে আমাদের ডাকত সে। আমরা সর্বস্ব ফেলে তরোয়াল দেখতে যেতাম। গঞ্জে শওকত আলিকে সবাই খাতির করত।
সেবার চা-বাগান ঘুরে ছেঁড়া পাতলুন পরা ম্যাজিশিয়ান প্রোফেসর ভট্টাচার্য গঞ্জে এসে হাজির হল। ডাক্তার শশধর হালদারই তখন গঞ্জের সবচেয়ে বড়োলোক। ফোড়া কাটতে ভয় পেতেন দারুণ, একমাত্র ইঞ্জেকশনেই ছিল তার হাতযশ। ব্যথা লাগত না যে তার নয়। এমনকী রুগীর যে-রকম মুখ বিকৃত হত ব্যথায়, তারও সেরকম হত। তবে ইঞ্জেকশনটা খুব তাড়াতাড়ি দিতে পারতেন এবং তারপর ভালো করে ধুয়ে ফেলতেন। ডাক্তারির চেয়েও তার পসার ছিল ওষুধের ব্যবসায়, আর গোরুর দুধে! সাত সের দুধ দেয় এমন গোরু আমরা তার বাড়িতেই প্রথম দেখি। গঞ্জে গণ্যমান্য লোক এলে তার বাড়িতে ওঠাই ছিল রেওয়াজ।
বড়ো একখানা টিনের গুদামঘর ছিল সেই গঞ্জের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, তার একধারে বাজুরিয়াদের সিমেন্টের। বস্তা, ত্রিপল, কাঠ আর বাঁশের ভূপ। অন্য ধারে কাঠের তক্তা জুড়ে মঞ্চ। টিনের চেয়ারে সামনের দিকে বসতেন গণ্যমান্যরা, তাদের সামনে বিছানো ত্রিপল আর শতরঞ্চিতে বাচ্চারা, পিছনের বেঞ্চ-এ পাবলিক। প্রোফেসর ভট্টাচার্য প্রথমদিকে এলেবেলে খেলা দেখালেন। পিস্তল ছুঁড়ে ধোঁয়ার ভিতর থেকে ভারতমাতার আবির্ভাব দেখে পাবলিক আর বাচ্চারা খুব হাততালি দিল। তারপর বাক্সবন্দি খেলা, কঙ্কালের জলপান, শূন্যে ভাসমান মানুষ। ক্লাস সিক্সের দিলীপকে ডেকে নিয়ে অদৃশ্য করে দিলেন। আধঘণ্টা পর খেলার মাঠের গোলপোস্টের সঙ্গে বাঁধা অবস্থায় তাকে পাওয়া গেল। এসব দেখে গণ্যমান্যরা হাততালি দিতে লাগল। প্রোফেসর ভট্টাচার্য বারবার বলতে লাগলেন–
এই পুওর বেলিটার জন্য ডোর টু ডোর বেগিং করে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে… এই পুওর বেলিটার জন্যে… এইসব বললেন আর মড়ার হাড় নেড়ে সব আশ্চর্য খেলা দেখাতে লাগলেন। সবশেষে চ্যালেঞ্জ। যদি কেউ থাকেন যিনি প্রোফেসর ভট্টাচার্যের সব খেলা দেখাতে পারবেন, তবে ভট্টাচার্য তাঁকে একশো টাকা দেবেন, যদি কেউ চ্যালেঞ্জ করে না পারেন তবে তাঁকে একশত টাকা দিতে হবে।
শওকত আলি টিনের চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়িয়ে বলল–আমি পারি।
পরদিন সকালেই প্রোফেসর ভট্টাচার্য হাওয়া হয়ে গেলেন। কিন্তু শওকত আলি সব খেলা দেখাল। প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত। এমনকী নন্তুকে ডেকে হিপনোটাইজ করে তাকে দিয়ে এমন সব শক্ত শক্ত অঙ্কের উত্তর। করিয়ে নিল যে, কালীমাস্টারমশাই পর্যন্ত হাঁ হয়ে গেলেন। নন্তু সাতঘরের নামতাও পারে না যে! সবশেষে নকে শওকত আলি বলেছিল–সাবধান, কাউকে খুঁয়ো না, তুমি কিন্তু কাঁচের তৈরি। সেই ঘোর নন্তু পরের সাতদিনেও কাটাতে পারেনি। খেত ঘুমোত খেলত, কিন্তু কেউ ছুঁতে গেলেই আঁতকে উঠে চেঁচাত–ধোরো না, ধোরো না আমাকে, আমি কাঁচের তৈরি।
দিন শুরু হত। কালীমাস্টারমশাই বেলা করেই পড়িয়ে উঠতেন। আইবুড়ো মানুষ। গঞ্জে কী করে যে কবে এসে পড়েছিলেন কে জানে! নন্তুদের বাড়ি সকালবেলাটায় খেয়ে স্কুল সেরে বিকেলে সাধনদের পড়িয়ে রাতে শশধরবাবুর বাড়িতে খাওয়া সেরে ওদের বাইরের ঘরের একধারে গিয়ে শুয়ে পড়তেন। আমাদের দিন। সূর্যোদয়ের সঙ্গে শুরু হত, শেষ হতে চাইত না। কালীমাস্টার চলে গেলে দুই লাফে বাইরে গিয়ে পড়তাম। বই খাতা গুছোনোর জন্য দিদি পড়ে থাকত। বাইরে তখন সকালের প্রথম বনজ গন্ধটি আর নেই। শওকত আলির কসরত শেষ হয়ে গেছে। মাঠ ফাঁকা। তবু পৃথিবীতে করণীয় কিছুর শেষ ছিল না। মড়ার হাড় খুঁজতে শেলিদের। বাড়ির পিছনে পোড়ো মাঠটাতে চলে যেতাম।
সেই মাঠে পশ্চিমাদের বয়েল গাড়ির বড়ো বড়ো বলদগুলো চরে বেড়াত। কাঁধে ঘা। সেই ঘা খুঁটে খাচ্ছে কাক। সেখানে হাড় পাওয়া যেত বিস্তর। কিন্তু সাধন বলত–ও হাড় ছুসনি, ভাগাড়ের গো হাড়। সেই মাঠ পার হলে নদীর ধারে ছিল শ্মশান। শরৎকালে শ্মশানের দিকটায় কাশ ফুলে ঢেউ দিত। কিন্তু শ্মশান পর্যন্ত যেতে সাহস হত না। সেই মাঠে দাঁড়িয়ে আমরা দূর থেকে শ্মশান দেখতাম। ভয় করত। মানুষের হাতের হাড় পাওয়া হয়নি।
দূর থেকেই দেখতাম বাবুপাড়ার রাস্তা দিয়ে শচীন আর শেলি গোবরের ঝুড়ি হাতে ফিরছে। শচীনরা ছিল তিন বোন আর এক ভাই। পিকলি, বিউটি, শচীন, শেলি। শচীনের বোনদের এইসব সাহেবি নাম রেখেছিলেন। তার বাবা। একসময়ে শচীনরা ছিল গঞ্জের বড়োলোক। তার বাবা কাছেপিঠের এক চা-বাগানের ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। বন্দুক ছিল, ঘোড়া ছিল। বাড়িখানাও ছিল বাংলো প্যাটার্নের। তার ছিল দুই বিয়ে, অনেককাল সেটা জানা যায়নি। আগের পক্ষের ছেলেরা সব বড়ো বড়ো। সেবার শচীনের বাবা কালাজ্বরে মারা গেলে, আগের পক্ষের ছেলেরা এসে সব সম্পত্তি দখল করে। কলকাতায় তাদের বাড়ি ছিল বলে কেবল গঞ্জের বাড়িখানা ছেড়ে দেয়। শচীনরা গরিব হয়ে গেল। পিকলি, বিউটি আর শেলি লেস-এর জামা পরা, রুজ পাউডার মাখা, অর্গান বাজিয়ে গান গাওয়া, কিংবা জন্মদিনে পার্টি দেওয়া–এসব ভুলেই গেল। বাড়িখানা এখন রংচটা, কোথাও দেওয়ালের ইট বেরিয়ে আছে, বাগানের ভিতরে মোরামের বাহারি রাস্তাটায় গর্ত, সকাল থেকেই শচীন আর শেলি গোবর কুড়োয়, কাঠ-পাতা কুড়োয়। তার মা একসময়ে জর্জেটের শাড়ি পরত, এখন লজ্জার মাথা খেয়ে বাজুরিয়াদের বাড়ি আয়ার কাজ করে। বাজুরিয়াদের এক ছেলে বিলেত গিয়ে মেম বিয়ে করে। এনেছিল। বাজারের ভেতরে তাদের পৈতৃক বাড়িতে সেই মেমবউয়ের ঠাঁই হয়নি বলে হাই স্কুলের পেছনদিকে চমৎকার একখানা বাড়ি করে সেইখানে থাকত। সেই বাড়িতেই যেত শচীনের মা। পিকলি আর বিউটি একসময়ে কারও সঙ্গে মিশত না। ঘরে তাদের ব্যাপাটেলি, কারম, লুডো কত কী ছিল, ভাই-বোনেরা সেসব নিয়ে থাকত। এখন সেই দু-বোন পাড়ায় পাড়ায় ঘোরে। এ-বাড়ি সে-বাড়ি গিয়ে এর-ওর তার নিলেমন্দ করে। কেউ তাদের বসতে বলে না। তাদের চরিত্র নিয়ে কথা ওঠে। শচীন ক্লাসে ফাস্ট হয়। হেডমাস্টার এমদাদ আলি বিশ্বাস নিজের পকেট থেকে তাকে বই কেনার খরচ দেন। বলেন, গরিবরাই ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভের যোগ্য।
ছোটো ছোটো ঝুপসি লিচুগাছের ঘন ছায়ার ভেতর দিয়ে পথটি গেছে। বইখাতা হাতে সেই পথ ধরে যেতে যেতেই হঠাৎ শুনতে পেতাম দূর থেকে ইস্কুলের ঘণ্টার শব্দ। ওয়ার্নিং। সাধন বলত–দৌড়ো। এমদাদ আলি বিশ্বাস এ সময়টায় গেট-এর কাছে দাঁড়িয়ে থাকেন। টর্চবাতির মতো তাঁর চোখ জ্বলে। আমরা দৌড়োতাম!
ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে পড়ে সেই ইস্কুলে। মাস্টারমশাইরা আছেন, দিদিমণিরাও আছেন। মেয়েরা ক্লাসে বসে থাকে না, তারা থাকে মেয়েদের কমনরুমে। মাস্টারমশাই কিংবা দিদিমণিদের সঙ্গে ক্লাসের শুরুতে লাইন বেঁধে আসে, আবার ক্লাসের শেষে লাইন বেঁধে ফিরে যায়। ছেলেদের দিকে তাকানো বারণ। কথা বলা তো দূরের কথা। দিদি এক ক্লাস উঁচুতে পড়ত, ফেল করে আমার সঙ্গে পড়ে তখন। ক্লাসে আমি পড়া না পারলে একমাত্র সে-ই আমার দিকে কটমট করে চেয়ে থাকত। বিশ্বাস সাহেবের দাপটে তখন বাঘে-গোরুতে এক ঘাটে জল খায়।
সেবার শহরের ইস্কুলের টিম ফুটবল খেলতে আসে। এইট-এর কামু দারুণ খেলেছিল। শহরের টিম দু-গোল খেয়ে গেল। ফ্রেণ্ডলি ম্যাচ বলে কোনো প্রাইজ ছিল না। তবু বিশ্বাস সাহেব কামুদার পিঠ চাপড়ে দিয়ে আদর করলেন এবং ঘোষণা করলেন–কামুদাকে তিনি রুপোর মেডেল দেবেন। খেলার শেষে আমরা কামুদাকে ঘিরে ধরলাম। কামুদা বাড়ি ফেরার সময়ে বলল–বিশ্বাস সাহেবের গায়ে যা সুন্দর আতরের গন্ধ, না রে!
পরদিন হইহই কান্ড। সারাস্কুলের দেওয়ালে সব অসভ্য কথা লেখা। কমনরুমেই বেশি। শহরের ফুটবল টিম ইস্কুলবাড়িতেই রাত্রিবাস করে সকালে ফিরে গেছে। সবাই বলল–এ ওদেরই কাজ। দু-গোল খেয়ে রাগের চোটে এসব করে গেছে। কিন্তু তবু আমাদের ইস্কুলের কোনো ছেলে এ কান্ডের সঙ্গে জড়িত কিনা সে-বিষয়ে নিঃসংশয় হওয়ার জন্য এমদাদ আলি বিশ্বাস ক্লাসে ক্লাসে ঘুরে ডিকটেশন দিলেন–মনোজ মাংস মুখে দিয়া মুখ মুছিয়া মালদহ মুখে যাত্রা করিল। এই বাক্যটা আমরা সবাই খাতায় লিখে, সেই পাতায় নাম ক্লাস রোল নম্বর দিয়ে পাতাটা ছিঁড়ে বিশ্বাস সাহেবকে দিয়ে দিলাম। ভয়ে বুক শুকিয়ে আছে। কিন্তু কারও কিছু হল না। আমরা সেই বাক্যটার মধ্যে তন্নতন্ন করে খুঁজেও কোনো অসভ্য কথা পেলাম না। বিশ্বাস সাহেব তবে কেন ওই অদ্ভুত বাক্যটা আমাদের দিয়ে লেখালেন? দেওয়ালের কথাগুলো আমরা দেখিনি! তবে অনেকে বলল। বেশির ভাগ অসভ্য কথাই ম দিয়ে লেখা। সাধন সেদিন সন্ধেবেলা এসে বলল–মাংস মুখে দিয়ে কেউ মুখ মোছে নাকি! না আঁচালে এঁটো থেকে যায় না?
বিকেলটা ফুরোত সবার আগে। পূর্ণিমা থাকলে খেলা শেষ হতে না হতেই চাঁদ উঠে পড়ত। বিকেলটা শেষ হয়ে যাক এরকম ভাবতে ভালো লাগত না। দরগার পেছনে চাঁদমারির মতো উঁচু একটা ঢিবি ছিল। আমরা সেটার ওপর উঠে বসতাম। সাধন, দীপু, প্রদীপ, নন্তু, কোনো কোনো দিন সতুয়া। পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু তালগাছ আছে তাদের গাঁয়ের পাশের গাঁয়ে, সে গাছ শুইয়ে দিলে পৃথিবী ছাড়িয়ে আধ হাত বেরিয়ে থাকবে –এই গল্প বলত সতুয়া। সেই তালগাছ থেকে তাল পড়লে নাকি আশপাশের দশ-বিশটা গ্রামে ভূমিকম্প হয়। এক-একটা তালের ওজন বিশ মন। দীপু বয়সে প্রায় আমার সমান। কিন্তু সে দৌড়ঝাঁপ তেমন করতে পারত না। একটু খেলেই হাঁফিয়ে পড়ত, মারপিট লাগলে বরাবর সে মার খেত। তারপর কাঁদতে বসত। বলত–ম্যালেরিয়া না হলে তোদের দেখে নিতুম। সে সব সময়ে আমার পাশ ঘেঁষে বসত এবং বন্ধুত্ব অর্জনের চেষ্টা করত। সেই ঢিবির ওপর থেকে দেখা যেত, শেলিদের বাড়ির পেছনের মাঠে সূর্য ডুবে গেলে কেমন দু-খানা আকাশজোড়া পাখনা মেলে অন্ধকার উঠে আসছে। সেই দিকে চেয়ে ক্ষণস্থায়ী বিকেলের জন্য খুব দুঃখ পেতাম। নীল সমুদ্রে চাঁদ সাঁতরে চলত অবিরাম। খেলার শেষে আমরা সেই ঢিবির ওপর বসে আরও কিছুক্ষণ বিকেলের আলো দেখার চেষ্টা করতাম। সন্ধে উতরে ফিরলেও আমার তেমন ভয় ছিল না। বাবা বারমুখো লোক, মা রোগাভোগা। আমাদের বাড়ির শাসন তেমন কঠিন নয়। সবচেয়ে বেশি শাসন ছিল প্রদীপের। তার বাবা দেবীপ্রসাদ চক্রবর্তী ছিলেন সাহিত্যিক। অল্প বয়সেই মারা যান। প্রদীপের মা নানারকম হাতের কাজ শিখে গঞ্জে মহিলা সমিতির দিদিমণির চাকরি পেয়ে কলকাতা থেকে চলে আসেন। শোভনা দিদিমণি রোগা কালো মানুষ, ঠোঁটে একটু শ্বেতির দাগ, খুব নিয়ম মেনে চলতেন। প্রদীপ কড়া শাসনে থাকত। তার এক বড়ো ভাই। আছে–সুদীপ। সে মার সঙ্গে আসেনি। কলকাতায় মাসির কাছে থেকে ইস্কুলে পড়ে। সন্ধে হলেই প্রদীপের বাসায় তার বাবার বড়ো করে বাঁধানো ছবির সামনে দীপ জ্বেলে, ধূপকাঠি জ্বেলে দেওয়া হয়, ফুলের মালা দেওয়া হয় ছবিতে। প্রদীপ তাদের বাড়িতে যত্নে রাখা মাসিক পত্রিকা বের করে আমাদের দেখাত। শ্রীদেবপ্রসাদ চক্রবর্তীর নাম ছাপা গল্প আর কবিতা দেখে অবাক হয়ে যেতাম। তাঁর লেখা একটা কলের কোকিলের গল্প ছিল। কিছু বুঝিনি। প্রদীপ বলত–বাবার লেখা বুঝতে হলে মাথা চাই। আমার মা-ই কত লেখা বোঝে না। গঞ্জের সবাই তাদের খাতির করত। যদিও দেবপ্রসাদ চক্রবর্তীর লেখা কম লোকই পড়েছে। শোভনা দিদিমণি তাঁর স্বামীর কথা উঠলেই চোখ আধবোজা করে রাখতেন। সেই চোখের পাতার গভীর থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল জন্ম নিত। কিন্তু অন্য সময়ে তিনি ছিলেন ভীষণ কড়া। প্রদীপকে কখনো আদরের কথা বলতেন না। উঠতে-বসতে খেতে-শুতে সময় বাঁধা ছিল। বিকেলের দিকটায় দিদিমণির ফিরতে দেরি হত বলে সেই সময়টুকুতে চাঁদের আলোয় চাঁদমারির মতো উঁচু ঢিবিটায় সময় চুরি করে সে আমাদের সঙ্গে খানিক বসে থাকত। বলত–আমি একদিন পালাব, দেখিস। লোকের বাড়ি বাসন মাজব, ঘর ঝাঁট দেব, তবু পালাব। কথার মাঝখানে দীপু হঠাৎ চেঁচিয়ে বলত, রন্টু, ওই দেখ তোর বাবা আজও আবার লোক এনেছে। অবাক হয়ে। তাকিয়ে দেখতাম ঠিকই। দরগার সামনে লিচুবাগানের ভেতর থেকে রাস্তাটা যেখানে হঠাৎ বেরিয়ে এসেছে। সেই জায়গাটা পার হয়ে গল্প করতে করতে বাবা আসছে, সঙ্গে একটা খাকির হাফপ্যান্ট পরা লোক, মাথায় হ্যাট। কোথা থেকে যে ধরে ধরে বাবা অতিথি নিয়ে আসত কে জানে। সপ্তাহে তিন-চার দিনই বাইরের অচেনা লোকেরা এসে পাত পাড়ত আমাদের বাসায়। মা রাগ করলে বাবা উদার গলায় বলত–অতিথি খেলে বাড়ির মঙ্গল হয়, মানুষের পায়ের ধুলোয় কত জায়গা তীর্থ হয়ে গেল। মা তখন ঝোঁকে বলত–তা অসময়ে লোক এলে যে আমাদের হরিমটর করতে হয়। বাবা শান্ত গলায় মিনমিন করে বলত–তিথি মেনে যে না আসে সেই তো অতিথি। যারা আসত তাদের মধ্যে ভবঘুরে, চোর, জ্যোতিষী সব রকমের মানুষ ছিল। এসব লোক আমাদের গা সওয়া হয়ে গিয়েছিল। এই হাফপ্যান্ট আর হ্যাটঅলা লোকটা আসার আগে যে এসেছিল, সে এক সকালে চলে গেলে দেখা গেল একটি পেতলের ঘটি, বিছানার চাদর, একজোড়া চটিজুতো সে নিয়ে গেছে। এরপর মা রাগারাগি করায় বাবা আর লোক আনত না। কেবল একা খেতে বসে দুঃখ করে বলত–আমাদের দেশের বাড়িতে প্রতিবেলা একশোখানা পাত পড়ে। বিদেশে চাকরি করতে দেখে এসে দেখ কেমন একা একা খেতে হয়। একা খেলে আমার পেট ভরে না। সেই চুরির পর অনেকদিন বাদে লোক এল। দীপু আমাকে ঠেলা দিয়ে বলল–মামিমা আজ কুরুক্ষেত্র করবে। চল দেখি গিয়ে–! শুনে আমি তাকে একটা গাঁট্টা মারি, বলি। আমার মা-বাবার ঝগড়া দেখবি কেন? সে কাঁদতে থাকে।
খাকি হাফপ্যান্ট পরা লোকটা ছিল গায়ক। মোটাসোটা নাদুসনুদুস চেহারা, গালে পানের ঢিবি। বাবার একখানা লুঙ্গি পরে নিয়ে দিদির সিঙ্গল রিডের হারমোনিয়ামটা নিয়ে সে বারান্দায় চাঁদের আলোয় শতরঞ্চি পেতে বসে গাইতে লাগল–ভুলিনি, ভুলিনি, ভুলিনি প্রিয়, তব গান সে কি ভুলিবার…! বাবা শুনতে শুনতে আধশোয়া হয়ে চাঁদের দিকে চেয়ে উদাস হয়ে গেল। মা নতুন করে রাঁধতে বসেছে। সেই ফাঁকে দেখি উত্তরের মাঠে নালির ধারে শওকত আলি হ্যারিকেন জ্বেলে মুরগি জবাই করতে বসেছে। মুরগি কাটা দেখতে চুপে উঠে গেলাম। ভুলিনি… ভুলিনি… গানের সঙ্গে মুরগিটার প্রাণান্তকর ডাক মিশে যাচ্ছিল। আকাশে জ্যোৎস্নার বান।
লোকটার নাম আমরা দিলাম ডি ও সান্যাল। আমাদের বাড়ির অতিথিরা দু-রকমের ছিল। কিছু লোক ছিল যারা একবার এসে সেই যে চলে যেত, আর আসত না। আর কিছু লোক ছিল যারা ঘুরে-ফিরে আসত। এই লোকটাকে দেখে মনে হল, এ দ্বিতীয় দলের। কাজেই এর একটা নাম দেওয়া দরকার। বাবা তাকে সান্যাল, সান্যাল বলে ডাকে, নাম টের পাই না। সান্যাল আরও একজন আমাদের বাড়িতে আসে। সে ফোকলা। এ লোকটার দাঁত আছে তাই তার নাম দেওয়া হল, দাঁতঅলা সান্যাল। সংক্ষেপে ডি ও এস। ফোকলা জনের নাম এফ সান্যাল আগেই দেওয়া ছিল। পরদিন সকালে কোনো সময়ে যেন বাবার চটিজোড়ায় আমার পা লাগলে লোকটা বলল, খোকা, বাবার চটিতে পা লাগলে প্রণাম করবে। তারপর সে মার রান্নার প্রশংসা করল। আমাকে শংকরা আর বেহাগের পার্থক্য বোঝাতে লাগল। দু-দিন গানে গানে আমাদের মাথা গরম হয়ে রইল। কালীমাস্টারমশাই পর্যন্ত একদিন কামাই করলেন। তারপর লোকটা চলে গেল। শুনলাম সে যুদ্ধে যাচ্ছে। ডি ও সান্যাল আর কোনোদিনই ফিরে আসেনি।
হিটলারের হাতে ইংরেজ তখন বেজায় মার খাচ্ছে। তার ফলে চারদিকে বেকার আর ভবঘুরে বেড়ে গেল। খুব। চাল-ডাল পাওয়া যায় না, কেরোসিন নেই, দেশলাইয়ের আকাল। মার মেজাজ সপ্তমে চড়ে থাকে। দেশ থেকে সেই সময়ে বাবার দু-চারজন জ্ঞাতি, আর তাদের আত্মীয়েরা এসে আমাদের বাসায় থানা গাড়ল। তারা শুনেছে যুদ্ধের বাজারে ধুলো বেচে অনেকে বড়োলোক হচ্ছে। তারাও সব কারবার কনট্রাক্টরি করার জন্য চলে এসেছে কিন্তু ঘাঁতঘোঁত জানা না থাকায় বেমক্কা সারাদিন ঘোরে, রাতে ঘরে বসে জটলা পরামর্শ করে। বাবা অনেকদিন থেকেই সিগারেট ছেড়ে স্বদেশি বিড়ি ধরেছে। জ্ঞাতিরা আসার পর সেই বিড়ি প্রায়ই চুরি হতে লাগল। বাবা কিছু বলতে পারে না কাউকে। তাড়ানো তো দূরের কথা। আমাদের ভাতের ফ্যান গালা বন্ধ হয়ে। গেছে তখন। বাসায় অঙ্ক কষতে আর কাগজ নষ্ট করি না, স্লেটে কষে মুছে ফেলি, স্কুলে উঁচু ক্লাসে স্লেট অ্যালাউ করলেন বিশ্বাস সাহেব। বাড়িতে মা-বাবার কথাবার্তা বন্ধ। শোনা গেল শওকত আলি যুদ্ধে যাবে। আমরা ক-দিন খুব উত্তেজিত হয়ে রইলাম। শওকত আলি লাঠি দিয়ে গুলি ঠেকায়, হাতে বাঘ মারে, মানুষকে সম্মোহিত করে দেয়, সে যুদ্ধে গেলে একটা হেস্তনেস্ত হবেই।
জ্ঞাতিদের জ্বালায় মার প্রাণ ওষ্ঠাগত। দিনে পঞ্চাশবার উনুন থেকে কাগজ জ্বেলে তাদের বিড়ি ধরিয়ে দিতে হয়। দেশলাই নেই। মা প্রকাশ্যে রাগারাগি শুরু করে। জ্ঞাতিরা তখন মাকে খুশি রাখার জন্য বিচিত্র কান্ড শুরু করল। কেউ মার চেহারার, কেউ মার রান্নার প্রশংসা শুরু করল। কেউ বা এর-ওর বাগান থেকে চুরিচামারি করে ফলপাকুড় এনে দিত। ঘরের কিছু কিছু কাজকর্মেও আসত। বাবা ফিরলে তারা সবাই একসঙ্গে হইহই করে উঠত–কাকা এসেছেন, কাকা এসেছেন! তারপর বাবার চটি ধরে টানাটানি, জামা খুলে দেওয়া নিয়ে কাড়াকাড়ি। শেষে বাবা হাত-পা ধুয়ে বিশ্রাম করার সময়ে তারা বাবার হাত-পা-পিঠ দাবাতে বসত, আঙুল মটকে দিত, পিঠে সুড়সুড়ি, মাথা চুলকোনো–সবই করত। বাবা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়ে চেঁচামেচি করত–ওরে আর জোরে দাবাসনি, হাড়গোড় ভেঙে যাবে। তারা ছাড়ত না।
জ্ঞাতিদের মধ্যে একজন ছিল পুলিন। একদিন তাকে দেখি শেলিদের বাড়ির পেছনের মাঠে ভাগাড়ে হাড় কুড়িয়ে একটা বস্তা বোঝাই করছে।
ভারি অবাক হয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম–এসব কুড়োচ্ছেন কেন?
পুলিন ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বলল–চুপ। একটা কারবারের কথা মাথায় এসেছে। হাড়ে বোতাম হয় জানো তো?
জানি।
পুলিন খুব হেসে বলল–কথাটা এতদিন একদম মাথায় আসেনি। হঠাৎ সেদিন এপাশটা দিয়ে যেতে যেতে ব্যাপারটা মাথায় এসে গেল। শুধু বোতাম না, লবণ শোধন করতেও লাগে। গোরারা তো সবই কিনে নিচ্ছে, যুদ্ধে নাকি সব লাগে। কাউকে বোলো না কিন্তু, লোকে বুদ্ধি পেয়ে যাবে।
পুলিন সেই হাড়ের বস্তা নিয়ে বাসায় ঢোকামাত্র মার উনপঞ্চাশ বায়ু কুপিত হয়। সন্ধেরাতে সেই হাড় পুলিনকে ফেলে দিয়ে আসতে হয়। তারপর শীতের রাতে স্নান করে ঘরে ঢোকা। সেই বস্তার মুখটা একবার আমি একটু ধরেছিলাম। কিন্তু পুলিন খুব মহত্ত্ব দেখাল, আমার কথা মাকে বলল না। বাজারে তখন লোহার বোতাম চালু হয়েছে।
ব্ল্যাক মার্কেট কথাটা তখন শোনা যাচ্ছে খুব। পুলিন সর্দিজ্বরে পড়ে থেকেই প্রায়ই বলত–এবার ব্ল্যাক মার্কেটের ব্যাবসা চালু করব। কথাটার অর্থ সেও ভালো বুঝত না।
বাড়িতে জ্ঞাতিরা জড়ো হওয়ায় বাবা অখুশি ছিল না। একা খেতে হত না। পেট ভরত। কিন্তু মার মূর্তিখানা দিন দিন মা কালীর মতো হয়ে আসছিল। ঠিক সেই সময়ে কলকাতায় বোমা পড়ায় সেখানে আমার মামাবাড়ি থেকে দিদিমা, তিন মামা, দুই মাসি চলে এল আমাদের বাসায়। মার আর কিছু বলার রইল না। বাবার মুখ উজ্জ্বল দেখাল। মামাবাড়ির লোকজন যেদিন গেল সেইদিনই মা নিজে যেচে বাবার সঙ্গে ভাব করে। বাড়িতে আর জায়গা ছিল না। পড়াশুনো মাথায় উঠে গেল। আমরা সারাদিন মনের আনন্দে ঘুরি। সাধনদের বাড়িতেও লোক, দীপুদের বাড়িতেও। কেবল প্রদীপদের বাড়িতে সন্ধেবেলা সাহিত্যিক দেবপ্রসাদ চক্রবর্তীর ফটোতে রোজ বিকেলে মালা দেওয়া হয়, ধূপকাঠি জ্বলে। প্রদীপ সকাল-বিকেল পড়তে বসে। তার মা বলে–কত বড়ো সাহিত্যিক ছিলেন তোমার বাবা সে-কথা কখনো ভুলো না। তোমাকে বড়ো কিছু হতেই হবে। প্রদীপ আড়ালে-আবডালে বলত–সাহিত্যিক না কচু! লিখত তো বাচ্চাদের লেখা, তাও বেশির ভাগ অনুবাদ।
আমরা অবাক হয়ে বলতাম–তুই কী করে জানলি?
মামাবাড়িতে এই নিয়ে হাসাহাসি হত কত! আমি যুদ্ধে যাব জানিস। সাহিত্যিক-ফাহিত্যিক নয়, আমি হব। সোলজার।
চারদিকে ট্রেঞ্চ কাটা হচ্ছে তখন। দরগার মাঠে লোকলশকর লেগে দিব্যি আঁকাবাঁকা ট্রেঞ্চ কেটে দিল। নতুন রকমের একটা খেলা পেয়ে গেলাম আমরা। গর্তের মুখে লাফ দিই। সবাই পারি, কেবলমাত্র দীপুই পারে না। তিন বোনের পর দীপু একমাত্র ভাই, তার মা-বাবার খুব আদরের, তাই বোধ হয় পারত না। তার হাত-পা নরম নরম ছিল।
বর্ষায় ট্রেঞ্চে ব্যাঙের আস্তানা হল। জল জমে ডুবজল। নিধে ছিপ ফেলত। চ্যাঙা-ব্যাঙা মাছ ধরত। অনেক রাতে বৃষ্টি নামলে প্রবল ব্যাঙের ডাক শোনা যেত। আকাশে কাক, চিলের মতো এরোপ্লেন দেখে দেখে আর শব্দ শুনেও চোখ তুলে তাকাতাম না।
মামারা ছিল বয়সে আমাদের চেয়ে অনেক বড়ো। তারা তখন কিশোর কিংবা যুবা। প্রখর চোখে তারা মেয়েদের দেখত। দীপুদের বাড়িতে তাদের বয়সি কয়েকটা ছেলে এসেছিল। সব কলকাতার ছেলে। মামারা তাদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াত। সিঁথি কাটা, জুতো পরা, জামার হাতা গুটোনো–এসব আমরা তখনই তাদের কাছ থেকে শিখছি।
দরগার সামনে আমাদের ট্রেঞ্চ-এর দু-ধারে লাফাতে দেখে মামারা হেসে খুন। দীপু লাফাতে পারে না দেখে আমার ছোটোমামা জ্যোতির্ময় গম্ভীর হয়ে বলল–ও লাফাবে কী! ও তো মেয়ে!
যাঃ। বলে আমি চেঁচিয়ে উঠি।
মামা হাসল। বলল–আমি জানি। ওর ভাই নেই বলে ওর মা-বাবা শখ করে ওকে ছেলে সাজিয়ে রাখে।
আমরা তাকিয়ে দেখি, দীপু দরগার মাঠ ধরে প্রাণপণে দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছে।
পরদিন বিকেলে টিলার ওপর আমাদের মিটিং বসল। আমি সাধন, প্রদীপ, সতুয়া, নন্তু আর একধারে দীপু গোঁজ হয়ে বসে। তার চোখে জল।
তুই মেয়ে? সাধন জিজ্ঞেস করল। মাথা নাড়ল দীপু, হ্যাঁ।
আমরা অনেকক্ষণ কথা খুঁজে পাই না। কী বলব! দীপু ততক্ষণে কাঁদতে থাকে। বলে–আমার সঙ্গে খেলবি? আর খেলায় নিবি না?
সেসময়ে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলতে খেলতে আমাদের মধ্যে পৌরুষ এসে গেছে। প্রদীপ বলল–কী করে খেলি বল! সবাই জেনে গেলে বলবে মেয়েদের সাথে খেলি।
দীপু অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল–আমি যে মেয়েদের খেলা কখনো খেলিনি। আমার মেয়ে-বন্ধুও নেই।
সতুয়া খুব অবাক হয়েছিল। বলল–মেয়েছেলে তো তোকে হতেই হবে। ও কি লুকোনো যায়?
আমার মন খুব খারাপ ছিল। দীপু আমার বন্ধুত্বই সবচেয়ে বেশি চাইত। আমার দিকে চেয়ে দীপু বলল–মেয়ে হতে আমার একটুও ভালো লাগে না।
নন্তু ধমক দেয়–মেয়ে হবি আবার কী! তুই তো মেয়েই।
দীপু গোঁজ হয়ে বসে কাঁদতে থাকে, সে কিছুতেই আমাদের সঙ্গ ছাড়বে না।
নন্তু আমাদের আড়ালে ডেকে বলল–ভাই, বদনাম হয়ে যাবে কিন্তু। আমরা ক-জন ছাড়া দীপুর সঙ্গে আর কেউ খেলত না। ওকে দলে রাখা যাবে না।
আমরা পরামর্শ করলাম অনেক। সবশেষে সতুয়া গিয়ে বলল–দীপু, তোকে আমরা অনেক জিনিস দেব। কাল থেকে আর আমাদের সঙ্গে খেলতে আসিস না।
সেই দিন দীপুকে আমরা প্রায় একটা ফেয়ারওয়েল পার্টি দিলাম। সেদিনও দিনের শেষে চাঁদ উঠেছিল। আমরা যে-যার বাসা থেকে মার্বেল, ছুরি, গল্পের বই এনে দিলাম। দীপু নিল। চলে যাওয়ার সময় বলল-বড়ো হয়ে তো কোনো ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ে হবেই, তখন আমি
বলে সে সবার দিকে তাকাল। আমরা চুপ।
দীপু পায়ের আঙুলে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে মুখ নীচু করে বলল–তখন আমি রন্টুকে বিয়ে করব।
এই বলে এক ছুটে টিলা থেকে নেবে গেল দীপু।
যুদ্ধের শেষে একদিন বাড়ি বাড়ি তেরঙা পতাকা উড়ল। ইস্কুলে পতাকা তুললেন এমদাদ আলি বিশ্বাস। তার কিছুদিন পরেই ফেয়ারওয়েল দেওয়া হল তাঁকে। সবাই তাঁর কৃতিত্বের কথা বললেন। তিনি বলতে উঠে বললেন–আমি যে মুসলমান বলে পাকিস্তানে চলে যাচ্ছি তা নয়। আমি বুড়ো হয়েছি, এই জায়গা ছেড়ে কোথাও না কোথাও আমাকে যেতেই হত। গোরও তো ডাকছে। আমি হিন্দু-মুসলমান দু-রকম ছেলেই পড়িয়েছি। যখন শাসন করতে হাত তুলেছি তার ভালোর জন্য তখন হিন্দু বলে ভয় পাইনি, মুসলমান বলে ছেড়ে দিইনি। যে শেখায় তার ভয় পেতে নেই। যে ভয় পায় সে ভয় পেতে শেখায়। … ইত্যাদি। শহরসুদ্ধ লোক তাঁর জন্য দুঃখ করল। তিনি চট্টগ্রামে চলে গেলেন। শওকত আলি যুদ্ধে যায়নি। যাব যাব করছিল, তার আগেই যুদ্ধ থেমে গেল। শওকত আলি চলে গেল লালমণিরহাট।
আমরা স্কুলের শেষ ক্লাসে পড়ি তখন। স্কুলের মাঠে ফুটবল খেলতে নামি। গোঁফের জায়গাটা কালচে হয়ে আসছে। ট্রেঞ্চগুলো বুজিয়ে ফেলা হয়েছে। দরগার পেছনের টিলাটা ফাঁকা পড়ে থাকে। এখনও দিনের শেষে চাঁদ ওঠে। টিলার ওপর কেউ গিয়ে বসে না। আলাদা গার্লস স্কুল খোলায় পুরোনো স্কুলে মেয়েদের পড়া বন্ধ হয়ে গেল। আমরা তখন মেয়েদের মানে বুঝতে শিখেছি।
দীপু অনেক লম্বা হয়েছে। মাথার চুলে পিঠ ঢাকা যায়। লালচে আভার এক ঢল চুল তার। পরনে কখনো ফ্রক, কখনো শাড়ি। তার নাম এখন দীপালি। খুব সুন্দর হয়েছে, কেবল একটু রোগা। তারা এখন চার বোন। মাঝে মাঝে লিচুগাছে ছাওয়া রাস্তায় দেখা হয়। ছেলেবেলা থেকেই মেয়েদের সঙ্গে কথা না বলার অভ্যেস। বিশ্বাস সাহেবের নিয়ম ছিল। দেখা হলেও দীপুর সঙ্গে কথা বলতাম না। দীপুও বলত না। তাকাতও না।
দিন শুরু হত। দিন শেষ হত। আবার শুরু হত। তার মানে তখন বুঝতে শিখেছি। বয়স।